কথাসাহিত্যিক শহীদুল জহিরের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁকে নিয়ে লেখা
নীলক্ষেত ফুটপাতের বইয়ের দোকানগুলো তখন বাংলা একাডেমির দিকে এগিয়ে আসত তার পুরনো বইয়ের নিজস্ব অপরিকল্পিত ভাণ্ডার নিয়ে; মূলত বইমেলার সময় পুরোটা ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে, হয়তো এর পরেও কিছুদিন। এখনও আসে, কিন্তু তখনও নীলক্ষেত ফুটপাত ভারতীয় বাংলা জনপ্রিয় উপন্যাসের পাইরেটেড সংস্করণে দখলীকৃত হয়নি, বাংলাদেশ বা পশ্চিমবাংলার পুরনো বইপত্তরে প্রায় ঠাসাই থাকত কোনও-কোনও দোকান। আর অভাবনীয়ভাবে সেখানে পাওয়া যেত দুর্লভ ও অদেখা পুরনো কোনও বাংলা বই। কখনও কম খ্যাত কোনও লেখকের বিখ্যাত কোনও লেখককে উপহার দেয়া বই, বিখ্যাত কোনও লেখকের পাঠককে স্বাক্ষর করা বই মিলে যেত কোনও কোনও সময়ে; হাতে নিয়ে কেনার আগে বা পরে, দরদাম করার আগে বা পরে ওইসব স্বাক্ষর দেখতে দেখতে এ কথাও উঁকি দিত মনে, কীভাবে এখানে এল এ বই, কার হাত ঘুরে? আর, সামনে যে লোকটি নিয়ে বসেছে এই বই, সেই-বা কীভাবে পেল তা? কিন্তু সেই বিস্ময় কি কেউ কখনও ভাঙে, অন্তত তখনও আমাদের যা বয়েস আর যে দুই-একখানা বই কিনবার সামর্থ্য আছে, তাতে দোকানির কী এমন দায় পড়েছে যে, জানতে চাইলে জানিয়ে দেবেন, কী করে তার হাতে এল এ বই! এর বাইরে ইংরেজি ভাষার বা ইংরেজিতে অনূদিত যেসমস্ত বই—তার কোনও-কোনওটিতে রাষ্ট্রের দূতাবাসের সিল দেখে বোঝা যেত, সেখান থেকে এই ফুটপাতে এসেছে কোনও সূত্রে, কোনও কায়দায়।
সবচেয়ে বিস্ময়কর অবশ্য ছিল, কোনও বইয়ের একাধিক অথবা আরও বেশি অন্তত আটটি-দশটি কপি একসঙ্গে কাছাকাছি ছড়ানো। উদার সেই আয়োজন! একই বই, এতগুলো, একসঙ্গে—দেখে যেন মনে হত এই ফুটপাতের দোকানদার নিজেই প্রকাশকের তরফ থেকে এখানে এই বইয়ের পসরা বসিয়েছেন। খোদ নীলক্ষেতে এই ঘটনা কম ঘটলেও, বইমেলার সময় বা পরে যখন এই ফুটপাথের বইয়ের দোকানগুলো এগিয়ে এসে নিজেই এক বিকল্প বইমেলা প্রায়, তখন কেন যেন এমন ঘটত খুব। যদিও এখন তা ভারতীয় বাংলা জনপ্রিয় উপন্যাসের এক অলিখিত পসরায় পরিণত হয়েছে, সেই সময়ে, সেই প্রায় বছর কুড়িটি আগে, নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে এই অবস্থা ছিল না। তখন রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয় বইগুলোর কোনও কোনওটির বাংলাদেশে অযত্নে ছাপা সংস্করণ পাওয়া যেত। (এখন হয়তো পাওয়া যায়, তবে এগুলোর এক মান্য ও সম্পাদিত সংস্করণও আমাদের প্রকাশনার চাকচিক্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের অবস্থানও বদলে নিয়েছে।) একটার পাশে একটা, অথবা, একটারই অনেকগুলোÑ সাজিয়ে রাখা, গুছিয়ে রাখা, কখনও কখনও ছড়িয়েও রাখা। বইগুলোর দামও ছিল যেটাতেই হাত দেওয়া যাক, দশ টাকা। কখনও কখনও এর ভিতরে হঠাৎ উঁকি মারত মুক্তধারার কোনও পাৎলা বই—এক সঙ্গে অনেকগুলো; অথবা, অবিন্যস্ত। ওই দামেই তা বিক্রি হচ্ছে। যেটা নেওয়া যাক, দাম তার দশ টাকাই।
নীলক্ষেত থেকে বাংলা একাডেমির দিকে অগ্রসরমান একটি ফুটপাতের দোকানে একদিন দাঁড়াতেই দেখি, একসঙ্গে ছড়ানো অনেকগুলো (গুনিনি, গুনলে তা অনুমান আট-দশটি হত) জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা। সম্ভবত সেই ১৯৯৩-র ফেব্রুয়ারির কোনও এক সন্ধ্যার মুখে, পশ্চিমে হেলানো সূর্যের তীর্যক তীব্র আলো এসে পড়েছে ফুটপাতে—সেই আলোতে সাদা জমিনের ওপর একটি কালো আপেলের মতো ফল আঁকা প্রচ্ছদ। হাতে নেয়ার আগে একটু ঝুঁকে ভালো করে দেখি। হাঁ, সব ঠিক আছে, বইয়ের নাম, লেখকের নাম! কিন্তু এতবার শোনা বইয়ের এই প্রচ্ছদ? এইভাবে ছাপা? হাতে নিয়ে তাই বোঝার চেষ্টা করি। ওদিকে অন্য সময় যা হয়, দোকানির চোখ হয়তো থাকে ক্রেতার দিকে—যে বইটা কত যত্নে আর প্রয়োজন মনে করে দেখছে সে, তাই লক্ষ্য করেন, তারপর দাম জিজ্ঞাসা করলে দাম বলবেন, এক্ষেত্রে তার সুযোগ নেই বুঝেই হয়তো তিনি আমার দিকে দেখেন না, আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেন না, কোনওপ্রকার সংযোগ তার সঙ্গে আমার সঙ্গে রচিত হোক, তাও হয়তো চানও-না, অথবা, তা সবই তার কাছে অপ্রয়োজনীয়। কারণ, এই বইটির দাম তো বটেই, সে তো হাঁকছিল, ‘যেডা নেন, দশ টাকা’, ‘ধরলে নেন, দশ টাকা’, ‘ছাইল্যা নেন, দশ টাকা’, ‘দশ টাকারে দশ টাকা’। ফলে, যে কোনওটা দশ টাকার বইয়ের ভিতরে আলাদা হয়ে আসা এই বই, প্রায় দলছুট, অনুমোদিত প্রকাশনা জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা দশটাকা যেমন, একেবারেই অবহেলায় ছাপা গীতাঞ্জলি (কখনও বানান : ‘গীতাঞ্জলী’), শেষের কবিতা, নৌকাডুবি, বিদ্রোহী, বাঁধনহারা, চন্দ্রনাথ, দেবদাস—যে কোনওটাই দশ টাকা। বেশিও না, কমও না।
ততদিনে অবশ্য বাজার থেকে সত্যি উধাও হয়ে গেছে জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা। নতুন সংস্করণও বের হয়নি। পরে কথা বলে দেখেছি, আমাদের সাহিত্যিক বান্ধবকুলের প্রায় কেউই এই সংস্করণ দেখেনি, তাদের চোখে পড়ার আগে, বইয়ের দোকানে দিয়ে বেচাকেনার আগেই প্রকাশক সম্ভবত কোনও অজ্ঞাত করণে বইটি বাজার থেকে তুলে নিয়েছেন, অথবা, হতে পারে গুদামে থাকা সকল কপি বাজারে ছেড়ে দিয়েছেন। ফাল্গুন ১৩৯৪-এ প্রকাশিত (ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭? প্রকাশক : গোলাম মোস্তফা, হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৪১ ঢাকা স্টেডিয়াম, ঢাকা-১০০০।) বই, দাম পঁচিশ টাকা; ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩-এ বিক্রি হচ্ছে ১০ দশ টাকায়। এটি একমাত্র গুদাম শেষের বিক্রি ছাড়া সম্ভব না।
এইভাবে হাতে এল জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রথম সংস্করণ, দশ টাকায়। সেবারের বইমেলার আগে-পরে বাংলা একাডেমির দিকে আগুয়ান ফুটপাত থেকে।
২.
১৯৯১-এর জুন বা জুলাইয়ে আনওয়ার আহমদ সম্পাদিত গল্পপত্র রূপম এ আমার একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। গল্প লিখবার সেই প্রায় শুরুর দিকে রূপম এ গল্প ছাপাবার ইচ্ছা আর আকাক্সক্ষা আর সাহস কোনওটাই আমার ভিতরে জন্মায়নি, আমি জানি। লেখাটি ছাপা হয়েছিল একেবারেই সম্পাদকের ইচ্ছায়, আমার লেখার গুণে ততটা নয়। ওটাই ছিল রূপম এর শেষ লেটার টাইপে ছাপা সংখ্যা। সংখ্যাটি হাতে নিয়ে নিজের গল্পটা দেখি, কয়েকজন পরিচিত ও খ্যাতনামা গল্পলেখকের সঙ্গে আমার গল্প আর একইসঙ্গে আবিষ্কার করি আগে না পড়া দুজন লেখককে : একজন, শহীদুল জহির; অন্যজন, মামুন হুসাইন।
শহীদুল জহিরের লেখা এর আগে পড়িনি, নামও শুনিনি। মামুন হুসাইনেরও লেখা পড়িনি, কিন্তু নাম শুনেছি। রূপমের এই সংখ্যাটিতে প্রথম পড়লাম শহীদুল জহিরের গল্প : ‘আগারগাঁ কলোনিতে নয়নতারা ফুল নেই কেন’ (১৯৯১)। তখনও পর্যন্ত গল্পের নাম অমন হতে পারে, তা আমার ভাবনার অতীত, ওই পর্যন্ত প্রায় অপরিচিত এই গল্পের বয়ানের ধরনও : ‘আবদুস সাত্তার বাসায় ফিরছিল; তালতলায় বাস থেকে নেমে বিকেলের নরম আলোয় পায়ে হেঁটে যখন তার কলোনির বাসার দিকে আসছিল তখন কেউ কেউ তাকে দেখেছিল, যদিও শীর্ণ এবং কালো রঙের একজন মধ্য-বয়স্ক কেরানির অফিস শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তনের এই নিত্যদিনের ঘটনা তাকিয়ে দেখার মতো কিছু ছিল না।’ এই ছিল শুরুর বাক্য। পরে তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ (এই পর্বের প্রথম গল্পগ্রন্থ) ডুমুর খেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প এর প্রথম রচনা হিসেবে বইয়ে জায়গা পায়। বন্ধনীতে ‘এই পর্বের প্রথম গল্পগ্রন্থ’ এই জন্যে লেখা, শহীদুল জহিরের প্রথম গল্পগ্রন্থ পারাপার, যে বইয়ের লেখক হিসেবে তার নাম, শহীদুল হক; সেখানের গল্পগুলোর সঙ্গে বেশ পরে মিলিয়ে পড়তে গিয়ে দেখা গেল, এই বয়ান সেখানে পুরোপুরি অনুপস্থিত। শহীদুল জহিরের যে লেখকতার সঙ্গে পাঠক হিসেবে আমরা পরিচিত, কথাসাহিত্যিক হিসেবে তাঁর রচনার যে কৌশল ও আঙ্গিকে আমাদের যাতায়াত, পারাপার এ তা নেই। পারাপার-এর গল্পগুলো, যথা : ‘মাটি এবং মানুষের রঙ’, ‘তোরাব শেখ’, ‘পারাপার’, ‘ঘেয়ো রোদের প্রার্থনা নিয়ে’, এবং, ‘ভালোবাসা’—এর কোনওটিতে আখ্যান বয়ানে তাঁর যে পরিচিতি এক আপাত রহস্যময় জটিলতার সঙ্গে পরিচিত হই, তা নেই। ওই অর্থে কোথাও একথা খুব নিবিড়ভাবে না-পড়লে বোঝা যায় না যে, এই লেখক সহসা এমন পরিচিত ও প্রচল এক গল্পকথকের ভঙ্গি হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে প্রায় নতুন রচনাকৌশলের কাছে যাবেন। পারাপার এর গল্পগুলো যখনই রচিত হোক, বইটির প্রকাশ সাল জুন ১৯৮৫। এই দিক দিয়ে ভেবে নেওয়া যায়, আশির দশকের শুরু থেকে মাঝামাঝি সময়ে রচিত হয়েছে এই গল্পগুলো। হয়তো পারাপার প্রকাশিত হওয়ার আগে-পরে, যে কোনও সময়ে শহীদুল জহির দৈনিক সংবাদের সাহিত্য সাময়িকীতে পড়েছিলেন সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের ‘অলস দিনের হাওয়া’ নামের অনিয়মিত কলামের কোনও একটি কিস্তি; যেখানে লেখক জাদুবাস্তবতা এবং লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে কাহিনি-রচনার কৌশল নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, সম্ভবত গার্সিয়া মার্কেজের কোনও লেখার সূত্রে। একথা শহীদুল জহির পরে সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছেন। ওই ‘অলস দিনের হাওয়া’ পড়ে মার্কেজের রচনায় সেই সম্পর্কসূত্র খুঁজে হয়তো তিনি এ সময়ে এইভাবে গল্প বলার কৌশলকে রপ্ত করেছেন। এর প্রথম সার্থক প্রকাশ তিনি ঘটান পারাপার এর (১৯৮৫) পরে জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় (ফাল্গুন ১৩৯৪)। আর ওই প্রয়োগে, প্রথম বাক্যটি ঋত্বিক ঘটকের বহুখ্যাত চলচ্চিত্র মেঘে ঢাকা তারার প্রথম দৃশ্যের সঙ্গে একেবারে স্পষ্ট মিল ঘটিয়েও এই জীবনকে যাপন করার রাজনৈতিক বাস্তবতাকে ভিন্ন করে তোলেন অনুচ্ছেদহীন কাহিনিতে।
দেশভাগের ছবি মেঘে ঢাকা তারা। এই ছবিতে উদ্বাস্তু কলোনির মেয়ে নীতা (অভিনেত্রী : সুপ্রিয়া দেবী) ইস্কুলে পড়াতে যাওয়ার সময় ছবির প্রথম দৃশ্যে তার স্যান্ডেলের ফিতে ছিঁড়ে যায়। জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রথম বাক্যটিও তাই, আর তা গোটা উপন্যাসের সঙ্গে স্পষ্ট সঙ্গতিময় হয়ে উঠেছে : ‘উনিশ শ’ পঁচাশি সনে একদিন লক্ষ্মীবাজারের শ্যামপ্রসাদ চৌধুরী লেনের যুবক আব্দুল মজিদের পায়ের স্যান্ডেল পরিস্থিতিরি সঙ্গে সঙ্গতি বিধানে ব্যর্থ হয়ে ফট করে ছিঁড়ে যায়।’ নীতার স্যান্ডেলর ফিতেও ছিঁড়েছিল। তবে ফট করে কিনা বোঝা যায়নি। শহীদুল জহিরের বাক্যটি যত দ্রুত কাহিনির ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে গেল, একই স্যান্ডেল ছিঁড়লেও মেঘে ঢাকা তারায় নীতার ক্ষেত্রে যেন অত দ্রুত তা ঘটেনি, ঘটার সুযোগও তার ছিল না। সে থেমে পিছনে তাকিয়েছিল, স্যান্ডেলটা হাতে নিয়েছিল, তারপর চলতে শুরু করেছিল, বাড়ি থেকে আর-এক জোড়া স্যান্ডেল বদলে নেওয়ার উপায় তার ছিল না। দৃশ্যটি ছবির প্রয়োজনে একবারে শেষ দৃশ্যে আবার অন্য-একটি মেয়েরও স্যান্ডেল একইভাবে ছিঁড়ে যাবে, সেও একবার পিছন ফিরে তাকাবে, সামনে এগিয়ে যাবে—একটি পরিবারকে বাঁচাতে উদয়স্ত পরিশ্রমে বেঁচে থাকার ঝুঁকি নেবে। কিন্তু, জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় শহীদুল জহির দ্বিতীয় বাক্যেই একেবারে উলটো মোচড় দেন। সাধারণত এমন বাক্য কথাসাহিত্যে খুব একটা লিখিত হয় না : ‘আসলে বস্তুর প্রাণতত্ত্ব যদি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতো তাহলে হয়তো বলা যেত যে, তার ডান পায়ের স্পঞ্জের স্যান্ডেলের ফিতে বস্তুর ব্যর্থতার জন্য নয়, বরং প্রাণের অন্তর্গত সেই কারণে ছিন্ন হয়, যে কারণে এর একটু পর আব্দুল মজিদের অস্তিত্ব পুনর্বার ভেঙে পড়তে চায়। রায়সা বাজারে যাওয়ার পথে কারকুন বাড়ি লেন থেকে বের হয়ে নবাবপুর সড়কের ওপর উঠলে তার স্যান্ডেলের ফিতে ছিঁড়ে যায় এবং সে থেমে দাঁড়ায়।’
৩.
কিন্তু জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা পড়া তো একটু পরের কথা। ‘আগারগাঁ কলোনিতে নয়নতারা ফুল কেন নেই’র পরে রূপম এর পরের সংখ্যায় বছর দেড়েক বাদে বেরয় ‘কাঠুরে ও দাঁড়কাক’ (১৯৯২)। আর, এই থেকে বোঝা গেল, অথবা, এইবার একথা নিজেদের পড়াশোনার কাছেও ইঙ্গিতময় হয়ে উঠল, শহীদুল জহির তাঁর নিজস্ব গল্পকথনের ভঙ্গিটি হাতে তুলে নিতে পেরেছেন। কিন্তু যে কথা চাইলেই বোঝা যায় না, ধারণা স্থিরীকৃত হলেও লেখা যায় না, যতদিন-না লেখক তাঁর সচল কলমকে থামিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর গল্পের ধারাবাহিক পাঠকের কাছে তাই, এই পর-পর এক জোড়া গল্প পড়ার অভিজ্ঞতা থেকে একেবারে শেষ গল্পটি পর্যন্ত একথা খুব বুঝে নেয়ার সুযোগ হল : তাঁর বহুচর্চিত ভঙ্গিটি এই সময়ে তিনি রপ্ত করে নিচ্ছিলেন, তাঁর হাতে বেশ উঠে আসছিল, তিনি পর পরই (যেন খুব) সহজে তা কার্যকর করে তুলতে পারলেন। তাঁর বহুখ্যাত গল্পগুলো, যেমন : ‘ডুমুর খেকো মানুষ’ (১৯৯২), ‘মনোজগতে কাঁটা’ (১৯৯৫), ‘আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস’ (১৯৯৫) এর পর-পরই লেখা। এখনও পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে হয়তো গল্প হিসেবে এর চেয়ে প্রতিনিধিত্বশীল গল্প শহীদুল জহিরের আরও কয়েকটি নাম করা যায়, কিন্তু আঙ্গিক ও কাহিনি-বয়ান কৌশলের দিক দিয়ে ‘কুটির শিল্পের ইতিহাস’ সিদ্ধির খুব স্পষ্ট চূড়া ছুঁয়েছে। যে-কোনও গল্পেই তো তিনি কাহিনির বিভ্রম-লাগা এক ঘোরের সূত্রপাত ঘটান সূচনাতেই, গন্তব্য স্থিরীকৃত, লয় খুব ধীর, প্রায়শ গদ্যের গতি তীব্র আর লক্ষ্যাভিমুখী—কিন্তু পাঠক জানে না, এই শুরুতে প্রায় নিশ্চল কাহিনির একটি গতিশীল বাক্য তাকে কোথায় নিয়ে ঢুকে পড়েছে। আর কাহিনির পাক খাওয়া আর পেছনের পাক ছাড়ানো, ছড়িয়ে এগিয়ে যাওয়া, আবার পাক খাওয়া—এ তো চলতেই থাকে, কিন্তু তাতে তো পাঠকের কোনও ক্লান্তি হয় না, তিনিও পাকে পড়েও এগিয়ে যান। কোনও কোনও গল্প পড়তে পড়তে মনে হয়, এই পাক ছড়ানোর ও আবার জট পাকানো—এই করে কাহিনিকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার এ কৌশল তাঁর হাতে রপ্ত হয়ে উঠলে, শহীদুল জহির কাহিনির এই অজানা পরিণতির দিকে যেতে যেতে, লিখতে লিখতে পাঠককের তাতে কী ঘটছে আর ঘটতে পারে পড়ার সময় অথবা কী ঘটবে—আখ্যানের কাহিনি লিখতে লিখতে তিনি নিজেও এক প্রকার মজা পেতেন। সেই দিক থেকে, যা মনে হয়, ‘আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস’ তাঁর কৌশলের দিকে খুব সফল, হতে পারে পরিণততম গদ্যভঙ্গি— যেটি তিনি সচেতনেই ব্যবহার করেছেন, ওই গল্পের সঙ্গে খুব সহজে এঁটে গেছে। একথা শুধু গল্পটির আঙ্গিক নিয়ে, গল্প হিসেবে ওইটিই তাঁর সফলতম গল্প, একথা বলা হচ্ছে না।
কিছু উদাহরণ :
এক। ‘আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস’ (গল্পগ্রন্থ : ডুমুর খেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প) থেকে :
আমাদের মহল্লা, দক্ষিণ মৈশুন্দির শিল্পায়নের ইতিহাস আমাদের মনে পড়ে; মহল্লায় গরম পড়তে শুরু করলে চৈত্র, বৈশাখ অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসে তরমুজওয়ালারা তরমুজ নিয়ে আসে এবং আমরা তরমুজ খেতে শুরু করি, আমরা তখন তরমুজ সম্পর্কে সচেতন হই; আমরা লক্ষ্য করি যে, এই তরমুজওয়ালারা মহল্লার গলির সংকীর্ণ একটি জায়গায় মাটিতে দেয়ালের পাশ ঘেঁসে, গোলগোল তরমুজের ছোট ছোট ঢিবি বানিয়ে বসে, তারা এই জায়গায় কেন বসে আমরা বুঝতে পারি না, ফলে এই জায়গায় এসে রিকশা, ঠেলাগাড়ি, গরুর গাড়ি, বেবিটেক্সি, কুকুর, বেড়াল, ছাগল এবং মানুষ একটি জট পাকিয়ে ফেলে;....
দুই। ‘মনোজগতের কাঁটা’ (গল্পগ্রন্থ : ডুমুর খেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প) থেকে :
মহল্লার লোকেররা তখন এরকম আশা করতে থাকে যে, এ হয়তো অন্য কোনও সুবোধ, অন্য কোনও স্বপ্না, কিন্তু তাদের এই আশা নির্বাপিত হয়। তারা জানতে পারে যে, মহল্লায় যারা সুবোধ এবং স্বপ্নাকে দেখতে যায় তার তাদেরকে ঠিক চিনতে পারে না, কিন্তু তখন তারা স্বস্তিবোধ করলেও মনের গভীরে আসল বিষয়টি যেন তাদের জানা থাকে; এই বাইতে ভাড়া আইলেন ক্যালা? ভূতের গলির লোকের বলে যে, এই কথা শুনে মুখটি মলিন হয়ে আসে, তাদের বোধহয় এরকম মনে হয় যে, মহল্লার লোকেরা তাদেরকে পছন্দ করে নাই।
তিন। ‘ইন্দুর-বিলাই খেলা’ (গল্পগ্রন্থ : ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প) থেকে :
নমুনা ৭ : বিলাইয়ের নাম ডেঙ্গু।
তখন মহল্লায় ডেঙ্গু জ্বর দেখা দেয়, আমরা বুঝতে পারি মশা কেমন করে বিলাই হয়ে ওঠে এবং মানুষ তাদের ভয়ে ইন্দুরের মত দৌড়ায়; আমরা জানতে পারি যে, এডিশ মশা থেকে এই ছাতার রোগ হয় এবং এই রোগ হলে পশ্চাৎদেশ দিয়ে রক্ত বের হয়ে লোক মরা পড়ে। এই খবর শুনে আমাদের মায়েরা আমাদের জন্য খুবই দুশ্চিন্তা করে, তারা আমাদের বলে, সারা দিন ইন্দুর-বিলাই খেলচ, দেখচ না চাইর দিকে কেমুন ডেঙ্গু হয়া মনুষ মরতাছে; কিন্তু আমরা আমাদের মায়েদের এই যুক্তি বুঝতে পারি না যে, ইন্দুর-বিলাই খেলার সঙ্গে ডেঙ্গুর কি সম্পর্ক, ফলে আমরা তাদের পাত্তা দেই না, আমাদের খেলা জারি থাকে।
চার। ‘ডলু নদীর হাওয়া’ (গল্পগ্রন্থ : ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প) থেকে :
তৈমুর আলীর হয়তো মজা লাগে, সে এক কথায় রাজি হয় এবং ভিটার চারদিকে চক্কর দিয়ে ভিতরে ঢোকার ফাঁক খোঁজে। সে অন্ধকারের ভিতর কয়েকবার পাক খায় কিন্তু কোন ফাঁক ফোঁকরই দেখে না, তার মনে হয় যে, সমর্ত বানু কাছেই আছে, কিন্তু যখন সে বলে, আর লগে চালাকি করচ্ছে না? তখন সমর্ত বানুর কোন সাড়া পাওয়া যায় না। ফলে আহম্মদ তৈমুর আলীর রাগ এবং হতাশা বাড়ে। তারপর সে সত্যি কাঁটার বেড়ার তিনটা ফোঁকর খুঁজে পায় : যে রাস্তাটা ক্ষেতের ভিতর দিয়ে এসে ভিটায় উঠেছে তার পাশেই একটা ফোঁকর, দ্বিতীয়টা ভিটার পিছন দিকে এবং তৃতীয়টা ভিটার ডান পাশে নদীর দিকে মুখ করা; তিনটা ফোক্কর-ই এত ছোট এবং নিচা যে, তার মনে হয় কুত্তা কিংবা শিয়াল ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে এর ভিতর দিয়ে প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব। তথাপি, কথা মত তিনটা ফোকর ঠিকঠিক খুঁজে পাওয়ায় সে সমর্ত বানুকে বিশ্বাস করতে শুরু করে এবং তার মনে হয় যে, এখন তার কাজ হচ্ছে ফাঁদ পাতা নাই একটা পথ বেছে নেয়া অথবা আরো সহজ হয় ফাঁদ পাতা পথটা খুঁজে বের করে অন্য দুইটা নিরাপদ রাস্তার যে কোন একটা দিয়ে এগোনো। সে ভিটার মূল রাস্তার কাছে ঘাসের উপরে বসে একটু জিরায় এবং বলে, তিয়ো ওডি, আঁই আইর; তারপর সে তিনটা প্রবেশ পথের বিষয়ে দুই স্তর বিশিষ্ট শিকার-শিকারি খেলার একটা বিশ্লেষণ দাঁড় করায়—সে হয়তো রেঙ্গুন, পেগু অথবা মান্দালয়ে থাকার সময় এসব শেখে।
ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প শহীদুল জহিরের পরিণততম গল্পগ্রন্থ। আবার, সে কথা এক টানে বলাই-বা যায় কী করে? আগে উল্লেখ করা, ‘ডুমুর খেকো মানুষ’ বা ‘মনোজগতের কাঁটা’ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ গল্প। লেখকের সিদ্ধি সেখানে সবটুকু নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে, কৌশল ও আঙ্গিকগত যে নিরিখে শহীদুল জহির আমাদের সামনে প্রায় স্থিরীকৃত এক মডেলই প্রায়—সে সবই ওই বইয়ে আছে। তবু ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প পরিণততম, এই দুইয়ের ভিতরে। না, এমন তুলনা অপ্রয়োজনীয় : ‘মনোজগতের কাঁটা’ ভালো গল্প না ‘ইন্দুর বিলাই খেলা’; ‘আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস’ না ‘ডলু নদীর হাওয়া’? এটি পরিণততম বই, একটি গল্পগ্রন্থ হিসেবে, একথা এই জন্যে বলা যে, গল্পের ক্ষেত্রে ‘আগারগাঁ কলোনিতে নয়নতারা ফুল নেই কেন’ (১৯৯১) থেকে যেই শহীদুল জহির আখ্যান-কথনের এক ভঙ্গি নিজের কলমে তুলে নিতে সচেষ্ট হলেন, আর তাতে তাঁর সিদ্ধিও এল, নিজের সিদ্ধির দুর্গ তিনি ঠিক আগলে না-থাকলেও ওই মোক্ষম অস্ত্রটি বারবার ব্যবহার করেছেন, সেই-যে ব্যবহার করাটা, একই কৌশলকে চেঁচে-কুঁদে আদলকে ঠিকঠাক মিলিয়ে দেওয়াটা ডুমুর খেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্পে বোঝা যায়। সিদ্ধি হাতে এলে তাতে যাপন করেন লেখক, শহীদুল জহিরও তা করেছেন, কিন্তু যাপন করাটাও এক সময় নতুন নতুন অস্ত্রের সফল প্রয়োগে চোখে পড়ে না। ডুমুর খেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প এ কোথাও কোথাও চোখে পড়লেও ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প এ তা চোখে পড়ে না। কিন্তু আখ্যান বয়ানের তার অমলিন ভঙ্গিটি দুই বইয়েই এক। সেটা পুরোপুরি শহীদুল জহিরীয়। তা আছে তাঁর উপন্যাস মুখের দিকে দেখিতেও। জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা আর সে রাতে পূর্ণিমা ছিলর মাঝখানে লেখা উপন্যাস আবু ইব্রাহীমের মৃত্যুতে (প্রকাশ : ২০০৯) তা প্রায় নেই।
ডুমুর খেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প এর বেশির ভাগ গল্প রচনা কাল থেকে ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প এ তাঁর পরিণতিতম যাত্রার মাঝখানে আছে একটি উপন্যাস : সে রাতে পূর্ণিমা ছিল (১৯৯৫)। এই উপন্যাস, তাঁর লেখকতার দিকটি মনে রেখে যদি বলা যায়, এই দীর্ঘ কাহিনি পরিণত সফলতার মাঝখানের সেতুবন্ধ। নিজস্ব নির্মিতির পরাক্রমী দখলদারিত্ব অর্জনের সুযোগও তাঁর হাতে আসে এই থেকে। এই দিকটি মনে রাখলে ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প এর অর্জিত সাফল্যে পৌঁছান সে রাতে পূর্ণিমা ছিলর ধারাবাহিকতায়।
তবে, গল্পগ্রন্থ ধরে পারাপার থেকে ডুমুর খেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প হয়ে ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প-এর দিকে বিস্ময়কর যাত্রায় একটি স্মরণযোগ্য প্রবণতাও খুব চোখে পড়ে। সেটি যে কোনও গল্পে, উপন্যাসেও (সে রাতে পূর্ণিমা ছিল আর মুখের দিকে দেখি) নির্মিতির ছকটা শহীদুল জহিরের জানা থাকে। সিদ্ধির যে দুর্গের কথা বলা হল, এটা তা রক্ষার জন্যে নয়, শহীদুল জহিরের জন্যে তা অপ্রয়োজনীয় ছিল, হয়তো সিদ্ধির প্রচলিত ধারণাকেই তিনি অস্বীকার করতেন। খোলাসা করে বলা দরকার, কাহিনির প্রয়োজনে আখ্যানের এক আপাতজটিল নির্মিতি দিতে তাঁর অজ্ঞাতে এই প্রবণতা হাতে উঠে এসেছিল। তাঁর গল্প-উপন্যাসের চরিত্রের দিকে খুব মনোযোগে লক্ষ করলেই দেখা যায়, যে কোনও চরিত্রের বিকাশ সব সময়ই তাঁর ইচ্ছাধীন। কাহিনির শেষ পঙ্ক্তি পর্যন্ত (যেন) তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে যতি টানতেন। যাকে বলে চরিত্র বাহাদুর হয়ে কাহিনির নির্মিতিতে ক্ষমতা প্রয়োগ করা, চরিত্রের নিজের মতো নড়েচড়ে গন্তব্য স্থির করে নেয়া—সেই কাজটি তাঁর হাতে প্রায় কখনও ঘটেনি, কোনও গল্প-উপন্যাসেই না। ফলে, একটি গল্পের শুরু থেকে শেষ পঙ্ক্তি পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে, তা তাঁর ওই কাহিনিকে নির্মিতি দেয়ার ইচ্ছারই অংশ। অন্যদিক দিয়ে ভাবলে, যদি এই তীব্র কথাগুলোর বিপরীতে একটু নমনীয় হলে, ভাবা যায় ও বলা যায় : শহীদুল জহির জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা থেকে আখ্যানকে যে ভাবে ভাবতেন, যা ছিল তাঁর রচনার কৌশল, সেখানে চরিত্রের সেই বিকাশের সুযোগ কোথায়? সেই বিকাশ অর্থাৎ গল্প-উপন্যাসে যেভাবে চরিত্র কখনও কখনও লেখক আর পাঠকের সকল আকাঙ্ক্ষা আর ইচ্ছার মুখ মাড়িয়ে নিজেই এগিয়ে যায়। সেটি যে ঘটনা না, আর ঘটার সুযোগ নেই, শহীদুল জহিরের কলমের মুখ চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে বলেই বলা যায়, হয়তো তাঁর ইচ্ছাকৃত ছিল না, তাঁর কাহিনি-নির্মিতির প্রয়োজনেই ওইভাবে চরিত্রকে লেখকের হাতে রেখেই বর্ণিত হতে হত। কিন্তু এটাকে কোনও কৌশল হিসেবে ধরে নেওয়া যাচ্ছে না। যেভাবেই দেখি না কেন, তাঁর আখ্যানকার হিসেবে জাদুবাস্তবতার এই গাথায় এই একটি সুযোগই যেন বারবার হাতছাড়া হয়ে যেত। অথবা হয়তো, তা কখনও হাতে তুলে নেওয়ার চেষ্টাও করেননি তিনি।
৪.
ওই বাহাদুর হয়ে না-ওঠা চরিত্ররাও তো নিজেদের দৈনন্দিনতার ভিতরে নিজের মতো করে মহত্তর হয়ে ওঠে, একেবারে কেন্নো হয়ে লীন হয়ে যায়, হারিয়ে যেত যেতে ফিরে আসে, ডুবে যেতে যেতে ভেসে ওঠে, বেঁচে থাকার সমস্ত আগ্রহ হারিয়েও বেঁচে থাকে, প্রবলভাবেই বেঁচে থাকে। আন্তঃসম্পর্কে একেবারেই ভালোলাগাহীন হয়েও ভালোবেসে দিনান্তের অন্ধকারে সন্ধ্যাপ্রদীয় জালায়। মানুষকে নিয়ে এই দিনযাপনের প্রাত্যহিকতার গাঁথা রচনাই শহীদুল জহিরের মহত্ত্ব, তা-ই বারবার তাঁর রচনার কাছে নিয়ে দাঁড় করায়।
যেমন, এক অস্তাচলগামী সূর্যের বিকালে ছায়া দীর্ঘ হয়ে আসা ফুটপাতের কোলে জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রথম সংস্করণ দেখে দাঁড়িয়েছিলাম। হাতে নিয়ে দশ টাকায় কিনেছিলাম। সেদিনের সেই আগ্রহ কখনও লীন হওয়ার নয়। এখনও শহীদুল জহিরের যে কোনও রচনা পড়ার সময় ওই একুশে বইমেলার দিকে এগিয়ে আসা নীলক্ষেত ফুটপাতের বইয়ের দোকানের কোলের ছায়ার মতো তাঁর ছায়াও নিয়ত দীর্ঘতর হতে থাকে।








































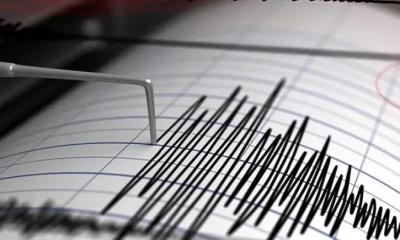







-20250327140635.jpeg)



