সনজীদা খাতুনের সমালোচনা/বিরোধিতার সঙ্গে রবীন্দ্রবিরোধিতার সম্পর্কটা পরিস্কার। আর রবীন্দ্রবিরোধিতার পেছনে অন্যতম কারণ রবীন্দ্রনাথ ‘হিন্দুকবি’, তার ওপর ভারতীয় (বিদ্বেসজীবীদের দৃষ্টিতে)। এজন্য তাঁকে ইসলাম-বিদ্বেষী প্রমাণ করার জোর চেষ্টা বহু আগে থেকেই চলমান। সেই চেষ্টায় তারা এখন সফলও বলা চলে। জ্ঞানে না, গুজবে এই অন্ধ সমাজে সবই ফলে!!
কিন্তু আসলেই কি রবীন্দ্রনাথ ইসলামবিদ্বেষী ছিলেন? মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন? তিনি কি ইসলামের নবী হজরত মুহাম্মদ (সা)কে কটাক্ষ করেছেন কোথাও? তিনি কি অত্যাচারী জমিদার ছিলেন? তিনি কি বর্তমান ‘বিদ্বেষজীবী মুসলমান কবিদের’ মতো ‘বিদ্বেষজীবী হিন্দু কবি’ (যদিও তিনি ব্রাহ্মধর্মের অনুসারী) ছিলেন?
এখন ধৈর্য ধরে আমার এই লেখাটা পড়তে হবে।
প্রথমেই বলে নিই, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুসলমান (কবি) ছিলেন না, এটা তো পরিষ্কার। এমনকি তাঁর সময়ে তার পূর্ববঙ্গের মুসলমান প্রজারা তাঁর সাহিত্যের টার্গেট পাঠকও ছিলেন না। কেননা তাদের অধিকাংশ ছিলেন নিরক্ষর কৃষিজীবী মানুষ। প্রত্যেক লেখক তাঁর সমাজ ও টার্গেট পাঠকের জন্য লেখেন। এই কারণে আল মাহমুদ, শামসুর রাহমানের সাহিত্যে হিন্দুসমাজ কম পাওয়া যাবে, নজরুলসাহিত্যে বৌদ্ধসমাজ পাওয়া যাবে না। এর মানে নজরুল বৌদ্ধবিদ্বেষী হয়ে যান না।
রবীন্দ্রনাথ জমিদারিত্বের ভার নিয়ে পূর্ববঙ্গে আসেন মাত্র ২৯ বছর বয়সে। ওই বয়সেই তিনি মুসলিম অধ্যূসিত পল্লি সংস্কারে যে অভূতপূর্ব উদ্যোগ গ্রহণ করেন তা আমাদের চিন্তার বাইরে। আমাদের বিদ্বেষজীবী লেখক-কবিরা রবীন্দ্রনাথের মতো একটা কবিতা/গান/গল্প লিখতে পারলেও পারতে পারেন—কিন্তু (মুসলিম) সমাজের জন্য ২৯ বছরের সেই তরুণ যা করছেন, সেইটা করে দেখানো তো দূরে থাক, বোঝার ক্ষমতা রাখেন কিনা সেই সন্দেহ থেকে যায়।
রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রে লিখেছেন: ‘আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে (যার অধিকাংশ মুসলমান) দেখলে ভারি মায়া করে—এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মতো—নিরুপায়। ... পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায় তখন এরা কেবল কাঁদতে জানে, কোনোমতে একটুখানি খিদে ভাঙলেই আবার সমস্ত ভুলে যায়। সোসিয়ালিস্টরা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধনবিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানি নে—যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তাহলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ ভারি হতভাগ্য।’ এজন্য তিনি বলেছিলেন, সাহাদের হাত থেকে শেখদের রক্ষার জন্যেই তাঁর শিলাইদহে আসা। সাহারা হচ্ছে মহাজন। জমিদারদের পক্ষ থেকে এরকম কথা আর কেউ কখনো বলেনি। রাশিয়ার চিঠিতে তিনি স্পষ্ট করে বলেন: ‘চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে, এই ছিল (জমিদার হিসেবে) আমার অভিপ্রায়।...জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর।..সমবায়নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না।’
গ্রামসমাজের উন্নয়ন নিয়ে তাঁর চিন্তাটা ছিল পরিষ্কার, আধুনিক এবং যুগোপযোগী। সেটার ধারণা আমরা পাই তাঁর ‘স্বদেশী আন্দোলন’ প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন: ‘স্বদেশী আন্দোলনের জন্য দেশের মন প্রস্তুত এবং সে কারণে ‘পঞ্চায়েত’, ‘গ্রাম্য সম্মিলন’, ‘পল্লীসমিতি’ প্রভৃতি স্থাপনা এখন একান্তই আবশ্যক। পল্লীর অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়-শিক্ষা-রাস্তাঘাট প্রভৃতি সম্পর্কে সমস্ত অভাবমোচনের ভার নিজেরাই গ্রহণ করা, আর কাহাকেও গ্রহণ করিতে না দেওয়া এটি ‘পল্লীসমিতির’ মূলনীতি। এইভাবে কিছুদিন কাজ করিতে পারিলে পল্লীর দুঃখী দরিদ্রদের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের যোগ সংস্থাপিত হইবে এবং একত্র হওয়ার সার্থকতা আমরা বুঝিতে পারিব।’
এই চিন্তা থেকে ওই তরুণ বয়সে তিনি তিনি গ্রামীণ সমাজের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন ‘শ্রীনিকেতন’। মধ্যবিত্ত বাঙালির সাংস্কৃতিক এবং মননগত বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বিশ্বভারতী বিদ্যালয়। তৎকালীন পূর্ববাংলা অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশে দরিদ্র প্রজাদের ভাগ্যোন্নতির জন্য তিনি সমবায় ব্যাংক, সমবায়নীতি ও কল্যাণবৃত্তি চালু করেন। সারা ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম চালু করেন হেলথ্ কোঅপারেটিভ্ সোসাইটি। অধিক ফলনের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন কৃষি ল্যাবরেটরি।
বাংলার কুটিরশিল্পের উন্নয়নেও কাজ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তার উদ্যোগে বয়নশিল্প শেখাতে শ্রীরামপুরে নিয়ে যাওয়া হয় একজন তাঁতিকে। স্থানীয় একজন মুসলমান জোলাকে পাঠানো হলো শান্তিনিকেতনে তাঁতের কাজ শিখতে। তিনি এসে খুললেন তাঁতের স্কুল। পটারির কাজেও হাত দেওয়া হলো একই সময়ে। রবীন্দ্রনাথ পুত্র রথীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে লেখেন: ‘বোলপুরে একটা ধানভানা কল চলচে—সেই রকম একটা কল এখানে (পতিসরে) আনতে পারলে বিশেষ কাজে লাগবে।...এখানকার চাষীদের কোন্ রহফঁংঃৎু শেখানো যেতে পারে সেই কথা ভাবছিলুম। এখানে ধান ছাড়া আর কিছু জন্মায় না। এদের থাকবার মধ্যে কেবল শক্ত এঁটেল মাটি আছে। আমি জানতে চাই চড়ঃঃধৎু জিনিসটাকে ঈড়ঃঃধমব রহফঁংঃৎু-রূপে গণ্য করা চলে কি না। একবার খবর নিয়ে দেখিস—ছোটখাট ভঁৎহধপব আনিয়ে এক গ্রামের লোক মিলে এ কাজ চালানো সম্ভবপর কি না। আরেকটা জিনিস আছে ছাতা তৈরি করতে শেখানো। সে রকম শেখাবার লোক যদি পাওয়া যায় তাহলে শিলাইদহ অঞ্চলে এই কাজটা চালানো যেতে পারে। নগেন্দ্র বলছিল খোলা তৈরি করতে পারে এমন কুমোর এখানে আনতে পারলে বিস্তর উপকার হয়। লোকে টিনের ছাদ দিতে চায় পেরে ওঠে না— খোলা পেলে সুবিধা হয়।’
পল্লীসংগঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি চালু করেন হিতৈষীবৃত্তি ও কল্যাণবৃত্তি। এই বৃত্তি থেকে সংগৃহীত অর্থ ব্যয় হতো রাস্তাঘাট নির্মাণ, মন্দির-মসজিদ সংস্কার, স্কুল-মাদ্রাসা তৈরি, চাষিদের বিপদ-আপদে সাহায্যসহ প্রজাদের নানামুখী উন্নয়ন কাজে। গ্রামীণ চাষিদের উন্নয়নে তিনি সমাজের সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের আহ্বান জানিয়ে বলেন: ‘আমার প্রস্তাব এই যে, বাংলাদেশের যেখানে হোক একটি গ্রাম আমরা হাতে নিয়ে তাকে আত্মশাসনের শক্তিতে সম্পূর্ণ উদ্বোধিত করে তুলি। সে গ্রামের রাস্তাঘাট তার ঘরবাড়ি পরিপাট্য, তার পাঠশালা, তার সাহিত্যচর্চা ও আমোদপ্রমোদ, তার রোগীপরিচর্যা ও চিকিৎসা, তার বিবাদ নিষ্পত্তি প্রভৃতি সমস্ত কর্মভার সুবিহিত নিয়মে গ্রামবাসীর দ্বারা সাধন করাবার উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করি।’
শিলাইদহে তিনি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং পতিসরে বড় হাসপাতাল তৈরি করেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ‘পতিসরে আমি কিছুকাল হইতে পল্লীসমাজ গড়িবার চেষ্টা করিতেছি যাহাতে দরিদ্র চাষী প্রজারা নিজেরা একত্র মিলিয়া দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য ও অজ্ঞান দূর করিতে পারে—প্রায় ৬০০ পল্লী লইয়া কাজ ফাঁদিয়াছি...আমরা যে টাকা দিই ও প্রজারা যে টাকা উঠায়..এই টাকা ইহারা নিজে কমিটি করিয়া ব্যয় করে। ইহারা ইতিমধ্যে অনেক কাজ করিয়াছে।’
‘মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল নিয়ে আল-বাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসীতে জল আনা একই কথা।’ পুত্রকে লেখা চিঠিতে এই কথা উল্লেখ করে সেই আমলে চাষের জন্যে পতিসরে কৃষকদের জন্য ট্রাক্টর নিয়ে আসেন, ভাবা যায়?
এখানেই শেষ নয়, নৌকাভর্তি নষ্ট ইলিশ সস্তায় কিনে চূন মিশিয়ে মাটিতে পুঁতে জৈবসার তৈরি করার ব্যবস্থা করেন। কবি রবীন্দ্রনাথ যে কৃষিকাজ সম্পর্কেও জ্ঞাত ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় একাধিক পত্রে।
কালীগ্রামে চাষ সম্পর্কে এক চিঠিতে তিনি জনৈক কর্মীকে লেখেন : ‘প্রজাদের বাস্তুবাড়ি, ক্ষেতের আইল প্রভৃতি স্থানে আনারস কলা খেজুর প্রভৃতি ফলের গাছ লাগাইবার জন্য তাহাদের উৎসাহিত করিও। আনারসের পাতা হইতে খুব মজবুত সুতা বাহির হয়। ফলও বিক্রয়যোগ্য। শিমুল, আঙ্গুর গাছ বেড়া প্রভৃতির কাজে লাগাইয়া তার মূল হইতে কিরূপে খাদ্য বাহির করা যাইতে পারে তাহাও প্রজাদিগকে শিখানো আবশ্যক। আলুর চাষ প্রচলিত করিতে পারিলে বিশেষ লাভের হইবে।’
ক্ষুদ্রঋণ নামের যে ব্যাংকিং ব্যবস্থা আজ দেখি ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পতিসরে সেটাই ‘পতিসর কৃষি সমবায় ব্যাংক’ নামে প্রতিষ্ঠা করেন। অনুরূপ না হলেও প্রায় কাছাকাছি চিন্তার জন্য একশ বছর পর ডক্টর ইউনুস ও গ্রামীণ ব্যাংককে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।
নোবেলের পুরস্কারমূল্য ছিল ১ লক্ষ ৮ হাজার টাকা। ১৯১৩ সালে এই টাকা কত টাকা আমাদের কল্পনার বাইরে। রবীন্দ্রনাথ পুরস্কারের প্রায় সিংহভাগ দিয়ে দিলেন পতিসরের কালীগ্রাম কৃষিব্যাংকে। বাকি যা থাকল, ঢেলে দিলেন বিশ্বভারতী তৈরির কাজে।
শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই কৃষিব্যাংক টিকিয়ে রাখতে পারেননি। পতিসরের গ্রামবাসীরা বলেন এই ব্যাংক চলেছিল ২০ বছর। ব্যাংকের খাতায় ২৫ বছর পর্যন্ত লেনদেনের হিসাব পাওয়া যায়। ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে গেলে, লগ্নির কোনো টাকা ফেরত পাননি রবীন্দ্রনাথ। এও উল্লেখ্য, ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেন ‘ট্যাগোর অ্যান্ড কোং’। ট্যাগোর লজ নামে কোম্পানির অফিস এখনো কুষ্টিয়া দেখা যাবে। এই কোম্পানি ন্যায্যমূল্যে চাষিদের ধান ও পাট কিনে বাজারে বিপণনের দায়িত্ব নেয়। সরাসরি বিপণনে অক্ষম প্রাথমিক উৎপাদকদের ন্যায়সঙ্গত পণ্যমূল্য পাওয়ার ব্যবস্থাস্বরূপ এটা ছিল অত্যন্ত জরুরি উদ্যোগ। শিলাইদহের কুঠিবাড়ি সংলগ্ন ৮০ বিঘা খাস জমিতে চালু করেন আধুনিক কৃষি খামার। এই হলেন তরুণ বয়সের রবীন্দ্রনাথ।
এখানেই শেষ নয়, ১৯০৬ সালে কৃষিবিদ্যা ও গোষ্ঠবিদ্যা শেখাতে তিনি পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পাঠান আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯০৭ সালে জামাতা নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকেও বিদেশে পাঠান কৃষিবিদ্যা পড়ার জন্য। তখন আইসিএস বা ব্যারিস্টার বানানো ধনী বাঙালি পরিবারের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, আর জমিদার রবীন্দ্রনাথ কি না পুত্র, জামাতা ও বন্ধুপুত্রকে চাষাবাদ শিখতে বিদেশ পাঠালেন! আমরা কিন্তু এই কৃষিবিপ্লবের কালেও সন্তানদের কৃষিবিদ্যায় উচ্চশিক্ষিত করে তোলার বিষয়ে উৎসাহী নই।
রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গের প্রজাদের জন্য, বিশেষ মুসলমান প্রজাদের জন্য যা কিছু করেছেন মানবিক কর্তব্যবোধ ও ভালোবাসার দায় থেকে করেছেন। ১৯৩১ সালে ৬ই সেপ্টেম্বর হেমন্তবালা দেবীকে লেখা একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লেখেন: ‘...একদিন আমার একজন মুসলমান প্রজা অকারণে আমাকে এক টাকা সেলামী দিয়েছিল। আমি বললুম, আমি তো কিছু দাবী করি নি। সে বললে, আমি না দিলে তুই খাবি কি। কথাটা সত্য। মুসলমান প্রজার অন্ন এতকাল ভোগ করেছি। তাদের অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি, তারা ভালবাসার যোগ্য।’
ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে তিনি ইন্দিরাকে লিখেছেন যে, একদিন পতিসরের মাঠে এক দরিদ্র প্রজা তাঁর পায়ের ধূলো নিতে আসে। প্রজাটি অসুস্থ। তার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথের পায়ের ধূলো নিলে তার অসুখ সেরে যাবে।
উল্লিখিত পত্র থেকে দুটি বিষয় বোঝা যায়: এক. তিনি মুসলমান প্রজাদের অন্ন ভোগ করার বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ উদাত্তচিত্তে প্রকাশ করেছেন; দুই. মুসলমান প্রজারা তাকে ঘৃণা নয়, ভালোবাসা থেকে গ্রহণ করেছে। তিনি প্রজাদের নিয়ে কতটা ভাবতেন তার নজির পাওয়া যায় অতুল সেনকে লেখা পত্র থেকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন: ‘কাজের সঙ্গে সঙ্গে একটি আনন্দের সুর বাজাইয়া তুলিতে হইবে। আমাদের গ্রামের জীবনযাত্রা বড়োই নিরানন্দ হইয়া পড়িয়াছে। প্রাণের শুষ্কতা দূর করা চাই। হিতানুষ্ঠানগুলিকে যথাসম্ভব উৎসবে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়ো। বৎসরে একদিন বৃক্ষরোপণ উৎসব করিবে। বৈশাখের শেষে কোনো একদিন ইস্কুলের ছুটি দিয়া সব ছেলেদের বনভোজন ও বৃক্ষরোপণ করিবার আয়োজন করিলে ভাল হয়। রাস্তা প্রভৃতির কাজ আরম্ভ করিবার প্রথম দিনটায় একটু উৎসবের ভাব থাকিলে এগুলো ধর্মকর্মের চেহারা পাইবে। আরেকটি কথা মনে রাখা চাই। চাষী গৃহস্থদের মনে ফুলগাছের সখ প্রবর্তন করিতে পারিলে উপকার হইবে। প্রত্যেক কুটিরের আঙিনায় দুই-চারিটি বেলফুল, গোলাপ ফুলের গাছ লাগাইতে পারিলে গ্রামগুলি সুন্দর হইয়া উঠিবে। দেশে এই সৌন্দর্যের চর্চা অত্যাবশ্যক একথা ভুলিলে চলিবে না।’
পারস্পরিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধের আরো কিছু নমুনা দেওয়া যায়। ১৯২২ সালে শেষবারের মতো তিনি শিলাইদহে আসেন। ২৪শে মার্চ শিলাইদহে পৌঁছান। দু সপ্তাহ ছিলেন। ২১শে চৈত্র গ্রামবাসীরা তাঁকে আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা জানান। মুসলমান নারীদের পক্ষ থেকে তাঁকে একটি নকশিকাঁথা উপহার দেওয়া হয়, যেটি বর্তমানে রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত আছে। প্রজারের পক্ষ থেকে মানপত্র রচনা করেছিলেন জেহের আলী বিশ্বাস। তিনি লেখেন: ‘আজ আমাদের কী আনন্দে দিন...সমস্ত প্রকৃতি যেন আজ শরবেণুরবে গাইছে-ধন্য হয়েছি মোরা তব আগমনে।’ মানপত্রের শেষ দিকে বলা হয়: ‘সমুদ্রমন্থন করিয়া একদিন দেবতারা অমৃত তুলিয়া অমর হইয়াছেন। আমরাও আজ আপনার জ্ঞানরূপ সমুদ্র ছেঁচিয়া তার মাঝখান থেকে অমৃতবাণী তুলিয়া মর্মে মর্মে গাঁথিয়া জীবনের কর্তব্যপথে অগ্রসর হব। কিন্তু শত পরিতাপের বিষয়, আমরা বিদ্যাহীন বুদ্ধিহীন; সে অমৃত তুলিতে আমাদের উপযুক্ত আসবাবের অভাব। তবে আজ আপনার ন্যায় একজন নায়কের শুভাগমনে যে আনন্দটুকু পেয়েছি, আর যতটুকু সাধ্য সাজাইয়া গুছাইয়া এই ক্ষুদ্র ঝুলিটি পূর্ণ করিয়া এই সোনার হাটের মধ্যে আনিয়া দিলাম, আপনার সুধামুখের সুধাবর্ষণ প্রার্থনা করিতে।’
রবীন্দ্রনাথ শেষবারের মতো পতিসরের আসেন ১৯৩৭ সালে (১০ শ্রাবণ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ)। একটি অভিনন্দন সভা অনুষ্ঠিত হয় কাছারি প্রাঙ্গণে। কালীগ্রাম পরগনার প্রজাবৃন্দের পক্ষে মোঃ কফিলদ্দিন আকন্দ রাতোয়ান অভিনন্দন পাঠ করেন। তিনি বলেন: ‘প্রভো, প্রভুরূপে হেথা আস নাই তুমি দেবরূপে এসে দিলে দেখা।/ দেবতার দান অক্ষয় হউক, হৃদিপটে থাক স্মৃতিকথা।’
তারপরও ‘অত্যাচারী জমিদার’, এই তো? অথচ তাঁকে তৎকালে অন্যান্য জমিদারদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার আবেদন জানাচ্ছেন এক ইংরেজ প্রশাসক। ১৯১৬ সালেই রাজশাহী জেলাগেজেটীয়ার-সম্পাদক এল. এস. এস. ও-ম্যালে, আই. সি. এস এক পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়ে জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের তাঁর জমিদারি এস্টেটকে কি রকম ওয়েলফেয়ার এস্টেটে পরিণত করেছিলেন : ‘It must not be imagined that a powerful landord is always oppressive and uncharitable. A striking instance to the contrary is given in the Settlement Officer`s account of the estate of Rabindranath Tagore, the Bengali poet, whose fame is world-wide. It is clear that to poetical genius he adds practical and beneficial ideas of estate management, which should be an example to the local Zamindars.
A very favourable example of estate government is shown in the property of the poet, Sir Rabindranath Tagore. The proprietors brook no rivals. Sub-infeudation within the estate is forbidden, raiyats are not allowed to sublet on pain of ejectment. There are three divisions of the estate, each under a Sub-manager with a staff of tahsildars, whose accounts are strictly supervised. Half of the Dakhilas are checked by an officer of the head office.’
‘জমিদার রবীন্দ্রনাথ’ যে মুসলমান প্রজাদের আত্মিক ও জাগতিক উন্ননি ও জাগরণে সদা তৎপর ছিলেন তার গুরুত্বপূর্ণ কিছু নজির আমরা এরই মধ্যে পেলাম। এবার ‘মানুষ রবীন্দ্রনাথ’ সম্পর্কেও জানার চেষ্টা করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যখন জমিদার নন, বা তার মুসলমানরা যখন তাঁর প্রজা নয়, তখন মুসলমানদের প্রতি তাঁর আচরণ কেমন ছিল? তিনি কি এড়িয়ে গেছেন? বা কারণে অকারণে বিদ্বেষ প্রকাশ করেছেন? নাকি মধ্যবিত্ত মুসলমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে নিশ্চুপ থেকেছেন? কয়েকটি নমুনা থেকে আমরা সেটা বোঝার চেষ্টা করতে পারি।
১৯১১ সালের নভেম্বরের শান্তি নিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয়ে একজন মুসলমান তাঁর পুত্রকে ভর্তি করার প্রস্তাব দেন। রবীন্দ্রনাথ মুসলমান ছেলেটিকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করে নেওয়ার জন্য সুপারিশ করে বিদ্যালয়ের শিক্ষক নেপালচন্দ্রকে একটি চিঠি লেখেন। নেপালচন্দ্রের নিকট থেকে উত্তর না পেয়ে তিনি পুনরায় ২রা নভেম্বর আরেকটি পত্রে লেখেন: ‘মুসলমান ছাত্রটির সঙ্গে একজন চাকর দিতে তাহার পিতা রাজী। অতএব এমন কি অসুবিধা, ছাত্রদের মধ্যে এবং অধ্যাপকদের মধ্যেও যাহাদের আপত্তি নাই তাঁহারা তাহার সঙ্গে খাইবেন। শুধু তাই নয়—সেই সকল ছাত্রের সঙ্গেই ঐ বালকটিকে রাখিলে সে নিজেকে নিতান্ত যূথভ্রষ্ট বলিয়া অনুভব করিবে না। একটি ছেলে লইয়া পরীক্ষা সুরু করা ভাল অনেকগুলি ছাত্র লইয়া তখন যদি পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়, সহজ হইবে না। আপাতত শাল বাগানের দুই ঘরে নগেন আইচের তত্ত্বাবধানে আরো গুটি কয়েক ছাত্রের সঙ্গে একত্র রাখিলে কেন অসুবিধা হইবে বুঝিতে পারিতেছি না। আপনারা মুসলমান রুটিওয়ালা পর্যন্ত চালাইয়া দিতে চান, ছাত্র কি অপরাধ করিল? এক সঙ্গে হিন্দু মুসলমান কি এক শ্রেণীতে পড়িতে বা একই ক্ষেত্রে খেলা করিতে পারে না?...প্রাচীন তপোবনে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাইত, আধুনিক তপোবনে যদি হিন্দু মুসলমানে একত্রে জল না খায় তবে আমাদের সমস্ত তপস্যাই মিথ্যা।’
তবে সে-যাত্রা রবীন্দ্রনাথের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। দশ বছর পরে বিদ্যালয়ের বিশ্বভারতী পর্বে সৈয়দ মুজতবা আলী প্রথম মুসলিম ছাত্র হিসেবে ভর্তি হন। উল্লেখ্য, সিলেট ব্রাহ্ম সমাজ, মহিলা সমিতি ও আনজুমানে ইসলামিয়া ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান থেকে আমন্ত্রিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৯১৯ সালে সিলেটে যান। সেখানেই সৈয়দ মুজতবা আলী প্রথম রবীন্দ্রনাথকে দেখেন। সৈয়দ মুজতবা আলীর বড়ো ভাই সৈয়দ মুর্তাজা আলীর স্মৃতিকথায় জানা যায়: চাঁদনি ঘাটে সিলেটের বনিয়াদী জমিদার পরিবারের-মজুমদার বাড়ি, কাজী বাড়ি (এহিয়া ভিলা) ও দস্তিদার বাড়ির প্রতিনিধিরা ঘোড়ায় চড়ে এসে কবিকে সংবর্ধনা করেন। কবি, মৌলবী আবদুল করিমকে নিয়ে বসেন এক সুসজ্জিত ফিটন গাড়িতে।
সৈয়দ মুজতবা আলীর বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনে তিনি রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্র লিখে বসেন। পত্রে রবীন্দ্রনাথের কাছে জানতে চান: ‘আকাঙ্ক্ষা করতে হলে কি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার?’
রবীন্দ্রনাথ আগরতলা থেকে সেই চিঠির উত্তর দেন। উত্তর পেয়ে সৈয়দ মুজতবা আলী তখন শান্তি নিকেতনে পড়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। প্রথম মুসলিম ছাত্র হিসেবে ভর্তি তো হলেনই, ১৯২১ সালে ১৬ই সেপ্টেম্বর বিশ্বভারতীর সম্মিলনী সভায় তিনি ঈদ উৎসব নিয়ে প্রবন্ধও পাঠ করলেন, তাও আবার রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে। এরপর ১৯২৩ সালে সৈয়দ মুজতবা আলীর সভাপতিত্বে বিশ্বভারতীর সম্মিলনী সভায় প্রাবন্ধিক রামচন্দ্র The little I know of Islam শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রসঙ্গক্রমে এও বলতে হয়, ১৯৩৫ সালে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে ঢাকা থেকে বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনের প্রবক্তা ও ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ’-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কাজী আবদুল ওদুদ শান্তিনিকেতনে নিজাম বক্তৃতায় অংশ নেন। বিশ্বভারতীর অর্থায়নে নিজাম বক্তৃতার আয়োজন করা হতো। আবদুল ওদুদ ছিলেন প্রথম বক্তা। ১৯৩৫ সালে ২৬-২৮শে মার্চ তিনদিন তিনি শান্তি নিকেতনে তিনটি বক্তৃতা দেন। তাঁর দুটি প্রবন্ধের বিষয় ছিল ‘মুসলমানের পরিচয়’ ও ‘হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ’। নিজাম বক্তৃতায় আমন্ত্রণ পাওয়া এবং উল্লিখিত বিষয়ে বক্তৃতাদানে অনুমতি প্রাপ্তি প্রসঙ্গে ওদুদ লিখেছিলেন: ‘হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ নিজাম বক্তৃতার বিষয়রূপে গণ্য ক’রে বিশ্ব-ভারতীর কর্তৃপক্ষ শুধু যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তা নয়, তাঁদের সুপরিচিত সজাগ মনের পরিচয়ও দিয়েছেন।...এই গুরু বিষয়ের আলোচনায় আমি অগ্রসর হয়েছি জ্ঞানের স্পর্ধায় নয়, দুঃখের তাড়নায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আনন্দিত আশীর্বাদে আমার সেই সামান্য প্রয়াস মহিমান্বিত হয়েছে।’
রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ অবস্থাতেও সভায় উপস্থিত হন। পঠিত তিনটি প্রবন্ধের সংকলন ‘হিন্দু-মুসলমান বিরোধ’ শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে, বিশ্বভারতী থেকে। বইটির ভূমিকাও লিখে দেন তিনি। ওদুদের প্রবন্ধপাঠে অংশ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন: ‘এদেশের হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের বিভীষিকায় মন যখন হতাশ্বাস হয়ে পড়ে, এই বর্বরতার অন্ত কোথায় ভেবে পায় না, তখন মাঝে মাঝে দূর দূরে সহসা দেখতে পাই দুই বিপরীত কূলকে দুই বাহু দিয়ে আপন করে আছে এমন এক-একটি সেতু। আবদুল ওদুদ সাহেবের চিত্তবৃত্তির ঔদার্য্য সেই মিলনের একটি প্রশস্ত পথ রূপে যখন আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছে তখনি আশান্বিত মনে আমি তাঁকে নমস্কার করেছি।’
পূর্ববাংলার প্রজা ও মুসলমান লেখকদের তিনি শুধু মানুষ হিসেবে নয়, মুসলমান হিসেবেও সম্মানের জায়গায় রেখেছেন। ইসলামের নবী ও ইসলামধর্ম সম্পর্কে তাঁর লেখাপত্র থেকে সেটি অনুধাবন করা যায়। তিনি কোনোভাবেই ইসলামবিদ্বেষী ছিলেন না, বরঞ্চ নিজে তো বটেই, পারিবারিকভাবেও ইসলামধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এই কথার প্রমাণক হিসেবে যৎসামান্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা সঙ্গত মনে করছি। হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে ১৯৩৪ সালের ২৫শে জুন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি বাণী পাঠিয়েছিলেন স্যার আব্দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দিকে। বাণীটি আকাশবাণীতে প্রচারিত হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: ‘ইসলাম পৃথিবীর মহত্তম ধর্মের মধ্যে একটি। এই কারণে উহার অনুবর্তিগণের দায়িত্ব অসীম, যেহেতু আপন জীবনে এই ধর্মের মহত্ত্ব সম্বন্ধে তাহাদিগকে সাক্ষ্য দিতে হইবে। ভারতে যে-সকল বিভিন্ন ধর্মসমাজ আছে তাহাদের পরস্পরের প্রতি সভ্য জাতিযোগ্য মনোভাব যদি উদ্ভাবিত করিতে হয় তবে কেবলমাত্র রাষ্ট্রীক স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা ইহা সম্ভবপর হইবে না। তবে আমাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে সেই অনুপ্রেরণার প্রতি, যাহা ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র ও মানবের বন্ধু সত্যদূতদিগের অমর জীবন হইতে চির উৎসারিত। অদ্যকার এই পূর্ণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে মস্লেম ভ্রাতাদের সহিত একযোগে ইসলামের মহাঋষির উদ্দেশ্য আমার ভক্তি-উপহার অর্পণ করিয়া ঊৎপীড়িত ভারতবর্ষের জন্য তাঁহার আশীর্বাদ ও সান্ত্বনা কামনা করি।’
বানীটির ইংরেজি পাঠও আছে। ইংরেজি পাঠটি রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছিলেন। বাংলা পাঠে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মোহাম্মদকে মহাঋষি হিসেবে অভিহিত করেছিলেন কবি। কিন্তু ইংরেজি পাঠে তিনি মহাঋষি শব্দটির অনুবাদ করেছিলেন ‘Grand Prophet of Islam’ হিসেবে।
১৯৩৩ সালের ২৬শে নভেম্বর নবী দিবস উপলক্ষ্যে একটি বাণী পাঠান রবীন্দ্রনাথ বোম্বের আনজুমানে আহমদিয়ার সম্পাদককে। সেখানে তিনি লেখেন: Message to the Secretary, Anjuman Ahmadiya, Bombay, on Prophet Day:
Islam is one of the greatest religious of the world and the responsibility is immense upon its followers who must in their lives bear testimony to the greatness of their faith. Our one hope of mutual reconciliation between different communities inhabiting India, of bringing about a truly civilized attitude of mind towards each other in this unfortunate country depends not merely on the realization of an intelligent self-interest but on the eternal source of inspiration that comes from the beloved of God and lovers of men. I take advantage of this auspicious occasion today when I may join my moslem brothers in offering my homage of adoration to the grand prophet of Islam and invoke his blessings for India which is in dire need of success and solace.
Rabindranath Tagore
26.11.1933.
দিল্লীর জামে মসজিদ থেকে প্রকাশিত The Peshwa পত্রিকার নবী সংখ্যার জন্য ১৯৩৬ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথের একটি বাণী পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ গ্রন্থে ভূঁইয়া ইকবাল সেই বাণীটি শান্তি নিকেতনের রবীন্দ্রভবনের অভিলেখাগার থেকে সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন। সেটিও তুলে দিচ্ছি:
Message for the Prophet Number of The Peshwa, Jama Masjid, Delhi.
I take this opportunity to offer my veneration to the Holy Prophet Mohammad, one of the greatest personalities born in the world, who has brought a new and latent force of life into human history, a vigorous ideal of purity in religion, and I earnestly pray that those who follow his path will justify their Noble faith in their life and the sublime teaching of their master by serving the cause of civilization in building the history of the modern India, helping to maintain peace and mutual goodwill in the field of our national life.
Rabindranath Tagore, Santiniketon
27th February 1936.
এছাড়াও উল্লেখ্য যে, শান্তিনিকেতন প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তিনজন ধর্মপ্রবর্তকের নাম উল্লেখ করেছেন। বয়স অনুসারে জ্যেষ্ঠ্যতা নির্ধারণ করে তিনি পর্যায়ক্রমে গৌতম বুদ্ধ, যীশুখ্রিষ্ট এবং হজরত মোহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে আলোচনা করেছেন। মোহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে লিখেছেন: মানুষের ধর্মবুদ্ধি খণ্ড খণ্ড হয়ে বাহিরে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাকে অন্তরের দিকে, অখণ্ডের দিকে, অনন্তের দিকে নিয়ে গিয়েছেন (মোহাম্মদ)। সহজে পারেন নি, এর জন্য সমস্ত জীবন তাঁকে মৃত্যুসংকুল দুর্গম পথ মাড়িয়ে চলতে হয়েছে, চারিদিকে শত্রুতা ঝড়ের সমুদ্রের মতো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে তাঁকে নিরন্তর আক্রমণ করেছে। মানুষের পক্ষে যা যথার্থ স্বাভাবিক, যা সরল সত্য, তাকেই স্পষ্ট অনুভব করতে ও উদ্ধার করতে, মানুষের মধ্যে যাঁরা সর্বোচ্চশক্তিসম্পন্ন তাঁদেরই প্রয়োজন হয়।
সবিস্তারে এই আলোচনার কারণ মূলত একটাই, প্রায় একশো বছর পরে এসে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করতে হলে আমরা যেন তাঁকে ও তাঁর সময়ের বাস্তবতা ভালোমতো জেনে তারপরে সেটা করি। ‘আমি মুসলমান, তিনি হিন্দু’—সমালোচনার জন্য এটুকুই যদি যথেষ্ট হয়, তাহলে অবশ্য আমার কিছু বলার নেই। সমালোচনার উর্ধ্বে অবশ্যই তিনি নন। রবীন্দ্রনাথ নবী না, কবি। তাও ফররুখ আহমদের মতো ‘মুসলিম রেনেসাঁ’র কবি না। তাঁর জীবন ও কর্মকে অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে আমাদের জন্য তিনি কোনো নীতিশাস্ত্র রচনা করে জাননি। সৃষ্টি করেছেন সাহিত্য, সংগীত, নাটক, কবিতা। যতটুকু বুঝি, একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমানের জন্য সেই পাঠ অপরিহার্য না। রবীন্দ্রসংগীত যার শোনারই তো কথা না, রবীন্দ্রনাথের সংগীতে তিনি ‘ইসলামধর্ম’ খুঁজবেন না বলেই আমার বিশ্বাস।
আর যিনি কট্টর মুসলমান না, তিনি রবীন্দ্রসাহিত্যে মুসলমান সমাজ খোঁজেন কেন? মানুষই তো খোঁজার কথা, তলস্তয়-দস্তয়েফস্কি, কিংবা হেমিংওয়ে-ফকনার পড়তে গিয়ে যেমনটি খোঁজেন। গোটা বিশ্ব রবীন্দ্রসাহিত্যে সেটাই খুঁজেছে। ইউরোপ-আমেরিকা-লাতিন আমেরিকা-পূর্ব এশিয়ার কথা বাদ দিলাম, প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় এখানে উল্লেখ করছি, রবীন্দ্রনাথ জীবদ্দশাতেই আরববিশ্বে রবীন্দ্রনাথ অনূদিত ও প্রশংসিত হয়েছেন। আরববিশ্বে, বিশেষ করে তুরস্ক এবং ইরানে তাঁর লেখার ভেতর সুফিবোধের অনুসন্ধান করা হয়েছে। ১৯২৬ সালের মে মাসের ২৭ তারিখ মিশর সফরে যান রবীন্দ্রনাথ। সফরকালে তিনি দেশটির প্রধান প্রধান কবি ও লেখকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রবীন্দ্র-অভ্যর্থনা এই পর্যায়ে যায় যে সেদিনের সংসদীয় অধিবেশন মুলতবি রাখা হয়। এরপর রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষ্যে মিশরের শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে রবীন্দ্রনাথের ওপর দেশটির সাতজন বুদ্ধিজীবীর লেখা ৭টি প্রবন্ধ নিয়ে একটি সংকলন বের হয়। মিশরের পর ইরানের রাজা রেজা শাহ’র বিশেষ আমন্ত্রণে তিনি ১৯৩২ সালে ইরানের তেহরান সফর করেন। একই বছর তিনি ইরাক সফর করেন। কয়েকজন প্রখ্যাত ইরাকি কবি তাঁকে উৎসর্গ করে কবিতাও রচনা করেন।
বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ শুধু যুদ্ধবিরোধী চেতনা, প্রেম ও শান্তির কথা প্রচার করেননি। পূর্ববাংলার বাউল গানে বৈশ্বিক পরিচিতি তৈরিতেও সক্রিয় থেকেছেন। গগন হরকরার ‘আমি কোথায় পাবো তারে, আমার মনের মানুষ যে রে’ এই গানের হুবহু সুরটা তিনি নিয়েছেন, সেটা আমরা জানি। নানাভাবে তিনি গগন হরকরার প্রতি তার ঋণ শোধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কথা অনেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, যেমন মুহম্মদ মনসুর উদ্দিনের ‘হারামণি’ সংকলনের ভূমিকা লিখতে নিয়ে গগনের এই গানের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। ফ্রান্সে গিয়ে ভারতীয় লোকধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে গিয়ে গগনের পরিচয় দিয়ে গানটির উল্লেখ করেন। হাসন রাজার গানের কথা তিনি ভারতীয় দর্শন মহাসভার অধিবেশনের ভাষণে বলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিবার্ট লেকচার দিলেন, সেখানেও হাসন রাজার গানের দার্শনিক ব্যাখ্যা দেন। লালনের গান তিনি সংগ্রহ ও প্রকাশ করেছেন। ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় ‘হারামণি’ বিভাগে তিনি গগন হরকরার ‘আমি কোথায় পাবো তারে’ গানটি ছাপেন। তিনি এই গানটির সুর গ্রহণ করে গানটির প্রতি তাঁর ভক্তির চূড়ান্তরূপ প্রকাশ করেন। একে একে লালনের কুড়িটি গান তিনি তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। লালনের গানের দুটি খাতা তিনি ছেঁউড়িয়া থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। তা এখন বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে আছে।
নিজের কিছু রচনার উপর বাউলের প্রভাব সম্পর্কে নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে লেখা এক চিঠিতে তিনি বলেছেন যে এসব ‘রবীন্দ্রবাউলে’র রচনা। ১৯০৯ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আলোচনাসভায় রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে লালনের কথা বলেন। ইন্ডিয়ান ফিলোসফিক্যাল কংগ্রেসে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেখানে ঐ ‘খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়’ গানটিতে ইংরেজ কবি শেলির কবিতার সাথে তুলনা করেন। নিজের ‘জীবনস্মৃতি’তে তিনি ‘খাঁচার ভেতর অচিন পাখি’ এই গানটির সুন্দর মরমি ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। লক্ষ করার বিষয়, রবীন্দ্রনাথের পোশাকটি হিন্দুয়ানি নয়। বাউলদের আদলে এই আলখেল্লা নামের পোশাকটি করেছিলেন তাঁর ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পোশাকটি তিনি আমৃত্যু পরেছেন।
রবীন্দ্রনাথ হিন্দু, এই তো? তাহলে পতিসরের একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করতে হয়। ঘটনাটি জানিয়েছেন আরেক কীর্তিমান বাঙালি অন্নদাশঙ্কর রায়। তখন তিনি রাজশাহীর ডি.এম.। রবীন্দ্রনাথ এলে তিনি পতিসরে দেখা করতে গেছেন। সেখানে একজন বৃদ্ধ মুসলমান প্রজা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মন্তব্য করেন: মহামানবকে আমরা দেখিনি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে দেখলে তেমনই মনে হয়।
তবু যারা ধর্মের নামে বুকে বিদ্বেষ ধারণ করেন তাদের জন্য রবীন্দ্রনাথই বলে গেছেন:
যে করে ধর্মের নামে
বিদ্বেষ সঞ্চিত
ঈশ্বরকে অর্ঘ্য হতে
সে করে বঞ্চিত।।
উল্লেখ্য, ১৯৪০ সালে, মৃত্যুর এক বছর আগে, সিরাজগঞ্জ সেবক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও ‘সেবক’ পত্রিকার সম্পাদক আবুল মনসুর এলাহী বক্স শান্তিনিকেতনে যান কবিগুরুর সঙ্গে দেখা করতে। রবীন্দ্রনাথ কাঁপা কাঁপা হাতে অটোগ্রাফ দিয়ে উল্লিখিত চরণগুলো লেখেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে যে দ্বন্দ্ব ও দ্বেষ তাতে মোটেও সুখী ছিলেন না, বরঞ্চ তার কঠোর ক্রিটিক ছিলেন। এ প্রসঙ্গে ময়মনসিংহের করিমগঞ্জের জুট রেজিস্ট্রেশনের সহকারী ইন্সপেক্টর কাজী আহমদকে লেখা চিঠিতে তিনি লেখেন: ‘ধর্ম যদি মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে খর্ব করে তার চেয়ে শোচনীয় কিছু হতে পারে না। যারা সর্ব মানুষের এক ঈশ্বরে যথার্থ বিশ্বাস রাখেন তারা কোনো কারণেই মানবকে অপমান করে নিজের ধর্মকে অপমানিত করতে পারে না। এই আমার মত। ক্ষুদ্র হৃদয় যাদের ঈশ্বরের সিংহাসনকে তারা সংকীর্ণ করে—এটা অপরাধ।
★ বই: ব্রাহ্মসমাজে ইসলাম, সাহিত্যে সক্রিয়তাবাদ ও অন্যান্য/ মোজাফফর হোসেন
প্রবন্ধ: রবীন্দ্রচেতনায় ইসলাম ও মহানবী`
বিদ্যাপ্রকাশ ২০২৫
নোট: কূটতর্ক ও কুতর্কে আমি নাই। যে কোনো সমালোচনা বিদ্বেষপ্রসূত না হোক, কামনা এইটুকুই।


















-20231109105053-20250402121817.jpg)





















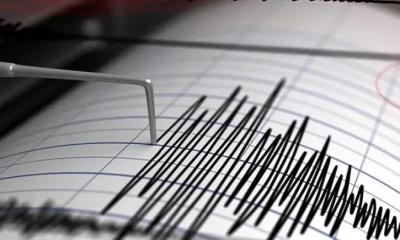







-20250327140635.jpeg)



