কাশ্মীর উপত্যকায় ১৯৭৩-এ জন্ম এই বাঙালি কন্যার। মদ্যপ সেনাকর্মী বাবার নিত্য অত্যাচারে চার বছর বয়সে মা তাদের দুই বোনকে নিয়ে চলে আসে মামার বাড়ি মুর্শিদাবাদ। আবারও বিয়ে করে মা, বড় হতে থাকে সৎবাবার সংসারে। ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় আচমকাই শেষ হয়ে যায় তার মেয়েবেলা।
একটা বাচ্চা মেয়ের যখন ফ্রক পরে খেলাধুলো করার কথা, তখন তাকে বসিয়ে দেওয়া হয় বিয়ের পিঁড়িতে। শেষ হয়ে যায় তার ‘শৈশব’, খেলার মাঝখান থেকে তাকে উঠিয়ে এনে মণ্ডপে একটা লোকের পাশে বসিয়ে দেওয়া হয়। কিছুই বুঝতে পারছিল না মেয়েটা, ভেবেছিল বোধ হয় কোনো পুজো হচ্ছে। তারপর তাকে বলা হলো যে ওই লোকটার সঙ্গে চলে যেতে হবে। তখন মেয়েটার মাত্র ১২ বছর বয়স, স্বামীর ২৬।
বিয়ের প্রথম রাত থেকেই শুরু হয় অত্যাচার। পতি দেবতাটির ধারণা, বউয়ের তো দুটোই কাজ, সন্তান ধারণ আর রান্না করা। কুড়ি বছর বয়সের মধ্যে মেয়েটি তিন সন্তানের জন্ম দিল। তখনই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সন্তানদের জীবন তার জীবনের মতো হবে না। ১৯৯৯ সালে, ২৫ বছর বয়সী তরুণী মা তার তিন সন্তানকে নিয়ে দিল্লিগামী একটি ট্রেনে উঠে বসেন।
-20210921094133.jpg)
দিল্লিতে এসে তিনি বিভিন্ন বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতে শুরু করলেন। একে অল্প বয়স তার ওপরে কোনো গার্জেন নেই, কাজের জায়গায় থেকেই নানা কুপ্রস্তাব আসতে লাগল। নানা বাড়ি ঘুরে শেষ অব্দি কাজ পেলেন প্রবোধ কুমারের বাড়িতে। অধ্যাপক কুমার ছিলেন মুন্সী প্রেমচন্দের নাতি।
বইয়ের তাক ঝাড়পোছ করতে গিয়ে মেয়েটি মাঝেই মাঝেই তাক থেকে পেড়ে আনতেন বই। কিছুক্ষণ বইয়ের পাতার ওপর চোখ বুলিয়ে আবার রেখে দিতেন যথাস্থানে। এই ঘটনা চোখ এড়ায়নি গৃহকর্তার, যাকে সে তাতুস বলে ডাকতেন। শব্দটির অর্থ বাবা, তিনিই তাকে এ নামে ডাকতে বলেছিলেন। একদিন তিনি বেবীর হাতে তুলে দেন তসলিমার লেখা আমার মেয়েবেলা।
“বইটা পড়ে আমার খুব ভালো লেগেছিল। মনে হয়েছিল, যেন আমার কথাই এখানে লেখা আছে,” বলছিল কাজের মেয়েটা।
এর কিছুদিন পর, দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে যাওয়ার আগে, নিজের ড্রয়ার থেকে প্রবোধ কুমার তাকে একটা ডায়েরি আর পেন দিয়ে যান। বলেন লিখতে। মেয়ে তো হতবাক…নিয়ে লিখবেন তিনি!
লিখলেন তাঁর হারানো শৈশবের কথা, লিখলেন তাঁর প্রথম সঙ্গমের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা, লিখলেন তেরো বছর বয়সের প্রসব যন্ত্রণার কথা, লিখলেন বছরের পর বছর ধরে নির্যাতনের ফলে শরীরে ফুটে ওঠা ক্ষতের কথা। লিখতে লিখতে ফিরে এল (বোনের) স্বামীর বোনের গলা টিপে ধরার অবদমিত স্মৃতি।
প্রায় কুড়ি বছর পর লিখছিলেন, প্রথম দিকে বানান, ব্যাকরণ নিয়ে একটু সমস্যা হচ্ছিল। কিন্তু একটু একটু করে পুরনো অভ্যাস মনে পড়ে গেল। আরো লিখতে থাকলেন। পরে বলছেন, “যত লিখতাম, ততই ভালো লাগত। মনে হতো যেন অনেক দিনের কোনো ভার আমার বুকের ওপর থেকে সরে যাচ্ছে।” প্রবোধ কুমার ফিরে এসে দেখলেন, একশ পাতার ওপর লেখা হয়ে গেছে!
এটাই বেবী হালদারের প্রথম বই – ‘আলো আঁধারি’। প্রথমবার পড়ে কেঁদে ফেলেছিলেন প্রবোধ। যে সমস্ত সাহিত্য-অনুরাগীদের লেখাটি দেখিয়েছিলেন তিনি, তাঁরা অনেকে ‘অ্যান ফ্রাঙ্কের ডায়েরি’র সঙ্গে তুলনা করেছিলেন লেখাটির।
বহু প্রকাশক নাকচ করে দেওয়ার পর, শেষ অব্দি কলকাতার একটা ছোট প্রকাশনী–রোশনি পাবলিশার্স – বইটি ছাপতে রাজি হয়।
“একদিন একটা বই দেখিয়ে তাতুস আমাকে বললেন, ‘এটা তোমার বই। তুমি এটা লিখেছ।’ ছাপা বই আমার সামনে হাজির! আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না!”
ঝাড়ুদার থেকে পরিচারিকা,পাশের বাড়ির অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা থেকে আধুনিকা কলেজ পড়ুয়া–বেবীর কাহিনি নাড়া দিয়েছিল সকলকেই। বইটির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন ঊর্বশী বুটালিয়া। ২০০৬ সালে বইটি বেস্ট সেলার তালিকায় ছিল। একুশটি আঞ্চলিক এবং তেরোটি বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে বইটি !
আরো দুটি বই লিখেছেন বেবী। লেখা তাঁকে দিয়েছে আত্মপরিচয়, যা আগে ছিলই না।
অর্থনৈতিকভাবে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মতো অবস্থায় পৌঁছে বেবী তাঁর তিন সন্তানকে (সুবোধ, তাপস, পিয়া) নিয়ে কলকাতায় থাকতে আরম্ভ করেন।
“এখন আমি বিশ্বাস করি, মানুষ সব পারে। আগে আমি পরিচারিকা ছিলাম। এখন আমি লেখিকা। আমি সবাইকে এটাই বলি যে, শুরু যেকোনো সময়েই করা যায়।”


-20210921094324.jpg)





































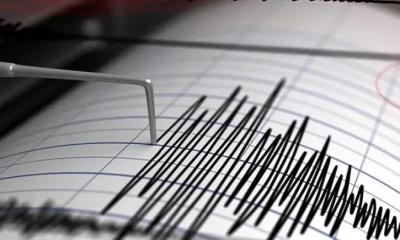







-20250327140635.jpeg)



