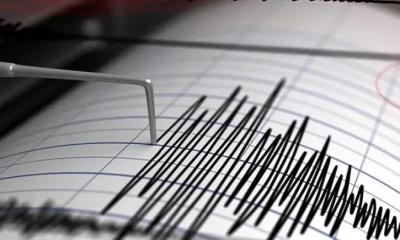যাদের কাছে সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত জেন্ডার বিশ্বকোষ আছে, তারা জানেন নারী অবদমনের প্রামাণ্য দলিল কাকে বলে। প্রতিটি পাতায় পাতায় অবদমিত নারীর জেগে উঠবার প্রাণপণ প্রয়াসের গল্প। ইট চাপা দেওয়া ঘাসের বিকাশ। এদের দেয়ালের ভেতরে, গণ্ডির ভেতরে, পা বেঁধে, শরীর ঢেকে, চোখে ঠুলি পরিয়ে, ধর্ম ও সমাজের ভয় দেখিয়ে কেমন করে বিকশিত হয়ে উঠবার পথ রুদ্ধ করা হয়েছিল, তারই নানান কথা জেন্ডার কোষের নারী পরিচিতির মাঝখানে। এখানে ২৩টা এন্ট্রি দেওয়ার সময় অবদমনের কত যে বিষয় জেনেছি, তা বলে শেষ করবার নয়। এই যেমন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে ১১৬৭-৬৮ সালে কেউ ভাবেনি একদিন নারী নামের দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ এখানে পড়াশোনা করতে আসবে। প্রায় সাতশ বছর পর মেয়েদের জন্য নির্মিত হয় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় নারীর জন্য পাঁচটি কলেজ। ১৮৭৮ সাল থেকে মেয়েরা এখানে পড়াশোনা করার সুযোগ পেলেও তারা কোর্স বা পড়াশোনা শেষ করে নামের শেষে ডিগ্রি লাগানোর সুযোগ পায়নি। এরপর দীর্ঘ আন্দোলন। সাফারজেট বা ভোটাধিকার আন্দোলনের মতো। আন্দোলন সফল হয়। বলা হয় ঠিক আছে মেয়েরাও বা নারী নামের দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ নামের শেষে ডিগ্রি বসাতে পারবে। সালেহা চৌধুরী এমএ বা মুনিরা পারভিন পিএইচডি। কিন্তু কেম নদীর ওপর ব্রিজ বানানো থেকে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম, সেই কেমব্রিজ একটু বেশি রক্ষণশীল। নারীদের এই দাবি অক্সফোর্ড মেনে নিলেও কেমব্রিজ মেনে নিতে সময় নিয়েছে। যার জন্ম ১২০০ সালে সেই বিশ্ববিদ্যালয় নারীদের ডিগ্রিধারী হতে বা নামের শেষে ডিগ্রি সংযুক্ত করতে ১৯৪৮ পর্যন্ত সময় নিয়েছিলেন। ভাবা যায় এমন কথা? পড়তে চাও পড় কিন্তু ডিগ্রিধারী হতে পারবে না। কারণ কী? ডিগ্রিধারী হলে তারা কি সব পুরুষ হয়ে যাবে? না তারা পুরুষদের সমকক্ষ হয়ে আর সন্তান প্রসব করতে চাইবে না? কারণ যা-ই হোক, এই হলো নারীর পড়াশোনার একধরনের ইতিহাস। পাক-ভারত উপমহাদেশে এসব ঘটনা নতুন নয়। আরব দেশের পুরুষ যেমন হেরেমে নারীদের ভরে রাখেন, যারা সর চন্দন মেখে পুরুষের মনতোষণের জন্য অপেক্ষা করেন এবং কোনোমতেই তারা যেন পুরুষের মতো পুরুষালি ব্যবহার না করেন, সেদিকে কঠোর কঠিন দৃষ্টি রাখা হয় তেমনই কোনো মনমানসিকতাই হয়তো এসবের পেছনে কাজ করে থাকে।
এখনো পড়াশনায় শানিত বা ব্যক্তিত্ব জাগরিত কোনো নারীকে কেউ পছন্দ করে না। বলে এরা পাকা বাঁশ। এদের ঠিক করা সম্ভব নয়। মানে নারীকে হতে হবে একতাল বেলে মাটি, না হলে থরথর কম্পমান বাঁশের কঞ্চি। বাঁশ হলেই ভাগ্য গেল। অনেক নারীও কিন্তু পুরুষদের এই ব্যাপারে কখনো সাহায্য করেন না জেনে।
ব্যক্তিত্বই নারীর সৌন্দর্য। সে বোন, মা ও জননী হতে পারে। সে ৯ মাস সন্তান ধারণ করে পৃথিবীতে আনতে পারে। কাজ থেকে এসে রান্না করতে পারে। যেমন ব্যাপার পুরুষের জন্য প্রায়ই অসম্ভব। এমন কঠিন কাজ করতে পারার নারীকে কেউ কেউ বলেন, উইকার সেক্স। একজন বলেছিল, উইকার সেক্স মাই ফুট। আসলে পুরুষই উইকার সেক্স। কখনো হুংকারে বস হতে চায় না হলে এমন শিশু যিনি এক গ্লাস পানি ঢেলেও খেতে পারেন না, আর এসব শিশুর কেউ কেউ আঁচলে ঢেকে রাখেন। যেমন শরৎচন্দ্রের বেশির ভাগ নায়িকা।
নারী অবদমনের বড় গল্প চীন দেশে। যেখানে হাজার হাজার বছর ধরে নারীর পা দুটো এমন শক্ত করে বেঁধে রাখা হতো, যারা সেই বাঁধা পা নিয়ে বাড়ির উঠানও পার হতে পারতেন না। এক হাজার বছরের বেশি দিন ধরে প্রায় এক বিলিয়ন নারী এই কাজ করেছেন। যদি সে পা বেঁধে না রাখে তার ভালো বিয়ে হবে না, তার ভাগ্য হবে মুটে মজুরের মতো। সেটা অবশ্য কেউ চায়নি। কেউ কেউ বলেন এটা শুরু হয়েছিল যিশুখ্রিষ্টের জন্মের আগে থেকে। আবার কেউ কেউ বলেন ৯৬০ সালে ইউ লি নামের এক নারী, সম্রাটের অগণিত কংকাবাইনের একজনের পা নাকি ছিল ছোট, ফুলের মতো। পরে সেই পা দুটোকে সৌন্দর্যের মাপকাঠি মনে করে সমস্ত মেয়ের পা বেঁধে রাখার রীতি প্রচলিত হয়। ১২৭৩ সালে মোঙ্গল যখন চীন দখল করে তারা এই নিয়মে অত্যন্ত খুশি হয়। কারণ, চীনের কোনো মেয়েই তাদের ছোট পা নিয়ে মোঙ্গলদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইবে না।
কত বছর বয়স থেকে এই পা বাঁধা শুরু হয়? চার পাঁচ ও ছয় বছর বয়স থেকে। যখন পায়ের হাড় কোমল এবং কঞ্চির মতো নরম তখনই শুরু হয় এই পা বাঁধা পর্ব। প্রথমে পা দুটোকে গরম পানিতে ধুয়ে, বেশ করে ম্যাসাজ করা হয়। তারপর সেখানে কোনো বিশেষ সুগন্ধি মাখানো হয়। পবিত্র প্রাণীর রক্ত এবং ভেষজ পাতা দিয়ে পা দুটোকে যত্ন করা হয়। এরপর পায়ের নখ যতটা সম্ভব ছোট করে কাটা হয়। এগুলো কখনো যেন বড় হতে না পারে। এরপর মা বা নানি-দাদি সেই শিশুকে যত্ন করে কোলে বসিয়ে পুট পুট করে তার পায়ের আটটি কোমল আঙুলের হাড় ভেঙে দেয়। এরপর ভাঙা পায়ে পরাবেন শক্ত ব্যান্ডেজ। সেই ব্যান্ডেজ পবিত্র রক্ত ও ভেষজ পাতার আরকে মেশানো। দুই বছর পর সেই ব্যান্ডেজ খোল এবং আরও শক্ত করে বাঁধো। ক্রমাগত যন্ত্রণার ভেতর সে চলাফেরা করবে। যে নখ কখনো বড় হবে না বলে কেটে ফেলা হয়েছে, তা বড় হয়ে তার পায়ের পেছনে গিয়ে বড় বড় ক্ষত সৃষ্টি করবে। পায়ের মাংস পচতে পচতে, দুর্গন্ধে ভরে যাবে। একসময় পা দুটো ছোট হয়ে এক অসাড় বস্তু হয়ে উঠবে। দীর্ঘ কয়েক বছর যন্ত্রণাকাতর মেয়ে নিজের পচা পায়ের গন্ধ শুঁকে জীবন কাটাবে। মাঝে মাঝে কেবল ব্যান্ডেজ খুলে শক্ত করে ব্যান্ডেজ বাঁধা হবে। এ ঘটনায় কেউ কেউ সেপটিক হয়ে মারা যাবে। কিন্তু তাতে কি? বড়লোক বা সম্ভ্রান্ত মানুষের সঙ্গে যদি তার বিয়ে না হয় তাঁর মেয়ে হয়ে জন্মানোর সার্থকতা কোথায়? সেই সময় ছেলের মা মেয়ে দেখতে এসে দাঁত, চোখ, নাক, কান দেখার আগে কাপড় তুলে দেখবে মেয়ের পা বাঁধা আছে কি না। যদি না থাকে পত্রপাঠ বিদায়। ফলে এসব মেয়ের বিয়ে হওয়া একটা অসাধ্য ব্যাপার হবে।
১৬০০ সালে মাংচু ডায়নেস্টির সময়ে চেষ্টা করা হয়েছিল মেয়েদের পা বাঁধা রীতি বন্ধ করে ফেলতে। তারা সক্ষম হননি। এরপর চীনের রানি জু সি স্বজাতির প্রতি দয়া অনুভব করে মেয়েদের পা বাঁধা রীতি চিরতরে বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, তিনিও সক্ষম হননি। এই রানির সময়কাল ১৮৩৫ থেকে ১৯০৮। ১৯১১ সালে সান ইয়াৎ সেন কঠোরভাবে এই নিয়ম বন্ধ করেন। তিন ইঞ্চি সোনার পদ্ম হয়ে উঠতে একজন নারীকে যে অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়, তা নিয়ে একজন চীনের নারী একটি গ্রন্থ লেখেন। দুঃখ করে বলেছেন, এত কাণ্ডের পর দেখা গেল তাঁর স্বামী একজন আফিমসেবী। যিনি জীবনে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাননি, তিনি কী করে স্ত্রীর পায়ের দিকে তাকাবেন? ঝু গুইজন যখন বই লেখেন তিনি তখন বেঁচে। ওয়াং লাইফেন নামের একজন লিখেছেন এখনো মনে আছে যখন আমার পায়ের আঙুল মুট মুট করে ভেঙে ফেলা হয়েছিল। কী অসহ্য সে যন্ত্রণা। মজার ব্যাপার কিং ডায়নেস্টির পর্নোগ্রাফিক বইতে এই বাঁধা পা দুটো নিয়ে কত বড় মজা করা যায়, সে নিয়ে নানা সব কথা লেখা আছে। প্রায় ৪৮টি যৌনক্রীড়ার কথা আছে। বলা হয়েছে, কত ভাবে এই তিন ইঞ্চির পাকে যৌনক্রীড়ার সময় আনন্দ দেওয়া যায়। পড়তে পড়তে বমি আসে। কিন্তু এই ছিল চীনের মেয়েদের জীবনের ভযাবহ সত্য। আজকের দিনের ইয়াসনুরি কাওয়াবাতা ‘দ্য হাউস অব স্লিপিং বিউটিতে’ আর একধরনের আনন্দের কথা বলেছেন। কোনো কোনো বেশ্যালয়ে অল্পবয়স্ক নারীদের ঘুমপাড়ানি ওষুধে দীর্ঘ সময়ের জন্য ঘুম পাড়িয়ে নিশ্চিন্তে তার সঙ্গে যৌনক্রীড়ায় মগ্ন হন পুরুষ। এর ভেতর কেউ কেউ মারা যায়। ছোট উপন্যাস শেষ হয়েছে এইভাবে। একজন পতিতালয়ের ম্যাডাম বলছেন—তাতে কি, মেয়েটি মারা গেছে? আর একটা মেয়ে তো আছে। এই হলো চীনের মেয়েদের গল্প।
আমাদের দেশের সতীদাহের কথা আমরা জানি। বাল্যবিবাহ নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন বিদ্যাসাগর। এসবও আমাদের জানা। পর্দাপ্রথার ভয়াবহতাও জানা আছে সবার। এসব কিছুই কি নারীকে অবদমিত করে রাখবার জন্য নয়?
ব্রিটেনের দীর্ঘ রাজকবির ইতিহাসে একজন নারীর রাজকবি হতে অনেক সময় লেগেছিল। ১৬০৬ সাল থেকে রাজকবি পদ তৈরি হয়। দীর্ঘদিন পরে কারোল আন ডাফি রাজকবি হয়েছিলেন ২০০৯ সালে। দশ বছরের জন্য। তিনি কমটেম্পোরারি সাহিত্যের অধ্যাপিকা ছিলেন। যখন এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং (১৮০৬ সালে জন্ম) এর নাম উঠেছিল তিনি হতে পারেননি। বর্তমানের রাজকবি আন্ড্রুমোশনের সময় রাজকবি হবেন বলে প্রথমবারের মতো ওয়েন্ডিকোপের নাম বেশ জোরেশোরে উচ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু তিনি রাজকবি হতে পারেননি। বর্তমান রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ তাকে রাজকবি হতে বাধা দিয়েছিলেন। অবদমনের কারণ একজন নারীর জন্য কেবল একজন পুরুষ নয়, একজন নারীর অবদমনের কারণ আর একজন নারীও হতে পারে। নানা মর্মান্তিক ঘটনা হয় একজন নারীর জীবনে অন্য সব নারীর ভূমিকায়। আমেরিকাতে আজ পর্যন্ত একজন নারী প্রেসিডেন্ট হননি।
ড. হুমায়ুন আজাদের ‘নারী’ গ্রন্থে এমনি অনেক নারী অবদমনের কথা আছে। বোভেয়ারের সেকেন্ডসেক্স এমনি ঘটনার কথা বলে। মধ্যপ্রাচ্যে বা আফ্রিকার নানা দেশে নারীদের খৎনা করবার রীতি এই প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে। আমার মনে হয় এই রীতির কথা সবাই জানেন। কী ভয়াবহ ব্যাপার। অনেক আগে পশ্চিমের কোনো দেশে স্বামী যুদ্ধে বা বাইরে যাওয়ার সময় নারীকে চেস্টটিটি বেল্ট পরাতেন। যেন নারী সতী থাকে। চাবি থাকত স্বামীদের পকেটে। বলা বাহুল্য, স্বামীদের বেলায় এমন কোনো চেস্টটিটি বেল্টের প্রয়োজন ছিল না। ব্রিটেনে আজকের দিনেও অনেক বাঙালি নারীকে স্বামী কাজে যাওয়ার সময় ঘরে তালা দিয়ে রাখেন। এমন এক লন্ডনি কন্যার গল্প নিয়ে আমার উপন্যাস ‘একজন জুশনারার গল্প।’ এমন গল্প কখনো শেষ হবে না।
দীর্ঘদিন ইউরোপে ডাইনি বলে মেয়েদের পুড়িয়ে মারা হয়। যে নারীকে বিয়ে করতে রাজা সপ্তম হেনরি চার্চ অব ইংল্যান্ড সৃষ্টি করেছিলেন একদিন সেই এ্যান বোলিনকে ডাইনি ঘোষণা করে জেন সেমুরকে বিয়ে করেন তিনি। ডাইনি কেন? এ্যান বোলিনের হাতে নাকি একটি বাড়তি আঙুল ছিল। তিনি আরও বলেছিলেন এ্যান বোলিনের ¯তন নাকি তিনটি। এমনি নানা অভিযোগ। ইউরোপ বা ভারত যেই দেশই হোক নারী সংগ্রামের ইতিহাস দীর্ঘ। ভোটদান করবার দীর্ঘ ইতিহাস বা সংগ্রাম এই প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে। ইউরোপ, আমেরিকা বা ভারতের নারী ভোটাধিকার। কতই না সংগ্রাম করতে হয়েছে ভোট দেবার অধিকারে।
বর্তমান ব্রিটেনের অনার কিলিংয়ের কথা জানি। যেসব পাকিস্তানি বা মুসলিম দেশের মানুষ ব্রিটেনে বসবাস করেন, তাদের মধ্যেই এমন ব্যাপার ঘটেছে। মেয়ে বড় হয়ে যখন পশ্চিমি রীতিতে জীবনযাপন করতে চায় তখনই শুরু হয় এই অনার কিলিং নামের খুন। কেন সে অবরোধবাসিনী হয়ে থাকতে চায় না। কেন সে নিজের ইচ্ছামতো বেঁচে থাকতে চায়, স্বামী নির্বাচন করতে চায়। বাবা মেরে ফেলছে মেয়েকে, ভাইয়েরা মেরে ফেলছে বোনদের। মা পর্যন্ত এ ব্যাপারে ছেলেকে সাহায্য করে বলছে, ডরাও নাহি বেটা এ ইজ্জত কা সওয়াল হ্যায়। এমন কিছু মেয়ের লাশ গুম করে ফেলা হয়েছে। যাদের আর কোনো খোঁজ জানে না কেউ। কাউকে পাওয়া যায় মাটির তলায়। কেউ নিজ বাড়িতে মারা যায়। এক পাঞ্জাবি শিখ বাবা মেয়েকে মেরে ফেলে হাওয়া। মেয়ের হাতের ভেতর ছিল বাবার দাড়ির কিছু চুল। সেটার ডিনএনএ করে দেখা গেল দাড়িটা কার। অনার কিলিং ব্রিটেনের এমন একটি অপরাধ পুলিশ পর্যন্ত হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে এসব সামলাতে। বাবা মায়ের যুক্তি তারা মেয়েকে এবং তাদের নিজ পরিবারকে দোজখের আগুন থেকে বাঁচাতে সাহায্য করছে।
নারী নির্যাতনের কারণ হিসেবে একজন বলেছিলেন ঈশ্বর পুরুষের বাঁকা হাড় দিয়ে নারীকে তৈরি করেছিলেন। ফলে নারী বাঁকা। তাকে সোজা রাখতে বা ঠিক পথে রাখতে তাকে শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন। ইসলামেও হালকাভাবে মারার কথা আছে।
খনা নামের একজন বিদূষী নারীকে জিব কেটে ফেলতে হয়েছিল একদিন। শশূরের চেয়ে নাকি খনা অধিক বিদ্বান হয়ে হয়ে উঠছিল। আজও কি নারী পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারছে। তার সমস্ত সম্ভাবনা কি আজও পূর্ণতা পাওয়ার মতো সত্য হয়ে ওঠে? জানি না।
একবার নবনীতা দেবসেন তার এক ইংরেজি প্রবন্ধে বলেছিলেন যখন নারী লেখে বা সাহিত্যকর্ম করে স্বামী অবাক হয়ে বলেন, ওর মতলবটা াক? এসব লিখে কী পেতে চায় ও। আর ছেলেমেয়েরা বলে, আমার মা অন্য মায়ের মতো না। তারপরেও নারী লেখে, নোবেল পায়। আশার কথা। আবার কোনো কোনো স্বামী স্ত্রীকে নিয়ে গর্বও করেন। সেটাও সত্য। তাহলে কি বলব নারী সংগ্রামের দীর্ঘ টানেলে কিছু আশার আলো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তবু নারীর সাহিত্য আজও কি দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষের সাহিত্য নয়। সেই কারণে কেউ খুব ভালো লিখলে বলা হয়, বেশ লেখেন তিনি। একেবারে পুরুষের মতো লেখেন। নারী তার সংবেদনশীলতায় ও স্পর্শকারতায় অনেক বেশি দেখতে পান, অনেক গভীরে যাওয়ার ক্ষমতা থাকে। নারীর এই ‘পারসেপশন’ অনেক সময় পুরুষ লেখকদের থাকে না। নারীর এই বিশেষ ক্ষমতা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা যায়। তাকে যে পুরুষের মতোই হয়ে উঠতে হবে, পেশল ও বলবান তার কি খুব প্রয়োজন আছে? লেখার প্রধান কথা ম্যাচুরিটি। সেটা থাকলে এরপর তাঁর লেখা পেশল হলো কি না, সে নিয়ে ভাববার তেমন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। নোবেলের দীর্ঘ ইতিহাসে ১১৪ জন সাহিত্যে নোবেল পেয়েছেন। সেখানে নারীর সংখ্যা ১৪। এত দিনে আরও বেশি নারী কি পেতে পারতেন না? নারীর ভাগ্য এসবে থেমে থাকবে এমন ভাবতে পারি না। তাকে এগোতে হবে। অবদমনের দীর্ঘ রাস্তা ভেঙে। ভার্জিনিয়া উলফের লেখায় নারীর পথ ভাঙার কথা আছে। তিনি অবশ্যই একজন শক্তিশালী নারী লেখক। যাকে এখনো সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।
নারীর অধিকারে অনেক আইন প্রণয়ন হয়েছে। দেশে ও বিদেশে। তবু কি নারী তার সমস্ত অধিকারে একজন পূর্ণ মানুষ? তার নামের আগে মেয়ে না বললে আমরা কি তাকে নারী হিসেবে চিনতে পারি। ইংরেজিতে বলে ওম্যান। ও মানে দুঃখ-কষ্ট। মনে হয় ওম্যান বলার সময় হয়তো বিবি হাওয়ার কথা মনে হয়েছিল অনেকের। আদমকে স্বর্গচ্যুত করেছিল যে নারী। কিন্তু কে স্বর্গচ্যুত করেছিল তার উত্তর কাজী নজরুল ইসলাম দিয়ে গেছেন, এ ব্যাপারে প্রসঙ্গ দীর্ঘ করবার প্রয়োজন নেই।
খালেদ হোসেনি তার ‘আ থাউজেন্ড স্লেনডিড সান’ নামের বিশাল কলেবরের উপন্যাসে একজন মা তার মেয়েকে বলছেন, ‘মেয়ে আমার কথা খুব মন দিয়ে শোন। যেমন করে কম্পাসের কাঁটা সব সময় উত্তর দিকে মুখ করে থাকে, ঠিক তেমনি পুরুষ সব অপরাধের কারণ হিসেবে একজন নারীর দিকেই আঙুল তুলে রাখবে।’ বইটি অনন্য সাধারণ।
তবে আমার সর্বশেষ কথা, নারী নারীই থাকুন। পুরুষ হয়ে উঠবার সাধনা না-ই বা থাকল। সমকক্ষ হয়ে ওঠার জন্য চেষ্টা করতে পারেন। সিগারেট টেনে পুরুষ হয়ে ওঠা নেহাতই হাস্যকর। আশির দশকে যখন জার্মানি যাই এমনি একটি প্রয়াস লক্ষ করেছিলাম তসলিমা নাসরিনের পুরুষের সমকক্ষ হওয়ার চেষ্টার ভেতরে। টেলিভিশন প্রোগ্রামে তিনি এসে বসেছেন। এক হাতে সিগারেট আর এক হাতে এক পাত্র মদ। ওঁর অনেক লেখা আমার প্রিয়, তবে এ ঘটনাটি নয়।
মনে রাখা ভালো নারীত্ব একটি চমৎকার ব্যাপার। একটি সজলাভ ছায়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু নারী যখন এগিয়ে এসে সমাজের সেসব নারীর মূল্যায়ন করতে চান, যারা অনেক বাধার পাহাড় ডিঙিয়ে, বাড়ির সব কাজের পর লেখেন আর বই প্রকাশ করেন, যারা অবহেলিত, উপেক্ষিত, পুরুষের সমাজে একলা, যারা তাদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন, মূল্যায়ন করেন, তাদের এই কাজের প্রশংসা করতেই হবে, বলতে হবে আপনারা অনন্য। অনন্যা শীর্ষ দশ এবং সাহিত্য পুরস্কার এমনি একটি ঘটনা।
১৯৬৩ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়জন মেয়ের ছবি দেখেছিলাম। কেউ হিজাবে নিজেদের ঢেকে রাখেননি। কী সাবলীল সুন্দর তারা। এখন হলে এই ছয়জনই হিজাব পরতেন।
লেখক : কথাসাহিত্যিক