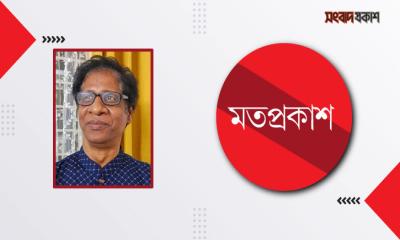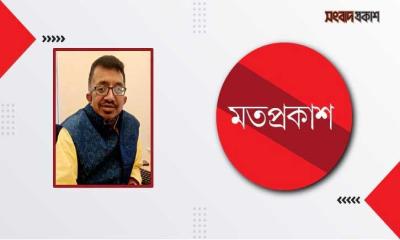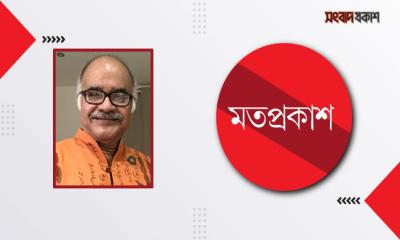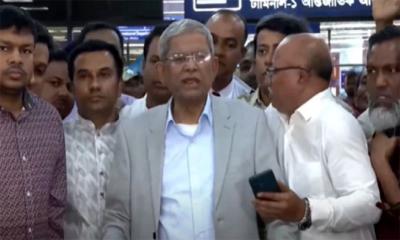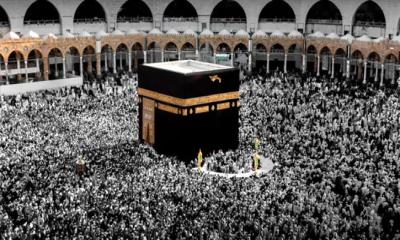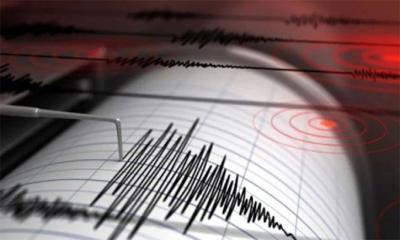ছোট্ট একটা শব্দ বা বাক্যও বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে। বদলে দিতে পারে ইতিহাসের বাঁক। প্রচলিত ধারণা-বিশ্বাসকে ভেঙে চুরমার করতে পারে। শব্দ বা বাক্যের এমন দানবীয় শক্তির মহড়া সভ্যতার ইতিহাসের পরতে পরতে দেখা যায়। ভাষার ক্ষমতা সহ্য করতে না পেরে মহীয়সী খনার জিহ্বা কেটে দিয়েছিলেন স্বামী ও শ্বশুর মিলে। আর সংস্কৃতের বদলে জনসাধারণের মুখের ভাষায় কাব্যচর্চা করায় আদি যুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কাহ্ন পাদের হাত কেটে নিয়েছিলেন ব্রাহ্মণবাদী শাসকরা।
শুধু শব্দ, বাক্য আর ভাষার জন্য এমন বহু অঘটনের সন্ধান পাওয়া যাবে সুদূর ইতিহাসে। আবার নিকট অতীতেও রয়েছে ভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জনের মতো বিরল ঘটনা। যার জন্য বিশ্ব ইতিহাসে সোনার হরফে নাম লিখিয়েছেন আমাদের বায়ান্নর ভাষা শহিদরা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ইহুদি আন্দোলনের নেতা ব্যারন রটসচাইল্ডকে ৬৭ শব্দে লেখা ব্রিটেনের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড আর্থার জেমস বেলফোরের চিঠিটি চিরতরে বদলে দিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস। মহাবিপর্যয় ডেকে এনেছে ফিলিস্তিনিদের জীবনে।
আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টকে লেখা আলবার্ট আইনস্টাইনের চিঠিটি কুখ্যাতি পেয়েছিল ‘খামবন্দি পারমাণবিক বোমা’ হিসেবে। ‘ইউরেনিয়াম’, ‘নিউক্লিয়ার ফিশন’, ‘রিঅ্যাক্টর’ এমন কয়েকটি শব্দের সমাহারে লেখা সেই চিঠির কারণেই তৈরি হয়েছিল কুখ্যাত ম্যানহাটন প্রজেক্ট। ফলাফল হিসেবে মানবসভ্যতার সবচেয়ে কলঙ্কজনক অধ্যায় লেখা হয় হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে।
শুধু শব্দ বা বাক্যই কি ইতিহাসে নাম লেখাতে পারে? কখনও কখনও বিরামচিহ্নও বিস্ময়কর ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে। ‘লা মিজারেবলস’ বইয়ের প্রকাশককে ১৮৬২ সালে লেখা ফরাসি ঔপন্যাসিক ভিক্টর হুগোর চিঠিটি তার বড় দৃষ্টান্ত। বইটি কেমন বিক্রি হচ্ছে, তা জানতে চেয়ে হুগো শুধুই লিখেছিলেন, ‘?’। প্রকাশকও কম যান না। উত্তরে লিখেছিলেন শুধু, ‘!’। যা বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে সবচেয়ে ছোট চিঠি হিসেবে।
তাই কোনো বিরামচিহ্ন, শব্দ, বাক্য বা ভাষা শুধু ভাব প্রকাশের মাধ্যমই নয়, এরা ইতিহাসে নজিরবিহীন বহু ঘটনারও জন্ম দিতে পারে। হয়ে উঠতে পারে কোনো জাতি, ধর্ম, বর্ণের আত্মপরিচয়, লড়াই-সংগ্রামের প্রতীক। কখনও সূত্রপাত ঘটাতে পারে সুগভীর আলোচনা-সমালোচনা-বিতর্কের। যেমনটি ঘটল এবারের বাংলা নববর্ষ-১৪৩২ উদযাপনে ইউনেসকোর স্বীকৃতি পাওয়া ‘মঙ্গল শোভাযাত্রার’ ‘মঙ্গল’ শব্দটি নিয়ে।
জাতিসংঘের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানবিষয়ক সংস্থার স্বীকৃতির সনদে স্পষ্ট লেখা রয়েছে ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা অন পহেলা বৈশাখ’। এখন সেই ‘মঙ্গল’ শব্দটিকে ‘অমঙ্গল’ বিবেচনায় অপসারণ করে সেখানে প্রতিস্থাপন করা হলো ‘আনন্দ’। ঘটনাটি বাস্তব জগতে তেমন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি না করলেও ভার্চুয়াল জগতে ঝড়-সুনামি বইয়ে দিয়েছে, দিচ্ছে। নেটিজেনরা ‘মঙ্গল’ আর ‘আনন্দ’ শব্দের পার্থক্য ধরতে না পেরে নেমে পড়েছেন শব্দের সুলুক সন্ধানে।
অনেকে প্রশ্ন রাখলেন, ‘মঙ্গল’ শব্দটা দূষিত হলে ‘আনন্দ’ কীভাবে পবিত্র?দুটো শব্দের উৎস তো একই। কেউ আবার ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখলেন, ‘মঙ্গল’ শব্দের সমস্যা হচ্ছে- সেটা হিন্দুয়ানি, পুরাতন, ধ্রুপদি, অতিরিক্ত পবিত্র!অথচ ‘আনন্দ’ শব্দেরও একই সমস্যা। এরা একই গোত্রের, একই শেকড় থেকে উঠে আসা।
গভীর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দিয়ে এক তাত্ত্বিক লিখলেন, ‘মঙ্গল’ শব্দটি নিয়ে যে আপত্তি, তা ভাষাতত্ত্বের জটিল কোনো সমীকরণ নয়, বরং গভীর সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনের বহিঃপ্রকাশ। এটি একদিকে যেমন শব্দের ঐতিহাসিক যাত্রাপথ ও তার বর্তমান অর্থকে অস্বীকার করার প্রচেষ্টা, তেমনি ধর্মীয় বিশুদ্ধতার নামে বিশেষ গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস।
বিশ্লেষণে আরও বলা হলো, ‘মঙ্গল’ নিয়ে আপত্তিকারীদের কাছে ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’ কেবল বর্ষবরণের লোকায়ত উৎসব নয়, বরং হিন্দু দেবতার নামে আয়োজিত মিছিল। তবে তাদের সেই যুক্তি দাঁড়িয়ে আছে বিরাট এক ভ্রান্তির ওপর, যা জ্ঞানতত্ত্বের ভাষায় জেনেটিক ফ্যালাসি নামে পরিচিত। যেখানে কোনো ধারণা, শব্দ বা প্রথার বর্তমান অর্থ ও ব্যবহারকে বিচার না করে, কেবল উৎস বা অতীত ইতিহাসের ভিত্তিতে গ্রহণ বা বর্জন করা হয়।
বঙ্গদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যের স্মারক হিসেবে বাংলা বর্ষবরণের আয়োজন ঘিরে ব্যবহৃত কোনো শব্দ নিয়ে এমন তীব্র-তুমুল আলাপ কখনও হয়েছে কিনা জানা নেই। তবে ‘মঙ্গল’ শব্দটি ঘিরে ঐতিহাসিক যে ‘কগনিটিভ’ তর্কের সূত্রপাত ঘটল বাংলাভাষা চর্চার ইতিহাসে তা দারুণ স্বাস্থ্যকর বটে। সেই সঙ্গে শব্দ আর ভাষাকে অবলম্বন করে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যবাদ, ধর্মীয় শুদ্ধ-অশুদ্ধতার যে গভীর বয়ান তৈরি হয়, তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কল্যাণে খোলাসা হলো বেশি করে। যা শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসন্ধানে জনপরিসরে কৌতুহল বাড়াতে দারুণ কাজে দেবে।
তবে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, বাংলা বর্ষবরণের আয়োজনে ‘মঙ্গল’ বা ‘আনন্দ’ যে নামেই শোভাযাত্রা হোক না কেন, তা নিয়ে তেমন আগ্রহ নেই আমজনতার। তাদের প্রত্যাশা খুবই সামান্য- সবকিছুর মধ্যে মঙ্গল নিহিত থাকুক; সবকিছু হোক আনন্দময়। শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থ, এর ওপর সংস্কৃতি, রাজনীতি, ধর্মের আধিপত্য নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।
পেছনে ফিরলে দেখা যায়, ষাটের দশকে ছায়ানটের হাত ধরে রমনার বটমূলে যে বর্ষবরণের যাত্রা শুরু হয়েছিল তার আঙ্গিকের বদল ঘটল আশির দশকে এসে। স্বৈরাচারী শাসন ও অপশক্তির অবসান কামনা করে ১৯৮৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা ইনস্টিটিউট প্রথম ‘আনন্দ শোভাযাত্রা’র আয়োজন করল। এরপর ১৯৯৬ সালে শোভাযাত্রার আগে প্রথম যুক্ত হলো ‘মঙ্গল’ শব্দটি। টানা দুই দশক ধরে ‘মঙ্গলময়’ শোভাযাত্রা শেষে ইউনেসকোর স্বীকৃতি মিলল ২০১৬ সালে এসে।
বিশ্ব ঐতিহ্যে স্থান পাওয়া সেই ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’ থেকে গত ১১ এপ্রিল ‘মঙ্গল’ শব্দটি অপসারণের ঘোষণা দিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কারণ ‘মঙ্গল’ শব্দটি নিয়েই নাকি প্রবল আপত্তি উঠেছে। ফলে আগের সেই ‘আনন্দ’ আয়োজনেই ফিরল পয়লা বৈশাখের শোভাযাত্রাটি। মাঝখান থেকে ‘মঙ্গল’ শব্দটি পরিণত হলো ঐতিহাসিক এক খলচরিত্রে। যা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম উত্তাল করে রাখলেন ‘মঙ্গল’ সমর্থকেরা।
তারপরও প্রশ্ন হচ্ছে ‘মঙ্গল’ শব্দ নিয়ে যে আপত্তি তা কি ধর্মীয় বিশুদ্ধতার বিচারে আসলেই নির্দোষ, নাকি এর পেছনে রয়ে গেছে বিশেষ কোনো অপ্রীতিকর ইতিহাস- এমন প্রশ্ন নিয়ে কৌতুহল থাকা স্বাভাবিক। কারণ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ আর বিশ্বাসের যে ভেদাভেদ আর দ্বন্দ্ব আদিকাল থেকে মানবসমাজে চলে আসছে তা নিরসন-নির্মূলের পথ বড়ই জটিল। হাজার বছরের সাধনা, যোগ-বিয়োগের হিসাবে ফলাফল যার শূন্যই থেকে যায়।
কিছু অনলাইন এক্টিভিস্টের মতে, বহুকাল ধরে বাংলার মুসলমানেরা হিন্দু জমিদারদের হাতে নানাভাবে শোষিত, নিপীড়ত, নির্যাতিত হয়েছেন। এমনকি হিন্দু জমিদাররা মুসলমানদের কাছ থেকে দাড়ির ট্যাক্স, মসজিদের ট্যাক্স, মুসলমানি নাম রাখার ট্যাক্স, পূজাপার্বনের ট্যাক্সও জোর করে আদায় করতেন।এমন নিপীড়নের বিরুদ্ধে যুগ যুগ ধরে লড়াইও করেছেন মুসলমানেরা। যা তাদের মনস্তত্ত্বে হিন্দুয়ানি সংস্কৃতি নিয়ে নেতিবাচক চিত্র তৈরি করেছে। যে চিত্র শতাব্দির পর শতাব্দি জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। এমনকি ভূরাজনৈতিক কূটনীতির ছদ্মবেশে সেই ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে।
শেষ অবধি ইতিহাসের সেই ধারাবাহিকতা এসে ঠেকল সংস্কৃত থেকে আগত ‘মঙ্গল’ শব্দে। হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন অনুসঙ্গে যার ব্যবহার স্পষ্ট। যেমন- মঙ্গলকাব্য, মঙ্গলঘট, মঙ্গলচণ্ডী অথবা মঙ্গলযাত্রা। যে কারণে আপত্তিকারীদের সরল যুক্তি হচ্ছে, ‘মঙ্গল’ শব্দটি উচ্চারণ বা কোনো অনুষ্ঠানের শিরোনামে ব্যবহারের অর্থ হিন্দু দেবদেবীর উপাসনা বা তাদের সংস্কৃতির অনুসরণ করার নামান্তর।
আপত্তিকারীদের এমন দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করে তাত্ত্বিকরা বলছেন, ‘মঙ্গল’ শব্দের বিরোধিতা আসলে ভাষার শুদ্ধতা রক্ষার চেষ্টা নয়, বরং সংস্কৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। এখানে শব্দ বা প্রতীক নয়, বরং সেগুলোকে ব্যাখ্যা করার অধিকার এবং সমাজে সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষমতাই মূল লক্ষ্যবস্তু। তারা বলছেন, শব্দ শুধু যোগাযোগের মাধ্যমই নয়, তা ক্ষমতা, পরিচয় আর বিশ্বাসের এক শক্তিশালী প্রতীকও বটে। আর সেই প্রতীককে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার লড়াইয়ে প্রায়শই যুক্তি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়।
ভাষার প্রচলিত প্রবণতা আর চরিত্রের বাইরে সামাজিক, রাজনৈতিক আর সাংস্কৃতিক বিবর্তনে শব্দের এমন প্রভাব সত্যিই বিস্ময়কর। অথচ ভাষা আর শব্দের ধর্মই হলো পরিবর্তন। উৎস থেকে বহুপথ পেরিয়ে নতুন অর্থ, নতুন দ্যোতনা-ব্যঞ্জনা লাভ করেই জীবিত থাকে। ভাষা গবেষকদের মতে, আজ থেকে প্রায় ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ বছর আগে আফ্রিকার মানুষেরা প্রথম ভাষা ব্যবহার করেছিল। সেখান থেকেই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমান বিশ্বে যত জীবিত বা মৃত ভাষা আছে, সেসবের আদি উৎস আফ্রিকার প্রাচীন সেই মানুষদেরই ভাষা।
ভাষাবিদদের মতে, আদি উৎস অভিন্ন হলেও শব্দের বৈচিত্র্যই যেকোনো ভাষাকে সমৃদ্ধ করে। যে ভাষার শব্দসম্ভার যত সমৃদ্ধ সে ভাষা তত উন্নত। বাংলা ভাষাও ভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, গোত্র থেকে আসা অজস্র শব্দ আত্তীকরণ করেছে। এ বিচারে কোনো সমাজ-সংস্কৃতিতে শব্দের আগমন ও প্রায়োগিক প্রবণতাকে দূরে ঠেলে না দিয়ে সবার আগে আলিঙ্গন করলেই কেবল নিজ ভাষা ও শব্দকে সমৃদ্ধ করা হয়। যা ভাষার প্রবাহমান সৌন্দর্য।
নেটিজেনদের অনেকের মত, এবারের বর্ষবরণের আয়োজনে ‘মঙ্গল’ শব্দের অপসারণ নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে ‘অন্তর্ভুক্তিমূলক’ সমাজ গঠনের সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কারণ, বর্তমানের মানচিত্রহীন বিশ্বে ‘অন্তর্ভুক্তিমূলক’ সমাজে নানা ধর্ম, বর্ণ, বিশ্বাস ও ভাষার মানুষ থাকতে পারে। কোনো বিশেষ সংস্কৃতির শব্দ বা ভাষাকে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অপসারণ না করে নিজস্ব ঐতিহ্যে অন্তর্ভুক্ত করলেই কেবল কাঙ্ক্ষিত জাতিগঠনের প্রয়াস সফল হতে পারে। আর যেখানে বর্ষবরণের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে নতুনকে বরণ, সেটা হতে পারে নতুন কোনো শব্দ বা ভাষাও। যে শব্দ বা ভাষা আবার কখনও কখনও তৈরি করতে পারে নতুন কোনো ইতিহাস।
লেখক : সাংবাদিক