সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের কিছু সংশোধনীসহ উত্থাপন করা ব্যাংক কোম্পানি আইন ২০২৩ জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। যেখানে দেশের সাধারণ মানুষের কাছে ‘ঘৃণার পাত্র’ হিসেবে বিবেচিত ঋণখেলাপিদের দমনে অনেক শব্দ ও বাক্য সন্নিবেশ করে আইনটিকে যুগোপযোগী করার চেষ্টা রয়েছে।
আইনটির ভালো-মন্দ ব্যাখ্যা করে অনেক কথা শোনা গেলেও একই ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর বা গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠানের ঋণখেলাপি থাকলেও তার অন্য প্রতিষ্ঠান ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারার সুযোগ এবং পরিচালক পর্ষদে ৯ বছরের পরিবর্তে টানা ১২ বছর থাকতে পারা, এরপর তিন বছর বিশ্রামের পর আবার ১২ বছর পরিচালক হওয়া, একই পরিবারের চারজনের পরিবর্তে তিনজন পরিচালক থাকতে পারা, একই পরিচালকের কখনো মূল পরিচালক, কখনো বা বিকল্প বা আমানতকারীদের মধ্য থেকে পরিচালক নির্বাচিত হয়ে পরিষদে থাকা, পরিচালকদের অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতা কেমন হবে বা কেমন হওয়া উচিত, তা বিবেচ্য বিষয় না হওয়া (নতুন আইনে কিছু উল্লেখ নেই) এবং কোনো পরিচালকের ২০ শতাংশ শেয়ার থাকলে, তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কোম্পানি স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোম্পানি হিসাবে গণ্য হয়ে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান তৈরি করে ভিন্ন পরিচয়ে ঋণ নিতে পারার সুযোগ নিয়ে বেশ সমালোচনা হচ্ছে। নতুন আইনে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের চিহ্নিত করতে নতুন করে সংজ্ঞায়নও করা হয়েছে।
বিশ্লেষকেরা বলছেন, খেলাপি ঋণ কমানো এবং ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎকারীদের শাস্তির আওতায় আনার তীব্র দাবির মুখে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এবং ব্যাংক ব্যবসায়ীদের সাজিয়েগুছিয়ে দেওয়া বিল পাস করা সংশোধিত ব্যাংক কোম্পানি আইন ২০২৩ প্রকৃত অর্থে শূন্যগর্ভা এবং ধনিক শ্রেণি ও ব্যবসায়ীবান্ধব।
বাংলাদেশের অর্থনীতির দীর্ঘদিনের প্রবণতা ও বিদ্যমান কাঠামোব্যবস্থার নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদের নতুন ব্যাংক কোম্পানি আইনের শব্দচিত্রে মোটেও বিস্মিত হওয়ার কথা না। এমনতর শব্দচিত্রের ব্যতয় হওয়াটাই বরং অস্বাভাবিক। কেননা যে দেশে গড়ে প্রতি সাড়ে ৪ বছর অন্তর ব্যাংক কোম্পানি আইন সংশোধন (গত ৩২ বছরে ৭ বার) হয়; যে দেশে দেশের ৫৫টি ব্যাংক থেকে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর পরিচালকেরা ১ লাখ ৭১ হাজার ৬১৬ কোটি ১২ লাখ ৪৭ হাজার টাকা ঋণ তুলে নেন, যা ব্যাংকগুলোর বিতরণকৃত মোট ঋণের ১১ দশমিক ২১ শতাংশ (অথচ পরিচালকদের মোট তহবিল মাত্র ৮ শতাংশ; বাকি ৯২ শতাংশই জনগণের); যে দেশের যেকোনো আইন-সংশোধনী পাস করার অধিকারী জাতীয় সংসদের ৬১ দশমিক ৭ শতাংশই পেশায় আপাদমস্তক ব্যবসায়ী (৩০০ আসনের মধ্যে জয়ী হয়ে শপথ নেওয়া সংসদ সদস্যদের ১৮২ জন পেশায় ব্যবসায়ী), যাদের মধ্যে আবার ১৭ জনই ব্যাংক পরিচালক; যে দেশে মাত্র ৭ বছরের ব্যবধানে মোট শিল্প উৎপাদনে বৃহৎ আকারের প্রতিষ্ঠানের হিস্যা ৪৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬৯ শতাংশে হয় এবং একই সময়ে মাঝারি আকারের প্রতিষ্ঠানের হিস্যা ২৫ শতাংশ থেকে ৪ শতাংশে নেমে যায়; যে দেশে মাত্র পাঁচ বছরে ঋণ গ্রহণে প্রবৃদ্ধি হয় ৯২৭ শতাংশ; যে দেশে মাত্র সাড়ে সাত বছরে বৈদেশিক ঋণ ১২৮ শতাংশ বেড়ে যায়; যে দেশের মাত্র একটি পরিবারের সদস্যদের যাদের হাতে রয়েছে ৭টি ব্যাংক ও একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বড় অংকের শেয়ার, তারা মাত্র দুটি ব্যাংকের ২১ হাজার ৬৩ কোটি ৫৮ লাখ টাকা ঋণের মধ্যে ৫৭ দশমিক ৪ শতাংশই হস্তগত করে নেন; যে দেশে মাত্র একজন ব্যবসায়ীর হাতেই ৬০-৭০ হাজার কোটি টাকার বেশি ঋণ চলে যায়; যে দেশে মাত্র ২১ জন ব্যক্তি ৫০ কোটি ডলার বা ৫ হাজার কোটি টাকার বেশি সম্পদ থাকে, যে দেশে কোভিড মহামারির ভয়ানক বিপর্যয়ের ১ বছরের মধ্যেই ১০ কোটি টাকার বেশি সম্পদ থাকা ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় ৪৩ শতাংশ বেড়ে যায়—সেই দেশে জনগণের আকাক্সক্ষার প্রতিফলন ঘটানো একটি আইন থাকা কিংবা প্রত্যাশা করাটাই তো অস্বাভাবিক (সংবিধানে যা-ই থাকুক)। ঝুঁকির পরিমাণ ১০০০ শতাংশ হলেও যেকোনো মূল্যে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের মূল মন্ত্রধারী পুঁজিবাদী, আথির্কীকরণকৃত ও তথাকথিত উদারনৈতিক সমাজ-অর্থনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এমনতর বিধি-বিধানই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। যদিও মানবকল্যাণকামী যেকোনো মতবাদই স্বীকার করে যে মানুষের সম্পদের বিকাশ সম্পূর্ণ বৈধ ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় হতে পারে। কেননা যুক্তির বিচারে সত্য ও সততারও একটি মূল্য আছে। সবকিছু সত্য ও সরল পথে হলে সব পক্ষেরই তাতে লাভবান হওয়ার সুযোগ থাকে, যা সামগ্রিকভাবে সমাজে একটি ভারসাম্য বয়ে আনে। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সম্পদ বৈষম্যের সৃষ্টিই অন্যতম একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। সম্পদের এই বৈষম্যই সমাজে নানামুখী বৈষম্য বয়ে আনে। আর পুঁজিবাদে এই বৈষম্য সৃষ্টিতে ব্যাংকিং ব্যবস্থাই সর্বাধিক অবদান রাখে।
১৯৭২ সালে যুদ্ধপরবর্তী বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের কার্যক্রম তথা আমানত, ঋণ, মুনাফার চিত্রের সাথে আধুনিককালের চিত্রের তুলনা করলে অনেক ক্ষেত্রেই বিস্মিত হতে হয়। বঙ্গবন্ধু গ্রামীণ অর্থনীতিকে পুনর্জ্জীবিত করতে এবং সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে গ্রামের সহজ-সরল মানুষদের রক্ষায় সারা দেশে রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকের কার্যক্রম ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। মারপ্যাঁচহীন ব্যাংকিং কার্যক্রমের বদৌলতে অল্প সময়ের মধ্যেই গ্রামীণ অর্থনীতির আমূল উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল।
যুদ্ধপরবর্তী বাংলাদেশের উন্নয়নে ব্যাংকিং খাত অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিল, যার প্রমাণ বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৯৭২ পরবর্তী প্রতিবেদন ও সদ্য জাতীয়করণকৃত সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংকের তৎকালীন বার্ষিক প্রতিবেদনে পাওয়া যায়। ওই সময় এসব ব্যাংক অভূতপূর্ব অগ্রগতি ও প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল। অথচ যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিতে এসব ব্যাংক হাজারো সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার মুখে পড়েছিল।
সোনালী ব্যাংকের তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে এন আহমেদের স্বাক্ষরিত ১৯৭২ সালের ১ এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বর অর্থাৎ ৯ মাসের বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, “স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ব্যাংকটির ১৩৫টি শাখা এবং অবকাঠামো ধ্বংস করা হয়েছে। লুট করা হয়েছে- ক্যাশ ১.৫৮ কোটি টাকা এবং ৪০ লক্ষ টাকার স্বর্ণ। ৪৩টি শাখা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর নাগাদ আমানত বেড়ে দাঁড়ায় ১৭৩ কোটি টাকা, যা গত বছরে ছিল ৭২ কোটি, অর্থাৎ আমানত প্রবৃদ্ধি ৭১.২৯%। আমানত বৃদ্ধি পাওয়ার প্রধান কারণ ছিল পল্লী গ্রামের মানুষের ব্যাংকে টাকা রাখার প্রবণতা।”
সংস্থাপন খরচ ১.৫৮ কোটি টাকা এবং অন্যান্য খরচ বাদ দিয়েও সোনালী বাংক ১৯৭২ সালে নিট মুনাফা করেছিল ৫২ লক্ষ টাকা। জনতা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংকের নিট মুনাফার চিত্রও ছিল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। ১৯৭২ সালের ১ এপ্রিল-৩১ ডিসেম্বর সময়কালে জনতা ব্যাংকের আমানত ৮০% বৃদ্ধি পেয়ে ৮৭.৪ কোটি টাকা থেকে ১৫৭.৭ কোটি টাকা দাঁড়িয়েছিল।
ঋণের (অ্যাডভান্সের) পরিমাণ ৭৮.৭ কোটি টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ১১৩.২ কোটি টাকা অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি প্রায় ৪৪%। ব্যাংকটির নিট মুনাফা পূর্বের ৬৬ লক্ষ টাকা অপেক্ষা ৬৬% বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১ কোটি ৬ লক্ষ টাকায়। অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংকের আমানত, ঋণ ও মুনাফা পরিস্থিতিও ছিল আশ্চর্যরকম ভালো। পক্ষান্তরে ৫০ বছর পরে এসে ২০২২ সালে সোনালী ও জনতা ব্যাংকের আমানত, ঋণ ও মুনাফার চিত্র বিশ্লেষণ করলে বর্তমান ব্যাংকিং কার্যক্রম, নীতিমালা ও ব্যাংকসংশ্লিষ্ট মানুষজনকে যথেষ্ট লজ্জিত হতে হবে।
বিগত অর্থবছরের তুলনায় ২০২২ সালে সোনালী ব্যাংকের মুনাফা বেড়েছে প্রায় ২০ শতাংশ, যা আবার ব্যাংকের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় ও শক এবজর্বিং ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির নামে ছাড় দেওয়া ঋণের সুদ ব্যাংকগুলোর আয়খাতে দেখানোর সুযোগ দিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জারি করা সার্কুলারের বদৌলতে। অন্যান্য সরকারি ব্যাংকের কথা না-ই বা উল্লেখ করলাম। অথচ ১৯৭২ পরবর্তী কয়েক বছর ব্যাংকে কর্মরত অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জানতেনই যে সমমূলধন, মুনাফা, তারল্য ব্যবস্থাপনা, ঋণঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, পুনঃতফসিল, ক্যাশ ক্রেডিট, জামানত, জামানতের সম্পত্তির দলিল, সাসটেইনেবল ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সিং কীভাবে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে কাজ করে।
যুদ্ধে বিধ্বস্ত বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকারি ব্যাংকগুলোয় কর্মরত কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও প্রায়োগিক ব্যাংকিংয়ের জ্ঞানের অপ্রতুলতায় বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে কিছু অসাধু ব্যক্তি ঋণ খেলাপি হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাদের কঠোর হস্তে দমনের অভিযানও শুরু করেছিলেন। যে কারণে ১৯৭৫-৭৬ অর্থবছরে যে দুই মাস বঙ্গবন্ধু বেঁচেছিলেন, সে সময়টুকুতে ব্যাংক আমানত ৫০০ কোটি থেকে ১১০০ কোটি, তলবি আমানত বা ডিমান্ড ডিপোজিট ২৫০ কোটি থেকে ৫৭৫ কোটি এবং মেয়াদি আমানত বা টাইম ডিপোজিট ২০০ কোটি থেকে বেড়ে ৫৫০ কোটি টাকায় পৌঁছে গিয়েছিল। ৫০ বছর আগে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের প্রবৃদ্ধির চিত্রের সঙ্গে বতর্মান সময়ের ব্যাংকিং খাতের তুলনা করলে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে আমাদের ব্যাংকিং খাত প্রকৃত অর্থেই প্রচণ্ড অসুস্থতায় ভুগছে। ব্যাংক কোম্পানি আইনের ৩২ বছরে ৭ বারের সংশোধনী ব্যাংকিং খাতের সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে যে কোনো ভূমিকাই রাখতে পারেনি, সে কথা বুঝতে যে অর্থনীতি বা আইন শাস্ত্রের কোনো প-িত হতে হয় না, সে কথা এখন নির্দ্বিধায় বলা যায়।
সংশোধিত ব্যাংক কোম্পানি আইনে ঋণখেলাপি ও ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের নতুন সংজ্ঞায়ন করে তাদের দমনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী, মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে বকেয়া কিস্তির ৫০ শতাংশ বা অর্ধেক দিলেই তো ওই গ্রাহককে খেলাপি হিসেবে দেখানো যাবে না।
এ ছাড়া আরও অনেক নির্দেশনা রয়েছে, যা গ্রাহকের মনে ঋণ পরিশোধের জন্য যে ভয় ও চাপ কাজ করে তা দূর করতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। উপরন্তু‘ প্রভাবশালী ব্যক্তি ও মহল, রাজনৈতিক গোষ্ঠী, মুনাফাজীবী ব্যবসায়ীদের প্রচ- ক্ষমতাধর গোষ্ঠীর সুবিধার্থে বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ ব্যাংক পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে সার্কুলার জারি করে, যা এক অর্থে ঋণখেলাপি সংস্কৃতিকে আরও বড় ভিত্তি দিয়েছে-দিচ্ছে।
দেশের অর্থনীতি ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি, রেমিট্যান্স, ব্যাংক-বীমা সবই প্রভাবশালী নানা গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে, যেখানে রাজনীতি, ব্যবসা, ব্যাংকিং, বীমা সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় ব্যাংক খাতের শৃঙ্খলা ফেরাতে হলে বারংবার আইন সংশোধনের পরিবর্তে আইনের যথাযথ প্রয়োগ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার কোনো বিকল্প নেই। রাজনৈতিক ছত্রছায়া, স্বজনপ্রীতি আর যুদ্ধ-মন্দার প্রভাব দেখিয়ে ঢালাওভাবে ঋণখেলাপিদের ছাড় ও মাফ করে দেওয়ার আনন্দ থেকে বেরিয়ে না এলে কোনো আইনই আদতে কাজে আসবে না। ব্যাংক খাতের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনতে হলে আন্তর্জাতিক রীতিনীতি মেনে স্বদেশ-উত্থিত উন্নয়ন দর্শনের আলোকে ব্যাংক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর এখনই উৎকৃষ্ট সময়। কেননা এখনো বাংলাদেশের যাবতীয় ক্ষমতার কেন্দ্রে আসীন রয়েছেন বঙ্গবন্ধুর একজন কন্যা। সত্যি কথা বলতে কি, বঙ্গবন্ধুর উত্তরসূরীর আমলেও যদি আমাদের ব্যাংকিং খাতের সমস্যা ও সংকটের সমাধান বা ভগ্ন স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার না-হয়, তাহলে আর কোনো কালেই তা হবে না।
লেখক : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি


















-20231109105053-20250402121817.jpg)





















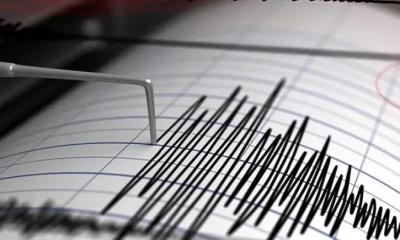







-20250327140635.jpeg)



