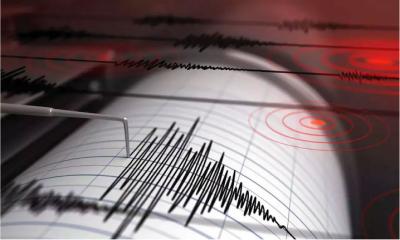“আমার বড় বোনের নাম সালেহা। সবাই ডাকত শেলী ইসলাম বলে। কিন্তু আমাদের কাছে উনি ‘বুবু’। ময়মনসিংহের মুমিনুন্নেসা কলেজে পড়তেন। ইপসু (পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন) করতেন। কলেজের ভিপিও ছিলেন। মেয়েদের নিয়ে বড় বড় চিন্তা ছিল তার। ওই আমলেই তিনি রাইফেল শুটিং করতেন, ব্যাটমিন্টনও খেলতেন। আইয়ুব খান যখন পূর্ব পাকিস্তান এলো, এর প্রতিবাদে তখন ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ উড়িয়েছিলেন বুবু। আমাদের পরিবারে পলিটিকসের ধারণা ঢুকেছিল বুবুর মাধ্যমেই।”
বড় বোনের স্মৃতিচারণা দিয়েই আলাপচারিতা শুরু করেন একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধা ডালিয়া আহমেদ। এক বিকেলে তার বাড়িতে বসেই কথা চলে।

মহিউদ্দিন আহমেদ ও আশরাফুন্নেসার দশম সন্তান ডালিয়া আহমেদ। বাড়ি নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলার কাজলা গ্রামে। বাবা ছিলেন স্টেশন মাস্টার। পরিবারে ছিল এগারো ভাইবোন–তিন বোন ও আট ভাই। এগারো সন্তানেরই স্বপ্ন দেখেছিলেন মা আশরাফুন্নেসা।
সে কাহিনি শুনি ডালিয়া আহমেদের জবানিতে। তাঁর ভাষায়, ‘ব্রিটিশ আমলের কথা। এগারো সন্তানের এক জননী রত্নগর্ভা উপাধি পেয়েছিলেন। সে ছবি ছাপা হয় পেপারে। তা দেখে মায়েরও ইচ্ছা এগারো সন্তানের জননী হবেন। হয়েছিলেনও তাই। রত্নগর্ভা মা। বড় ভাই আরিফুর রহমান, ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে চাকরি করতেন, রাওয়ালপিন্ডিতে। এরপর আবু ইউসুফ খান (বীরবিক্রম), ছিলেন বিমানবাহিনীতে। তারপরই কর্নেল আবু তাহের (বীর উত্তম), এগারো নম্বর সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়েই তিনি মেজর থেকে কর্নেল হন। তাঁর ছোট আবু সাঈদ (দাদা ভাই), প্লাটুন কমান্ডার ছিলেন। এরপরই আমাদের বুবু। তার ছোট ঝন্টু ভাই, ড. এম আনোয়ার হোসেন (মুক্তিযোদ্ধা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক), শাখাওয়াত হোসেন বাহার (বীরপ্রতীক), ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল (বীরপ্রতীক), এরপর আমি আর সবার ছোট জুলিয়া আহমেদ।’
ছুটিতে তখন বাড়িতে আসত কর্নেল তাহেরসহ সব ভাইরা। বাড়ির পরিবেশও সে সময় পাল্টে যেত। বালুর বস্তা ঝুলিয়ে ট্রেনিং করানো হতো সবাইকে। আশপাশের মানুষ অবাক হয়ে দেখত সে কাণ্ড। মুচকি হেসে ডালিয়া শোনান সে ইতিহাস–
“তাহের ভাই আমাদের কমান্ডো প্যারা পিটি শেখাতেন। বালুর বস্তার কাছে নিয়ে আমাকে বলতেন ‘আপনিও কিন্তু ঘুষি দিবেন। শক্ত করতে হবে তো হাতগুলোকে।’ বাড়িতে ইঁদারা (কুয়া) ছিল। দড়ি বেঁধে সেখানে নামানো হতো বেলাল ভাই আর আমাকে। কিন্তু বাহার ভাই ছিলেন সবচেয়ে সাহসী। ইঁদারায় তিনি ঝাঁপ দিতেন আবার একা একা উঠে আসতেন। একটা দড়ি বাঁধা থাকত গাছে। সেটা দিয়ে গাছের মধ্যেও উঠতে হতো। শীতের রাতে উঠানপোড়া পিঠা বানানো হতো বাড়িতে। আগুনের চারদিকে বসতাম সবাই। কলাপাতায় মোড়ানো পিঠা। আগুনে পুড়ছে। তাহের ভাইজান বলতেন–‘আগুনের ওপর দিয়ে যে লাফ দিয়ে আসতে পারবে, সে পিঠা পাবে।’ তিনি আগেই বুঝতে পেরেছিলেন একটা যুদ্ধ হবেই। তাই নানাভাবে পরিবারের সবাইকে গেরিলা প্রশিক্ষণ দিয়ে রেখেছিলেন। এ কারণেই অন্য ভাইরা মুক্তিযুদ্ধে খুব বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পেরেছিল।”
২৫ মার্চে সারা দেশে গণহত্যা শুরু করে পাকিস্তানি আর্মিরা। ময়মনসিংহ থেকে অনেক পরিবারই এসে আশ্রয় নেয় তাদের বাড়িতে। দেশের সঙ্গে বদলে যেতে থাকে পরিবারের চিত্রও। তাঁর ভাষায়–“বাড়িতে অনেক মানুষ তখন। রান্নাবান্না চলছে। তবে যুদ্ধের ভয়বহতা তখনো আমরা বুঝিনি। নানা কাজে ব্যস্ত রেখে আম্মাও বুঝতে দিতেন না। হঠাৎ একদিন সকালে উঠে শুনি আনোয়ার ভাই নাই। আম্মার কাছে একটা চিরকুট– ‘আম্মা, যুদ্ধে যাচ্ছি দোয়া করবেন।’ কিন্তু আম্মার চেহারায় উৎকণ্ঠা নেই। কেমন যেন একটা গর্ব ও আনন্দ দেখতে পেলাম। কিছুদিন পরে বেলাল ভাই আর বাহার ভাইও নাই। একইভাবে তারাও চলে গেছে যুদ্ধে। আমরা নানা খবর শুনতাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে। গোটা গ্রামের মানুষ আসত রাতে। চরমপত্র শুনতে বেশি ভালো লাগত। এভাবে ধীরে ধীরে পরিবারে যুদ্ধের একটা আবহ তৈরি হতে থাকে।”
তখনো কি পাকিস্তানি সেনারা কাজলা গ্রামে আসেনি?
“না। ওরা মনে করত কাজলা হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি। আর আমাদের বাড়িটা হলো তাদের অস্ত্রাগার। ওরা গেরিলা আক্রমণের ভয়ে এদিকে আসেনি। তবে মাঝেমধ্যেই গ্রামে গুজব ছড়াত– ‘মিলিটারি আইছে, মিলিটারি আইছে’। সবাই তখন দৌড়ে পালাত। আম্মার ভূমিকা দেখেছি ওই সময়টাতে। মাথা ঠান্ডা রেখে তিনি বলতেন–‘তুলা রাখ সবাই।’ যদি ওরা বোমা ফোটায়, গোলাগুলির শব্দে যেন বাচ্চাদের কানের ক্ষতি না হয়। মুড়ি, চিড়া আর গুড় আগেই প্যাকেট করে রেখে দিতে বলতেন।”
২৫ জুলাই ১৯৭১। কর্নেল তাহেরসহ কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে ভারতের দেবীগড় সীমান্ত অতিক্রম করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। পরে কর্নেল তাহেরকে ১১ নম্বর সেক্টরের কমান্ডের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এদিকে তাহেরের স্ত্রী লুৎফা নিরাপদ ভেবে বাবার বাড়ির থেকে দুই মাসের সন্তান জয়াকে নিয়ে চলে আসেন কাজলায়। কিছুদিন থাকার পরই চারজন মুক্তিযোদ্ধা গোপনে এসে খবর দেন তাদের জন্য কাজলা নিরাপদ নয়। ফলে এক রাতে জয়াসহ লুৎফা, তার ভাই সাব্বির, দাদা ভাই, ডালিয়া ও জুলিয়া রওনা হয় সীমান্তের পথে। অতঃপর কী ঘটল সে কথা জানালেন ডালিয়া আহমেদ।
তিনি বলেন–‘প্রথমে শ্যামগঞ্জ থেকে ট্রেনে আসি ঠাকরাকোনায়। অতঃপর নৌকায় কংস নদী পার হয়ে ভুরভুরাসুনই নামক জায়গায় আশ্রয় নিই। ওখানে চারদিকে পানি। মাঝখানে বাড়ি। এক সপ্তাহ ছিলাম সেখানে। এরপরই পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা টের পেয়ে যায়। আমরা তখন সরে পড়ি। এরপর বহু কষ্টের পথ পেরিয়ে বাগমারায় পৌঁছি। সেখানে ছিল একটা চালা ঘর। তার চারদিকে ফাঁকা। এক রাত থাকতে হলো ওখানেই। অতঃপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় তুরার বিএসএফ ক্যাম্পে।’ তুরাতে পাহাড়ের ঢালে থাকত এক পরিবার। সেখানে দরশনা কুমারী নামে এক মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় ডালিয়াদের। ওরা তীর-ধনুক চালোনায় পারদর্শী ছিল। দুই বোন শিখে নেয় তির-ধনুক চালানো। মাঝেমধ্যে শিকারেও বের হতো। তারা ভাবত এই তির-ধনুক দিয়েই তারা পাকিস্তানিদের মারবে।
কর্নেল তাহের সপ্তাহে এক দিন দেখা করতে আসতেন। একবার ডালিয়া তাকে তার ইচ্ছার কথা জানান। শুনে হাসতে থাকেন তিনি। অতঃপর বোঝালেন যুদ্ধের জন্য লাগবে ট্রেনিং। ডালিয়া বলে–‘আমি যুদ্ধে যাব আমাকে নিয়ে যান।’ তাহের বলেন–‘আপনি যুদ্ধে যাবেন? আপনার তো পোশাকই নেই। কী করে যাবেন? ওটার জন্য তো প্রপার পোশাক দরকার হয়।’ শুনেই মন খারাপ হয় ডালিয়ার।
তারপর কী করলেন?
ডালিয়া বলেন–‘মেজ ভাইজান কিছু কাপড় নিয়ে এসেছিল তুরাতে। সেখান থেকে এক জোড়া ট্রাইজার আর দুটো টি-শার্ট নিলাম। ওটাকে কেটে ছোট করে আমার সাইজে করা হলো। আগ্রহ দেখে এক জোড়া কেডস জোগাড় করে দিলেন লুৎফা ভাবি। আরেকটা ক্যাপও মিলল। তাহের ভাইজান আসার দিন সেগুলো পড়ে রেডি হয়ে অপেক্ষায় থাকি।
এবার উনি এসে অবাক হলেন। আমার আপাদমস্তক দেখে মুচকি হেসে বললেন–‘নাউ ইউ লুক লাইক আ রিয়েল গেরিলি’। ওই দিনই তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন মাহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্পে। ওই পাশে ধানুয়া কামালপুর। ভাইজান কী যেন বলে ক্যাম্পের ভেতরে ঢুকে গেলেন। কিন্তু আমাকে যেতে দিচ্ছিল না। জানতে চাইছে ‘পাসওয়ার্ড’। আমি তো জানি না ওটা কী। পরে একজন কানে কানে বলে দিলেন। ওই দিনের পাসওয়ার্ড ছিল ‘টুপি’। ওটাই ছিল আমার প্রথম শিক্ষা।
পরদিনই ট্রেনিং শুরু হয়। আমার সঙ্গে ট্রেনিং করেছেন ব্যারিস্টার শওকত আলী। উনি ছিলেন টাঙ্গাইলের মানুষ, আওয়ামী লীগের একজন এমএনএ। এক সপ্তাহের মতো ট্রেনিং চলে। প্রথম শেখানো হলো কী করে ক্রলিং করে যেতে হয়। সবচেয়ে ছোট অস্ত্র ছিল এসএমসি (সাব মেশিন কার্বাইন)। যেটা আমি নিতে পারব, সেটাই চালানো শিখাল0। নিশানা আমার খুব ভালো ছিল। এমএমজি সেট করেও চালানো শিখেছি। তবে রাইফেলগুলোতে খুব ধাক্কা খেতাম। ট্রেন্ড মুক্তিযোদ্ধা ও ইন্ডিয়ান কিছু অফিসার ট্রেনিং করায়। একটা মেয়ে ট্রেনিং নিতে এসেছে– এটা দেখতেই আসত অনেকেই।’
ট্রেনিং শেষে কী করলেন?
মুক্তিযোদ্ধা ডালিয়া আহমেদের উত্তর–‘অপারেশন থাকলে ভাইজান সীমান্তবর্তী জায়গায় আমাকে রেকি করতে পাঠাতেন। অনেক সময় গাছে চড়ে পাতার ফাঁকে ফাঁকে ক্যামোফ্লাক্স করে থাকতে হতো। আমি খুব আশা নিয়ে যেতাম। ভাবতাম একটা পাকিস্তানিকেও যদি দেখি, গুলি করব। আমাকে চিরকুট দেওয়া হতো। গ্রামের মেয়ে সেজে এক ক্যাম্প থেকে সেটা আরেক ক্যাম্পে পৌঁছে দিতাম। এক বাংকার থেকে আরেক বাংকারে যেতাম। মাঝেমধ্যে বাংকারেই থাকতে হতো। বলা হতো বের হওয়া যাবে না। গোলাগুলি চলছে। কী বিকট আওয়াজ! কিন্তু তাতেও ভয় হতো না। নিজেকে তখন যোদ্ধা ভাবতে শুরু করেছি। বোমা ও এন্টিপারসোনাল মাইনের বিষয়েও ধারণা হতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধাদের ম্যাগাজিনেও গুলি ভরে দিতাম। গানগুলোকে পরিষ্কার করে দেওয়ার কাজও করেছি অনেক।
১৪ নভেম্বর ঢুকেছিলাম বাংলাদেশের ভেতরে। আনোয়ার ভাই সঙ্গে ছিলেন। ওই দিন ছিল তাহের ভাইজানের জন্মদিন। তাই ধানুয়া কামালপুর অপারেশনে জয় আনতেই হবে। অন্য পাশে বাংকার থেকে ওয়্যারলেসে নানা নির্দেশ দিয়ে তাহের ভাইজান যুদ্ধটাকে পরিচালনা করছেন। একটা ঢালু জায়গায় রাত থেকে আমরা পজিশনে। ওয়্যারলেসটা আনোয়ার ভাইয়ের কাছে। সকাল হয় হয়। গোলাগুলির শব্দ পাচ্ছি। হঠাৎ ওয়্যারলেসে একটা খবর আসে। তাহের ভাইজান আহত হয়েছেন। কিন্তু আশপাশের যোদ্ধারা বলছে কর্তা (কর্নেল তাহেরের ছদ্মনাম) নেই। আনোয়ার ভাই আমার দিকে তাকিয়ে শুধু বললেন–‘তোমাকে এখনই চলে যেতে হবে।’ এরপর আর রণাঙ্গনে ফেরা হয়নি।’
দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন আপনি কোথায়?
‘তুরাতেই। সেদিন মনে হয়েছে কখন স্বাধীন দেশে যাব। ভাইয়েরা রণাঙ্গনে। তাহের ভাইজানের চিকিৎসা চলছে পুনাতে। ডিসেম্বরের শেষে একটা খোলা ট্রাকে করে আমরা ময়মনসিংহ সার্কিট হাউসে এসে এক রাত থাকি। অতঃপর চলে আসি কাজলায়। সবাই জেনে গেছে মুক্তিযুদ্ধ করেছি। তখন সবাই অন্য রকম সম্মান করত। মুক্তিযুদ্ধের গল্পও শুনতে চাইত।’
যে দেশের জন্য মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন, সে দেশ কী পেয়েছেন?
এ বীর নারী বলেন–‘পাকিস্তান আমলেও সম্প্রীতির মাঝে আমরা বসবাস করেছি। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান কাউকেই আমরা আলাদাভাবে দেখিনি। সব উৎসবই সমান গুরুত্ব পেত। ধর্মটা গুরুত্ব পেত না। স্বপ্ন ছিল অসাম্প্রদায়িক দেশ পাব। সেটা হয়নি এখনো। দেখ, আজ চারদিকে এত হেজাবধারী। আমাদের মায়েদেরকে তো দেখেছি খালি একটা ঘোমটা দিতে। তখন বোরখা নিয়েও মাতামাতি ছিল না। তাদের মধ্যে তো শালীনতা ছিল। তাহলে এখন এ কোন সংস্কৃতি শুরু হয়েছে দেশে!’
যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে শাহবাগে গড়ে ওঠা গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলন ছিল দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ– এমনটাই মনে করেন মুক্তিযোদ্ধা ডালিয়া আহমেদ। কিসের বিনিময়ে, কোন বলিদানে আমরা দেশটা পেলাম, সেই সঠিক ইতিহাসটাও প্রজন্মকে জানতে হবে। তবেই তৈরি হবে দেশের প্রতি মমতাবোধ। সলিল চৌধুরীর ‘চাবি’ কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে কবিতার কথাগুলোই তিনি নিবেদন করেন পরবর্তী প্রজন্মের উদ্দেশে–
‘উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি শুধু একগুচ্ছ চাবি
ছোট-বড়, মোটা-বেঁটে নানা রকমের, নানা ধরনের চাবি
মা বললেন, যত্ন করে তুলে রেখে দাও।
তারপর যখন বয়স বাড়লো
জীবন ও জিবিকার সন্ধানে পথে নামতে হলো
পকেটে সম্বল শুধু সেই একগুচ্ছ চাবি।
ছোট-বড়, মোটা-বেঁটে নানা রকমের, নানা ধরনের চাবি।
কিন্তু যেখানেই যাই সামনে দেখি প্রকাণ্ড এক দরজা
আর তাতে ঝুলছে প্রকাণ্ড এক তালা,
পকেট থেকে চাবিরগুচ্ছ বের করি
এ চাবি সে চাবি
ঘোরাই ফেরাই
লাগে না, খোলে না
শ্রান্ত হয়ে ঘরে ফেরি।
মা দেখেন আর হাসেন
বলেন—ওরে, তোর বাবার হাতেও এই চাবি দিয়ে, ওসব দরজাগুলো খুলেনি
শুনেছি নাকি তার বাবার হাতে খুলতো।
আসল কথা কি জানিস–
এসব চাবি হলো সততার, সত্যের, যুক্তির, নিষ্ঠার
আজকাল আর এসব দিয়ে কোন দরজা খোলে না।
তবুও তুই ফেলে দিস না
যত্ন করে তুলে রেখে দিস।
তুইও যখন চলে যাবি
তোর সন্তানদের হাতে দিয়ে যাস সেসব চাবিরগুচ্ছ।
হয়তো তাদের হাতে আবার একদিন–ওই সব চাবি দিয়ে,
ওই সব দরজাগুলো খুলে যাবে।’
লেখক: মুক্তিযুদ্ধ গবেষক