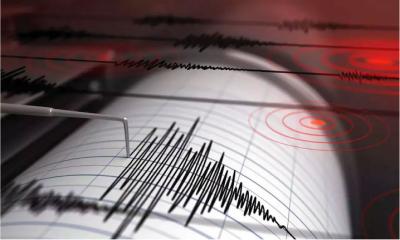ট্রেনিং শেষে আমাকে পাঠানো হয় কুর্মিটোলায়, বিমানবাহিনীর ব্যারাকে। ১৯৭০ সালের শেষের দিকের ঘটনা। সন্ধ্যায় ব্যারাকের বাইরে আড্ডা দিচ্ছি আনিসুর, দেলোয়ার, দেলোয়ার রহমানসহ পাঁচজন। একসঙ্গে দেখে একদল পাঞ্জাবি আমাদের ‘মাদার--’ বলে গালি দেয়। শুনে ঠিক থাকতে পারি না। সবাই ছিলাম কমান্ডো। ওদের দশজনকে এমন ধোলাই দিই যে পরে ওদের হাসপাতালে নিতে হয়েছিল। ঘটনাটি ব্যারাকের বাইরে হওয়ায় চাকরি হারাইনি। তবে আমাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় সেন্ট্রাল জেলে। পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে হাতাহাতির খবরটি পৌঁছে যায় আওয়ামী লীগ নেতা গাজী গোলাম মোস্তফার কাছে। জামিন করে তিনিই আমাদের জেল থেকে বের করে আনেন। অতঃপর পল্টনে তাঁর বাসার দুটি রুমে ঠাঁই হয় আমাদের।
যুদ্ধদিনের কথা শুনছিলাম যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান বীরপ্রতীকের মুখে। তাঁর বাড়ি নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার চর মল্লিকপুর গ্রামে। তিন ভাই ও দুই বোনের সংসারে মতিউর সবার ছোট। দুই বছর বয়সেই মারা যান তার বাবা আবদুল কাদের মৃধা। মতিউর লেখাপড়া করেন মল্লিকপুর প্রাইমারি স্কুলে। পরে লোহাগড়া পাইলট স্কুলে পড়েন নবম শ্রেণি পর্যন্ত। এরপর চলে যান খুলনার খালিশপুরে। সপ্তাহে দশ টাকা বেতনে কাজ করেন ক্রিসেন্ট জুট মিলে। সেখানে কিছুদিন কাজ করার পর মতিউর যোগ দেন সেনাবাহিনীতে। তার ভাষায়—
‘ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭। সেনাবাহিনীতে ভর্তির খবর পেয়ে খুলনা সার্কিট হাউসে গিয়ে লাইনে দাঁড়াই। এক অফিসার এসে বুকে খুব জোরে থাপ্পড় মারেন। তবু আমি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। পরে তিনি বুকে একটি সিল মেরে দেন। সিপাহি হিসেবে প্রথম ট্রেনিং করি করাচিতে, ডেরা ইসমাইল খান ট্রেনিং সেন্টারে। সেখানেই এসএসজি (স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপ) নামের বিশেষ কমান্ডো ট্রেনিং করি। আমার আর্মি নং ছিল– ৮৮০৭৯১৪।’

১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হন বীরপ্রতীক মতিউর। তাঁর ডান হাতের বাহুর হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। ফলে ওই হাতে পৌনে দুই ইঞ্চি আর্টিফিশিয়াল বোন লাগিয়ে রড দিয়ে সার্পোট দেওয়া হয়েছে। এখনো ডান কাত হয়ে ঘুমালে তাঁর শরীর অবশ হয়ে যায়। লিখতে গেলে অবশ হয়ে যায় হাতটাও। ভারী কোনো জিনিস তুলতে পারেন না। এভাবেই কাটছে জীবন। আবেগ, উত্তেজনা আর মাঝে মাঝে বিষাদের সাগরে ডুবে তিনি আমাদের শুনিয়ে যান একাত্তরের নানা গল্প।
‘৭ মার্চ, ১৯৭১। বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেবেন রেসকোর্স ময়দানে। আমরা স্বেচ্ছাসেবকের কাজ পাই। এখন যেখানে শিশুপার্ক, সেখানে তৈরি হয় মঞ্চ। দুপুরের মধ্যেই গোটা মাঠ লোকে লোকারণ্য। সবাই ভেবেছে বঙ্গবন্ধু সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। কিন্তু এমনটা তিনি করলেন না। কৌশলে বললেন– ‘যা কিছু আছে, আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে।… এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’
১৬ মার্চে ব্যারাকে ফিরে আমরা বাঙালি প্লাটুনের সঙ্গে অ্যাড হই। আমাদের ২১ জনের একটি দলকে অস্ত্রসহ পাঠিয়ে দেওয়া হয় পুরাতন বিমানবন্দরের রানওয়ের উত্তর পাশে। বিমান সংরক্ষিত বাংকার ছিল সেখানে। তাঁবু গেড়ে আমরা সেটা পাহারা দিতাম।
২২ ও ২৩ মার্চ। পাঞ্জাবি ও পাঠান সেনারা এয়ারপোর্টের ভেতরে অবস্থান নেয়। তারা রণসাজের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ২৪ মার্চ রাতে ট্যাংক ও আর্টিলারি এনে জড়ো করা হয়। এসব দেখেই অনুমান করেছি ডাস্টিক কিছু ঘটবে। তাই ঘটল। পরে সেটির নাম দেওয়া হয় ‘অপারেশন সার্চলাইট’।
২৫ মার্চ রাত ১০টা। এয়ারপোর্টের আশপাশের কাফরুল, শেওড়াপাড়া, কাজীপাড়া গ্রামগুলোতে তারা ঢুকে ব্যাপক অত্যাচার চালায়। দূর থেকে শত মানুষের আর্তচিৎকার শুনি। ওই সময় পুরো ঢাকা ছিল ব্ল্যাক আউট। কোথাও কোনো আলো ছিল না!
নায়েক সিদ্দিকুর রহমানের সঙ্গে পরামর্শ করে সিভিল পোশাকে অস্ত্রসহ আমরা তালতলা দিয়ে বেরিয়ে যাই। পরে রাজাবাজার দিয়ে রেসকোর্স ময়দান পার হয়ে চলে আসি ফুলবাড়িয়া স্টেশনে। ঠাটারি বাজারের কাছে এসে দেখা হয় নাদির ও শামসুর দলের সঙ্গে। তারা ছিল ওই এলাকার নামকরা গুণ্ডা। কিন্তু দেশের টানে নেমে এসেছিল পথে।
রাত তখন ১২টা ১ মিনিট। পাকিস্তানি সেনারা ফিল্ড আর্টিলারি সেল ছাড়ে পিলখানা, বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজারবাগের দিকে। আমরা তখন বংশাল পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করে অস্ত্র লুট করে নিই। পরে স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে সিদ্দিক বাজার, নওয়াবপুর, কাপ্তানবাজার এলাকায় প্রতিরোধ গড়ি।
২৬ মার্চ সন্ধ্যায় নওয়াবপুর মোড়ে সেনাদের গুলিতে শহীদ হয় নাদির। এলাকায় ঢুকে পড়ে আর্মিরা। তখন ওয়ারির খ্রিষ্টান কবরস্থানে অস্ত্র লুকিয়ে আমরা চলে যাই নরসিংদীতে। সেখানে পাকিস্তানি সেনারা এয়ার অ্যাটাক করে। ফলে শাহ আলম নামে এক ছেলের সঙ্গে লঞ্চে করে আমি চলে আসি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে।
শাহ আলমের বাবা মজিবুর রহমান ছিলেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি। বাড়ি গোপালপুরে। পুলিশ, আনসারসহ উনি ৩৫ জনের একটি দল রেডি করে রেখেছিলেন। আমাকে পেয়ে তিনি খুশি হলেন। ১ এপ্রিল, ১৯৭১। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গোকর্নঘাটে আমরা ফোর বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে যুক্ত হই। সেখানকার দায়িত্বে ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ। হাবিলদার আবদুল হালিমের নেতৃত্বে আমাদের একটি প্লাটুন তৈরি করে দেওয়া হয়। আমরা ডিউটি করি গোকর্নঘাট থেকে ২ কিলোমিটার উত্তরে মেঘনা নদীর তীরে।
এপ্রিলের তখন শুরু। মেঘনা নদীতে পাকিস্তানি যুদ্ধজাহাজ আমরা ডুবিয়ে দিব। নদীর কচুরিপানা ক্যামোফ্লেজ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। একটি স্পিডবোটের নিচে তিনটি ও ওপরে আড়াআড়িভাবে দুটি কলাগাছের টুকরো দিয়ে আরআর (রকেট লাঞ্চার) ফিট করে কচুরিপানা দিয়ে ঢেকে দিই। সাঁতরিয়ে ধাক্কা দিয়ে আমরা সেটি সামনে নিই। কাছাকাছি আসতেই আরআর-এ গোলা ভরে দেয় নায়েক মনির। ফায়ার করেন ক্যাপ্টেন গফফার। তিনটি ফায়ারেই ডুবে যায় পাকিস্তানি সেনাদের জাহাজটি।
এতে ক্ষিপ্ত হয়ে আশপাশে তারা ব্যাপক বিমান হামলা চালায়। ফলে ফোর বেঙ্গল রেজিমেন্ট শিফট করে চলে যায় আখাউড়া রেলওয়ে জংশনে। সেখানে হত্যার করুণ দৃশ্য দেখে মনটা হু হু করে ওঠে। ত্রিশের মতো পুরুষের পাশে পড়ে আছে জনা বিশেক নারীর লাশ। দেহ ক্ষতবিক্ষত। কারও স্তন নেই। কারও হাত কাটা। কারও যৌনাঙ্গে গাছের ডাল ঢোকানো। স্থানীয় বিহারিরা পাকিস্তানি সেনাদের সহযোগিতায় এভাবেই সেখানে বাঙালি নিধন করেছিল। এসব দেখে আমরা ঠিক থাকতে পারি না।’
এক অপারেশনে রক্তাক্ত হন এই বীর। কীভাবে?
তিনি বলেন, ‘চন্দ্রপুর গ্রামে ছিল আমাদের সি কোম্পানির ডিফেন্স। কমান্ডে লেফটেন্যান্ট আজিজ। সেখান থেকে দুইশ গজ উত্তরে লতিয়া মোড়ায় ছিল পাকিস্তানিদের শক্তিশালী ঘাঁটি। তারা অস্ত্র সেখানে জমা করে আগরতলার দিকে আর্টিলারি ছুড়ত। আমরা দেড় শ মুক্তিযোদ্ধা। অন্য পাশে ছিল ইন্ডিয়ান আর্মির একটি কোম্পানি। তিন দিন ধরে চলে রেকি ও ব্রিফিং।
২১ নভেম্বর, ১৯৭১। রাত ১২টার পর অপারেশন শুরু হয়। ইন্ডিয়ান আর্মি আক্রমণ করে লতিয়া মোড়ার পূর্ব দিকে। রেললাইনের ওপর দিয়ে ক্রলিং করে চন্দ্রপুর গ্রামের পূর্ব দিকে আমরা এগোই। পরিকল্পনা ছিল ওদের বাংকারের পেছনে পৌঁছে আমরা ফায়ার ওপেন করব। কিন্তু তা হলো না। একশ গজের ভেতরে প্রবেশ করতেই ওরা ফায়ার ওপেন করে দেয়। বেরি লাইট নিক্ষেপ করে আমাদের অবস্থান জেনে যায়। ধানক্ষেতে আমরা তখন পজিশন নিই।
তুমুল গুলি চলছিল। পাশে লেফটেন্যান্ট আজিজ, উত্তরে হাবিলদার আবদুল হালিম বীর বিক্রম। শোঁ শোঁ করে গুলি আসছে। খানিক পরেই দেখি তাদের নিথর দেহ পড়ে আছে। নিজেকে সামলে নিই। ক্রলিং করে দক্ষিণ পাশের একটি বাংকারের নিচে আসি। আমার হাতে একটা থাট্টি সি হ্যান্ড গ্রেনেড। অপেক্ষায় থাকি। ফায়ার বন্ধ হলেই থ্রো করব। তাই করলাম। কিন্তু সে মুহূর্তেই ব্রাশ এসে লাগে আমার ডান হাতে।
প্রথমে কিছুই বুঝিনি। মনে হলো কেউ যেন রাইফেল দিয়ে হাতে বাড়ি দিয়েছে। ডান হাত কোথায়? কোনো বোধ নেই। ভাবলাম, হাত কেটে পড়ে গেছে। পরে খেয়াল করে দেখি ডান হাতের বাহুর হাড় গুঁড়ো হয়ে হাতটি পেছনে উল্টো হয়ে উঠে গেছে। প্রচণ্ড ব্যথা। সহযোদ্ধারা ইনজেকশন দিতেই আমার শরীর ঢলে পড়ে। জ্ঞান ফিরতে দেখলাম, আমি আসামের গৌহাটি হাসপাতালে।’
যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের মানসিকতার উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন–‘‘বাঙালি মেয়েদেরকে ওরা মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করত। আমাদের সঙ্গে যখন পেরে উঠত না তখন মেয়েদের উলঙ্গ করে বাংকারের ওপর শুইয়ে দিয়ে মাইকে চিৎকার করে বলত, ‘মার, তেরা বেহেন কো মার’।
দীর্ঘশ্বাস ফেলে মতিউর বলেন–
“ওই ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সেনা যাদের আত্মসমর্পণের পর ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, আমি মনে করি তাদেরও বিচার করা উচিত ছিল।”
মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকারদের কার্যক্রম কেমন দেখেছেন জানতে চাইলে তিনি জানালেন–
“ওদের মূল কাজ ছিল গ্রামে গ্রামে ঘুরে ধনসম্পদ লুট করা ও বাঙালি মেয়েদের পাকিস্তানি সেনাদের হাতে তুলে দেওয়া। সেনারা যখন গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দিত, রাজাকাররা তখন ধন-সম্পদ লুট করত। তারা যদি পথ চিনিয়ে, লোক দেখিয়ে না দিত তবে পাকিস্তানি সেনারা এত লোক হত্যা করতে পারত না।”
বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গ উঠতেই এই বীরপ্রতীকের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়। অতঃপর তিনি বলেন–
“বঙ্গবন্ধু না হলে মুক্তিযুদ্ধ হতো না। বাঙালির মনে জাতীয়তাবোধের জন্মদাতা তিনি। একাত্তরে পাকিস্তানিরা তাঁর কিছুই করতে পারেনি। অথচ স্বাধীন দেশে তাঁকে সপরিবার নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বিশ্ব ইতিহাসে আমরা শুধু বীরের জাতি নই, নিমকহারাম ও খুনির জাতিতেও পরিণত হয়েছি।”
মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ভালো লাগার কথা জানতে চাই আমরা। চোখেমুখে আলো ছড়িয়ে তিনি বলেন–
‘আমাদের ছেলেরা বিদেশের মাটিতে যখন সফল হয়, কর্মজীবী লাখো নারী যখন স্বাধীন দেশে নিজেদের যোগ্যতা স্পষ্ট করে, দেশের প্রবৃদ্ধি এগিয়ে নেয়–তখন সত্যি খুব ভালো লাগে।”
এই বীর মুক্তিযোদ্ধা এখন প্রয়াত। কিন্তু তার বলা কথাগুলো আমাদের কাছে ইতিহাস হয়েই থাকবে। পরবর্তী প্রজন্মের হাত ধরেই দেশটা একদিন অনেক উন্নত হবে–এমনটাই আশা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা বীরপ্রতীক মতিউর রহমানের। তাই তাদের উদ্দেশেই তিনি বলে গেছেন শেষ কথাগুলো–
“তোমরা ঠিকভাবে লেখাপড়া কর, জ্ঞান অর্জন করে তা দেশের কাজে লাগিও। দেশটাকে ভালোবেস। তা না হলে তোমার সব অর্জনই বৃথা হয়ে যাবে।”
লেখক: মুক্তিযুদ্ধ গবেষক