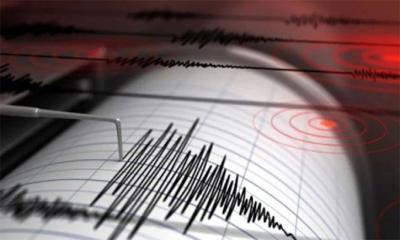প্রতিদিন, প্রায় সব কটি টিভি চ্যানেলে, প্রতি পাঁচ মিনিটে কমপক্ষে দুবার করে আমরা দেখছি বা দেখতে বাধ্য হচ্ছি যে হরলিকস খেলে বাচ্চারা মোটাতাজা হয়। লম্বা হয়। হয় বুদ্ধিমান। তো কিশোর-তরুণেরা হরলিকস খেতে পাগল হবে; আর তাদের মা-বাবারাও যেভাবে পারুক হরলিকস কেনার টাকার জোগান দেবেই দেবে। কিন্তু এই যে আমরা বই পড়ার কথা বলছি, বই তারা কেন পড়বে? আর অভিভাবকেরাই-বা কেন বই পড়ার পেছনে টাকা ঢালবেন? কী লাভ বই পড়ে?
মাত্র কয়েক দশক আগেও এ-বঙ্গে এমন প্রশ্ন কেউ তোলেননি। তোলেননি, কারণ তোলার প্রয়োজনই হয়নি। ভারত ভাগ হয়ে যখন পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্গত হয়, তখন আমাদের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর হার ছিল তলানিতে। আর অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল পরিবারের সংখ্যা ছিল আরও কম। তখনো স্বল্প আয়ের অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের সর্বাগ্রে বিদ্যালয়ে পাঠানোর কথা ভাবতেন। তাদের হাতে বই তুলে দিতেন। কেননা, তারা চাইতেন তাদের সন্তানরা মানুষ হোক। আর সন্তানকে মানুষ বানাতে হলে যে প্রকৃত শিক্ষার ও বইয়ের বিকল্প নেই, এটা তারা খুব ভালোভাবে বুঝতেন। অথচ তারা কিন্তু বিদ্যায়-বুদ্ধিতে আহামরি গোছের পণ্ডিত ছিলেন না। বরং তাদের বড় অংশই ছিলেন কৃষিজীবী সাদামাটা মানুষ। আর একটি অংশ ছিলেন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ছোট কিংবা বড়জোর মাঝারি পর্যায়ের চাকুরে। তাদের জীবনও ছিল অনাড়ম্বর।
তারপরও, সেই সময়ের বাঙালিরা সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ করার জন্য কতটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তার সর্বোত্তম উদাহরণ হিসেবে বঙ্গবন্ধু-পরিবারের ছবিটি সামনে আনা যায়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম ১৯২০ সালে। লক্ষ করুন, আজ থেকে একশ বছর আগে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার একজন পিতা তাঁর সন্তানকে সুশিক্ষার জন্য একের পর এক বিদ্যালয় বদল করছেন। উচ্চশিক্ষার্থে পাঠাচ্ছেন কলকাতায়। সেই পিতা জানতেন, কেবল বিদ্যালয়ে তোতা পাখির মতো বই মুখস্থ করলে সন্তান যথার্থ মানুষ হয় না; এর জন্য আরও অনেক কিছু দরকার। তারই অংশ হিসেবে তিনি, শেখ লুৎফর রহমান, সন্তানকে ফুটবল খেলার সুযোগ করে দিয়েছেন। নিজেও প্রতিপক্ষ হিসেবে অংশ নিয়েছেন সেই খেলায়। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এটি তিনি করেছেন মূলত সন্তানকে উৎসাহিত করবার জন্য। শুধু তা-ই নয়, সন্তান যখন অন্যায়ের প্রতিবাদ করে জেলে যাচ্ছেন, আর্তমানবতার সেবায় নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছেন এবং পরাধীন স্বদেশবাসীর কল্যাণে রাজনীতি করছেন, তখনো তিনি সানন্দে তাতে সায় দিয়ে যাচ্ছেন। পাড়া-প্রতিবেশীদের নানা অভিযোগ-অনুযোগের জবাবে বলছেন, ‘দেশের কাজ করছে, অন্যায় তো করছে না; যদি জেল খাটতে হয়, খাটবে; তাতে আমি দুঃখ পাব না।’ (শেখ মুজিবুর রহমান, ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’, পৃষ্ঠা ২১)। তো, এমন পিতার ছেলে জাতির পিতা ও ত্রাতা হবে না তো, কে হবে?
সন্তানকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী একজন মুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার যে সাধনা, এটি যদি হয় তার এক পিঠ, তবে অন্য পিঠটি ছিল নিশ্চিতভাবে বই পড়া। শৈশবে সেই দীক্ষাও বঙ্গবন্ধু পেয়েছিলেন পরিবার থেকেই। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, ‘আমার আব্বা খবরের কাগজ রাখতেন। আনন্দবাজার, বসুমতী, আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী ও সওগাত। ছোটকাল থেকেই আমি সকল কাগজই পড়তাম।’ (শেখ মুজিবুর রহমান, ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’, পৃষ্ঠা ১০) পরিবার থেকে প্রাপ্ত এই যে পরম্পরা, সবাই জানেন, তা আমৃত্যু অটুট ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনে। তাঁর অত্যন্ত প্রিয় একটি ব্যক্তিগত লাইব্রেরী ছিল ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বাড়িতে। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ জেলজীবনে তাঁর একমাত্র চাওয়া ছিল বই। বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:
১৯৪৯ সাল থেকে আব্বা যতবার জেলে গেছেন, কয়েকখানা নির্দিষ্ট বই ছিল, যা সব সময় আব্বার সঙ্গে থাকত।...তার মধ্যে রবীন্দ্র রচনাবলী, শরৎচন্দ্র রচনাবলী, নজরুলের রচনা, বার্নাড শ, রাসেল, শেলী ও কীটসসহ বেশ কয়েকখানা বই। এর মধ্যে কয়েকটা বইতে সেন্সর করার সিল দেওয়া ছিল। জেলে কিছু পাঠালে সেন্সর করা হয়, অনুসন্ধান করা হয়। তারপর পাস হয়ে গেলে সিল মারা হয়। পর পর আব্বা কতবার জেলে গেলেন তার সিল এই বইগুলিতে ছিল।
...মা প্রচুর বই কিনতেন আর জেলে পাঠাতেন। নিউ মার্কেটে মার সঙ্গে আমরাও যেতাম। সব সময়ই বই কেনা ও পড়ার একটা রেওয়াজ আমাদের বাসায় ছিল। প্রচুর বই ছিল।
১৯৫১ সালে কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু গোপনে ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে লিখেছেন, ‘আমার জন্যে কিছুই পাঠাবেন না। আমার কোনো কিছুরই দরকার নাই। নতুন চীনের কিছু বই পত্রিকা যদি পাওয়া যায় তবে আমাকে পাঠাবেন।’
শতবর্ষের ব্যবধানে আরও ব্যাপক ও গভীরতর নিষ্ঠার সঙ্গে পিতার বইপ্রীতি ও পাঠ-অভ্যাসের সেই পতাকা বহন করে চলেছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর গুরুদায়িত্বে থেকেও তিনি নিয়মিত লিখছেন এবং সম্পাদনা করছেন জাতির পিতার অমূল্য রচনাসম্ভার এবং ‘সিক্রেট ডকুমেন্টস’-এর মতো কঠিন ও শ্রমসাধ্য গ্রন্থাবলি। বলা বাহুল্য, বইয়ের প্রতি যথার্থ ভালোবাসা না থাকলে এ কখনোই সম্ভব হতো না। গোটা বিংশ শতাব্দীজুড়ে অবিভক্ত বঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রাজনীতিসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে পৃথিবী আলোকিত করা যে-সব মনীষীর সাক্ষাৎ আমরা পাই, তাদের বেড়ে ওঠার মাটি বা পশ্চাৎভূমিও ভিন্ন নয়। কিন্তু সবই এখন রূপকথার গল্পের মতোই স্মৃতি মাত্র।
২.
এখন দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সব মা-বাবাই চান তার সন্তান জিপিএ-৫ পাক। ক্লাসে সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট করুক। বৃত্তি নিয়ে অথবা জায়গা-জমি বিক্রি করে হলেও বিদেশে চলে যাক। নামি-দামি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুক। সর্বাধিক সুযোগসুবিধা-সংবলিত সবচেয়ে লোভনীয় চাকরিটি তার করায়ত্ত হোক। এ লক্ষ্যে শিশুকাল থেকেই তারা তাদের সন্তানকে একসঙ্গে একাধিক কোচিংয়ে পাঠাচ্ছেন। সবচেয়ে ভালো না হলেও সবচেয়ে দামি বিদ্যালয়ে পড়ানোর চেষ্টা করছেন। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢেলে তারা সন্তানকে ভালো চাকুরে কিংবা পারিবারিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সিইও বানানোর সর্বাত্মক প্রয়াস চালাচ্ছেন। অনেকে কামিয়াবও হচ্ছেন এ ক্ষেত্রে।
যাদের সেই সংগতি নেই সেই সব নিম্নমধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারও কিন্তু কম মরিয়া নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারাও ভিটেমাটি বিক্রি করে সন্তানকে বিদেশে পাঠাচ্ছেন। অথবা কোনো না কোনোভাবে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা তথাকথিত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষার সনদ পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। নামসর্বস্ব সেই সনদ নিয়ে বছরের পর বছর নানা কোচিং সেন্টারে অঢেল অর্থ ঢেলে তাদের সন্তানরা চেষ্টা করছেন কোনোমতে একটি লাভজনক চাকরি বাগিয়ে নিতে। লাভজনক মানে যেখানে বাড়তি উপার্জনের সুযোগ আছে। সবাই জানেন, অবৈধভাবে বিদেশ পাড়ি দিতে গিয়ে অনেকে ভূমধ্যসাগরে ডুবে মরছেন; আর একটি অংশ পাচারচক্রের ফাঁদে পড়ে প্রবাসে পচে মরছেন জেলে। কিন্তু তারপরও ভূমধ্যসাগরমুখী অবৈধ কাফেলা থেমে নেই।
লক্ষ্য একটাই, অর্থ উপার্জন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে এটাই এখন সমাজের মোক্ষ বা মূল অভীষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ হওয়ার সাধনা থেকে বিপজ্জনকভাবে বিচ্যুত হয়ে শ্রেণিনির্বিশেষে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের এই যে অর্থ বা ক্যারিয়ারমুখী মরিয়া অবস্থান, এটা শুধু যে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে বইবিমুখ করে তুলছে তা-ই নয়, উপরন্তু যে চেতনা নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল, সেই চেতনার ভিত্তিতে অসাম্প্রদায়িক মুক্ত সমাজ গঠনের ক্ষেত্রেও বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে সঙ্গে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে সৃজনশীল ও মননশীলতার চর্চা, যা ছিল পঞ্চাশের ও ষাটের দশকে মুক্তিকামী বাঙালির সবচেয়ে দামি সম্পদ।
এখন পরিবার, সমাজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেউই যদি কিশোর-তরুণদের বই পড়ার কথা না বলে, বরং পরীক্ষা-কোচিং ও চাকরির মোহচক্রজালে সর্বক্ষণ তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখে, তাহলে কীভাবে আমরা আশা করব যে আমাদের সন্তানরা বইমুখী হবে? একদা যে পরিবারগুলো ছিল আমাদের মহান স্বাধীনতাসংগ্রামের এক একটি দুর্গ, সেই সব পরিবার থেকেও বই ও সংস্কৃতির চর্চা প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে। সুবিদিত যে প্রকৃতিতে শূন্যতার কোনো স্থান নেই। অনিবার্যভাবে সেই শূন্যস্থানটিও প্রায় পূর্ণ হয়ে গেছে ধর্মান্ধতা, ধর্ম নিয়ে অহেতুক বাড়াবাড়ি এবং নানা কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতির বেনোজলে। গভীর বেদনার সঙ্গে বলতে হয় যে পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক শাসকগোষ্ঠী বিপুল কাঠখড় পুড়িয়েও যা করতে পারেনি, বই ও সংস্কৃতিবিমুখতার কারণে ঘাপটি মেরে থাকা স্বাধীনতাবিরোধী ধর্মান্ধ গোষ্ঠী ইতোমধ্যে সহজেই তা করে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সফলভাবে তারা ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার বিষ। উদ্বেগের বিষয় হলো, রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্ব ও সংঘাতকবলিত বর্তমান বিশ্ববাস্তবতায় এ যে কত বড় বিপদ, তা সম্ভবত কেউ আঁচ করতে পারছেন না।
৩.
বিপদ আরও আছে। দ্বিতীয় বড় বিপদটি সম্ভবত প্রযুক্তির। সত্য যে প্রযুক্তিবিপ্লব আমাদের জীবনকে এক লাফে একশ বছর এগিয়ে দিয়েছে, কিন্তু ক্ষতিও কম করেনি। এ যেন অনেকটা এ অঞ্চলের জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার মতো। এ ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় বিস্তর পলিমাটি নিয়ে আসে। জমিকে দেয় বিপুল উর্বরতা। কিন্তু তছনছ করে যায় আমাদের ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, হাটবাজার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সেই ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে লেগে যায় বছরের পর বছর। আবার বন্যা বা জলোচ্ছ্বাস কেবল পলিমাটিই বয়ে নিয়ে আসে না, সঙ্গে অনেক পচা-গলা আবর্জনাও নিয়ে আসে। নিয়ে আসে নানা রোগব্যাধিও।
শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজের তাৎক্ষণিক লাভমুখী মানসিকতার কারণে এমনিতেই কিশোর-তরুণদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে, তার মধ্যেও যেটুকু অবকাশ তারা পাচ্ছে সেটুকুও উত্তপ্ত বালুর মতো চুয়ে নিচ্ছে প্রযুক্তির সহজলভ্যতাজাত নানা সামাজিক মাধ্যম। অনেক ক্ষেত্রে এটা আসক্তির মতো হয়ে উঠেছে। এ আসক্তির কারণে নিদ্রা ও স্বস্তিহীন হয়ে উঠছে তাদের জীবন। মুহূর্তের জন্যও ডিভাইসের বাইরে আর কোনো কিছুতেই তারা আর মনোযোগী হতে পারছে না। শুধু তরুণদের কথাই-বা বলি কেন, বড়রা ব্যতিক্রম নন। দেখা যায়, খাবার টেবিলে পরিবারের চারজন সদস্য বসে খাচ্ছেন। কিন্তু কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছেন না। এমনকি খাবারের দিকেও নয়। সবার চোখ মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে।
আরও ভয়ের বিষয় হলো, সমাজের উচ্চপদে আসীন বহু শিক্ষিত মানুষও জ্ঞান ও তথ্যকে গুলিয়ে ফেলতে শুরু করেছেন। তথ্য ও জ্ঞান যে একজিনিস নয়, তা কোনোভাবেই তাদের বোঝানো যাচ্ছে না। তারা ভাবছেন (এবং চড়া গলায় বলছেনও) যে বই পড়ার কী দরকার, গুগলেই তো সব আছে! বইবিরোধী যত প্রবণতা চারপাশে ঘনীভূত হয়ে উঠছে, তার মধ্যে এটিও কোনো অংশে কম ক্ষতিকর নয়।
৪.
এই যে এত সব বৈরী পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি বছরের পর বছর ধরে, তার বিপরীতে আমরা যারা বইবান্ধব ও জ্ঞাননির্ভর সমাজ গঠনের কথা বলছি, বাস্তবে তারা কী ভূমিকা নিয়েছি, তা-ও খতিয়ে দেখার সময় এসেছে। বইসংশ্লিষ্ট পক্ষও তো কম নয়। প্রথমেই আসা যাক প্রকাশকদের প্রসঙ্গে। গ্রন্থকেন্দ্র যখন বই কেনার বিজ্ঞাপন দেয়, তাতে প্রতিবছর গড়ে ৫০০ প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। তার মানে হলো, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চার শতাধিক প্রকাশক এ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। অন্য সব বিবেচনা বাদ দিয়ে কেবল ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকেও আমরা যদি বিষয়টিকে দেখি তাহলে অনিবার্যভাবে যে-প্রশ্নটি সামনে চলে আসে, সেটি হলো বই যদি তাদের পণ্য হয় তাহলে এ পণ্যের বাজার সৃষ্টির জন্য তারা কী করছেন?
হরলিকস কোম্পানিকে যুক্তরাজ্যে তাদের ব্যবসা গুটাতে হয়েছে। ভারতেও তারা নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়েছে। কারণ তারা যা যা দাবি করছে, গবেষণায় দেখা গেছে তার একটিও সত্য নয়। তারপরও নানা কৌশলে আগ্রাসী উপায়ে শিশুকিশোরদের তারা হরলিকস গেলাচ্ছেন। এমনকি টার্গেট করেছেন গর্ভবতী মায়েদেরও। একইভাবে যারা রং ফর্সা করার ক্রিম বিক্রি করছেন, তাতে আদৌ কোনো ফল হোক বা না হোক, তারা কিন্তু পৃথিবীর কোটি কোটি তরুণ-তরুণীর তা কেনাচ্ছেনও সুকৌশলে। কিন্তু বই এত স্বচ্ছ ও অমূল্য একটি পণ্য তার প্রতি দেশের কিশোর-তরুণদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রকাশকদের কোনো উদ্যোগ কি আছে? থাকলেও তার প্রভাব এত ক্ষীণ যে তা আমার নজর এড়িয়ে গেছে। বইয়ের সপক্ষে সরকারি-বেসরকারি টেলিভিশনে বা পত্রপত্রিকায় তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো প্রচারণা দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।
সমাজের সবচেয়ে প্রভাবশালী দুটি প্রতিষ্ঠানের একটি হলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আমাদের শৈশবে প্রাথমিক বিদ্যালয়েও সপ্তাহে বই ও সংস্কৃতিকেন্দ্রিক একটি ক্লাস হতো। সেখানে শিক্ষক-ছাত্র সবাই অংশ নিত। এ ক্লাসটির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের বই ও সংস্কৃতিচর্চার প্রতি আগ্রহী করে তোলা। এখন কোথাও এ ধরনের কোনো উদ্যোগ আছে কি না, আমার জানা নেই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অবশ্যই পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি পাঠ্যসূচিবহির্ভূত সৃজনশীল ও মননশীল বই পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলার দৃশ্যমান ও কার্যকর উদ্যোগ থাকতে হবে। সর্বোপরি, খোলনলচে বদলাতে হবে কোচিংনির্ভর ও ফলাফলসর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থার। এ ছাড়া বর্তমান বিপর্যয়কর অবস্থা থেকে পরিত্রাণের কোনো পথ খোলা নেই।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পর সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানটি হলো পরিবার। আগেই বলা হয়েছে যে সেই পরিবারগুলোর একটি বৃহৎ অংশ বই ও সংস্কৃতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সন্তানকে প্রকৃত মানুষ করার পরিবর্তে তারাও এখন ভালো রেজাল্ট ও ভালো চাকরিকেই সন্তানের জন্য মোক্ষ জ্ঞান করছেন। এখানে একটা বড় ধরনের ঝাঁকুনি দরকার। কে দেবেন সেই ঝাঁকুনি? আমার মনে হয়, দেশবরেণ্য রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীরাই সেটা পারেন। পরিবারগুলোর মানসিকতার পরিবর্তন করা না গেলে কিশোর ও তরুণদের বই ও সংস্কৃতিমুখী করা যাবে বলে মনে হয় না।
এরপরেই আসে সমাজের ভূমিকার প্রসঙ্গ। পঞ্চাশের ও ষাটের দশকে আমাদের স্বাধীনতার ভিত্তি রচনার দিনগুলোতে ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে সমাজই যে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। পাড়া-মহল্লায় অজস্র ক্লাব ও সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল। তারা সেদিন পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিরুদ্ধে জোরালো সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পাশাপাশি গ্রন্থাগারের ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হয়েছিল। আমাদের মহল্লার ‘নবারুণ সংঘ’-এর কথা আমার মনে আছে। সংগঠনটি সব বয়সের যুবক-তরুণ ও কিশোরদের সংগঠিত করার পাশাপাশি নিয়মিত আমাদের বইও সরবরাহ করেছে। ম্যাক্সিম গোর্কির ‘মা’সহ কী অসাধারণ সব বই। আজও ভাবলে শিহরিত হই। এখন আবারও সে ধরনের একটি সুসংগঠিত উদ্যোগ ও সাংস্কৃতিক জাগরণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের তালিকাভুক্ত ও অনুদানপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলোকে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই মুখ্য ভূমিকা নিতে হবে। পাশাপাশি এগিয়ে আসতে হবে অন্য সব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনকেও।
লেখক : কবি ও প্রাবন্ধিক। পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র।