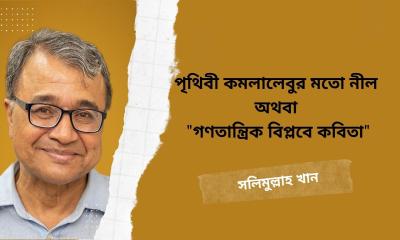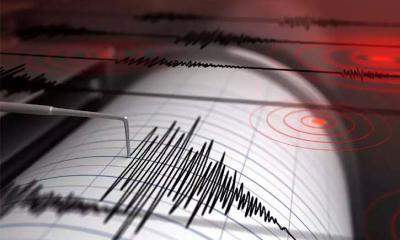একেবারে নীরবেই পার হয়ে গেল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জন্মশতবর্ষের তারিখটি—১৫ আগস্ট ২০২২। আমাদের জাতীয় শোক দিবসের দিন হওয়ায় ১৫ আগস্টে অন্য কোনো আয়োজন প্রায়ই হয়ে ওঠে না, কিন্তু উপলক্ষকে অভিন্ন রেখে উদ্যাপনের তারিখটি বদলে যেকোনো আয়োজনই সম্ভব নয় কি? সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর মতো লেখক, যিনি বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের একটি অবিস্মরণীয় মাইলস্টোন, বাংলা সাহিত্যেরই একজন মৌলিক সাহিত্যিক, তাঁর আবির্ভাবের একশ বছর পূর্তি উদ্যাপন; কেবল ওই তারিখটিতেই নয়, ২০২২ সালজুড়েই আয়োজিত হওয়ার কথা। কিন্তু আমাদের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠাপোষণাকারী বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর সে রকম কোনো আয়োজন এখনো দৃষ্টিগোচর হয়েছে কি? আমার ক্ষীণদৃষ্টির অন্তরালে কিছু হয়ে থাকলে তাকে সাধুবাদ জানাই, না-হলেও ওয়ালীউল্লাহর কোনো ক্ষতি নেই। ক্ষতি যদি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেটা বাংলা সাহিত্যের; কেননা, বড় বড় লেখককে স্মরণ করা মানে হলো নতুন লেখকদের কাছে তাঁদের মহৎ পূর্বসূরিদের তুলে ধরা, নতুন করে চেনার বা আবিষ্কারের সুযোগ করে দেওয়া আর নতুন নতুন সৃজনপ্রক্রিয়ায় প্রেরণা দেওয়া।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ১৯২২ সালের ১৫ আগস্ট চট্টগ্রামের ষোলশহরে জন্মেছিলেন। তাঁদের আদি নিবাস ছিল নোয়াখালী। বাবা সৈয়দ আহমদউল্লাহ্ সেই আমলে এমএ পাস করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। মা নাসিম আরা ছিলেন আরও বেশি বনেদি পরিবারের মেয়ে। নাসিম আরার পিতা, ওয়ালীউল্লাহর মাতামহ ছিলেন কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে পাস করা আইনশাস্ত্রের গ্র্যাজুয়েট। বড় মামা কেবল উচ্চশিক্ষিতই ছিলেন না, কর্মজীবনের কৃতিত্বে পেয়েছিলেন ‘খান বাহাদুর’ উপাধি। ওয়ালীউল্লাহর বড় মামি ছিলেন নওয়াব আবদুল লতিফের পরিবারের মেয়ে, উর্দু ভাষার লেখিকা। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প-নাটকের উর্দু অনুবাদ করেছিলেন বলে জানা যায়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কুড়িগ্রাম হাইস্কুল থেকে ১৯৩৯ সালে মাধ্যমিক, ১৯৪১-এ ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক এবং ১৯৪৩ সালে ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন কলেজ থেকে ডিস্টিংশনসহ বিএ পাস করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এমএ ভর্তি হন। কিন্তু পড়ালেখা শেষ না-করেই ১৯৪৫ সালে ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা ‘দ্য স্টেটসম্যান’-এ চাকরি শুরু করেন। এ বছরই তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘নয়নচারা’ প্রকাশ পায় কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের পূর্বাশা লিমিটেড নামের প্রকাশনা থেকে। উল্লেখ্য, এই বইয়ের নামগল্পটিও প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত ‘পূর্বাশা’ পত্রিকার পাতায়। এই সময় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রমুখ বিখ্যাত লেখকের সঙ্গে তরুণ লেখক ওয়ালীউল্লাহর পরিচয় হয়। ১৯৪৭-এর দেশভাগ হলে ‘দ্য স্টেটসম্যান’-এর চাকরি ছেড়ে তিনি ঢাকায় এসে রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রের সহকারী বার্তা সম্পাদকের পদে নিয়েজিত হন। পরের বছরই প্রকাশিত হয় প্রথম উপন্যাস ‘লালসালু’ (১৯৪৮)। এবং এ বছরই রেডিও করাচির বার্তা সম্পাদকের চাকরি নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান। এরপর পর্যায়ক্রমে নয়াদিল্লি ও সিডনির পাকিস্তান দূতাবাসের সেক্রেটারি পদমর্যাদায় চাকরি করেন। সিডনিতে থাকতেই ফরাসি দূতাবাসের তরুণী আন-মারি লুই রোজিতা মার্সেল তিবো’র সঙ্গে পরিচয় ও প্রেম জন্মে। এরপর ওয়ালীউল্লাহ্ ঢাকায় ফিরে এলেও কিছুদিনের মধ্যেই আবার বদলি হন করাচিতে। এ সময়, ১৯৫৫ সালের ৩ অক্টোবর আন-মেরির সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। এ-বছরই ‘বহিপীর’ নাটকের জন্য পিইএন পুরস্কার পান সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, যদিও এই নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় আরও পাঁচ বছর পরে, ১৯৬০ সালে। এরপর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জাকার্তা, লন্ডন, বন এবং সবশেষ প্যারিসে চাকরি করেন। ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস ‘চাঁদের অমাবস্যা’ এবং নাটক ‘সুড়ঙ্গ’। পরের বছর প্রকাশ পায় ‘তরঙ্গভঙ্গ’ নাটক এবং ‘দুই তীর ও অন্যান্য গল্প’ নামের গল্পের বই। প্যারিসে থাকা অবস্থায়, ১৯৬৭ সালের ৮ আগস্ট লন্ডনের শ্যাটো এ্যান্ড উইন্ডাস পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত হয় ‘লালসালু’র ইংরেজি অনুবাদ ‘Tree Without Roots’। এর আগেই অবশ্য উপন্যাসটির আন-মারি কৃত ফরাসি অনুবাদ ‘র্লাব্র্ সাঁ রাসিন্’ (L`Arbre sans racines) প্রকাশ পেয়েছিল। ১৯৬৮ সালের মে মাসে ঢাকা থেকে বের হয় উপন্যাস ‘কাঁদো নদী কাঁদো’। ‘The Ugly Asian’ ওয়ালীউল্লাহর মৌলিক ইংরেজি উপন্যাস। প্রকাশিত দুটো গল্পগ্রন্থের বাইরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর ৩২টি গল্পের সন্ধান পেয়েছেন সৈয়দ আবুল মকসুদ ও সৈয়দ আকরম হোসেন। এ ছাড়া ১৯৬৩ সালে ‘উজানে মৃত্যু’ নামে একটি নাটক প্রকাশিত হয়েছিল সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত ‘সমকাল’ পত্রিকায়।
১৯৭১ সালে পাকিস্তান সরকার তাঁকে ইসলামাবাদে বদলির প্রস্তাব দিলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের তখনকার রাজনৈতিক সংঘাতের কথা মাথায় রেখে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তা গ্রহণ করেননি। আর্থিকভাবে বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েও, তিনি বরং ফ্রান্সে থেকেই বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা করেছেন। বেকার থেকে, সামান্য হলেও অর্থ সাহায্য পাঠিয়েছেন কলকাতার মুক্তিযুদ্ধ তহবিলে। দেশের যুদ্ধপরিস্থিতি ও স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বিগ্ন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ১৯৭১-এর ১০ অক্টোবরের গভীর রাত্রে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে মাত্র ৪৯ বছর বয়সে মারা যান। স্বাধীনতার পরে, বাংলাদেশের তখনকার রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী একটি বার্তায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর স্ত্রী আন-মারিকে লেখেন, ‘আমাদের দুর্ভাগ্য যে মি. ওয়ালীউল্লাহর মাপের প্রতিভার সেবা গ্রহণ থেকে এক মুক্ত বাংলাদেশ বঞ্চিত হল; আমাকে এটুকু বলার সুযোগ দিন যে আপনার ব্যক্তিগত ক্ষতি বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষতি।’ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একসময়কার উপাচার্য, বিচারপতি এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর স্কুলবন্ধু আবু সাঈদ চৌধুরীর এই বক্তব্য যে আক্ষরিকভাবেই সত্য, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর মৃত্যুর পরে ১৫ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে কলকাতার দেশ পত্রিকায় সমসাময়িক কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমান বলেছিলেন, ‘বাঙালি মুসলমানের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পেছনে সত্যিকার চেতনা নির্মাণের দায়িত্ব যারা নিয়েছিলেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁদের অন্যতম মহৎ কারিগর।’ কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর আগে মুসলিম সম্প্রদায়ে জন্ম নেওয়া কোনো কথাশিল্পী এতটা আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতার সঙ্গে বাংলা কথাসাহিত্যের মূলধারার লেখক হিসেবে এমন সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হননি। বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় তাঁকে জগদীশ গুপ্ত (১৯০৮-১৯৫৬) ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৭১) সফল উত্তরসূরি মনে করা হয়। কেউ কেউ সতীনাথ ভাদুড়ীর সঙ্গেও তুলনা করেছেন। কেউ আবার অস্তিত্ববাদী দর্শনের পুরোধা জাঁ পল সাঁত্র এবং আলবেয়ার কামুর প্রভাবের কথাও বলেছেন। অস্তিত্ববাদী দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রচনায় ‘Stream of consciousness’ বা চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহরীতির চমৎকার প্রয়োগ রয়েছে। অতএব, এ কথা বলা চলে যে শিল্পচেতনার ক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ছিলেন একই সঙ্গে দৈশিক ও আন্তর্দৈশিক পর্যায়ের।
২.
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর প্রথম এবং সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস ‘লালসালু’ বাংলা সাহিত্যেরই একটি বিশেষ মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। এই উপন্যাসের মাধ্যমেই তৎকালীন পূর্ব বাংলার কোনো লেখক আন্তর্জাতিক মহলে পরিচিতি লাভ করেন। আবহমান বাংলার মুসলিম সমাজবাস্তবতার অতুল্য দলিল ‘লালসালু’। যে এলাকা ও সম্প্রদায়ের জীবনবাস্তবতা লেখক তুলে ধরতে চেয়েছেন, উপন্যাসের শুরুর দিকেই তার রূঢ় ও নগ্ন চেহারা পাঠকের সামনে হা হয়ে পড়ে, যা । যেমন :
...শস্য নেই। যা আছে তা যৎসামান্য। শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের চেয়ে আগাছা বেশি। ভোরবেলায় এত মক্তবে আর্তনাদ ওঠে যে, মনে হয় এটা খোদাতায়ালার বিশেষ দেশ। ন্যাংটা ছেলেটাও আমসিপারা পড়ে, গলা ফাটিয়ে মৌলবীর বয়স্ক গলাকে ডুবিয়ে সমস্বরে চেঁচিয়ে পড়ে। গোঁফ উঠতে না উঠতেই কোরান হেফ্জ করা সারা। সঙ্গে সঙ্গে মুখেও কেমন একটা ভাব জাগে। হাফেজ তারা। বেহেশতে তাদের স্থান নির্দিষ্ট।
মানুষের ক্ষুধার জ্বালা সবচেয়ে নিষ্ঠুর। সেটা পূরণ করতে না-পারলে ধর্মও যে সেখানে নিরুদ্বিগ্ন হয় না, সেটা পরের অনুচ্ছেদেই তুলে ধরেন লেখক।
খোদার পথে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসার চেতনায় যেমন একটা বিশিষ্ট ভাব ফুটে ওঠে, তেমনি না খেতে পেয়ে চোখে আবার কেমন একটা ভাব জাগে। শীর্ণ দেহ নরম হয়ে ওঠে, আর স্বাভাবিক সরুগলা কেরাতের সময় মধু ছড়ালেও এদিকে দীনতায় আর অসহায়তায় ক্ষীণতর হয়ে ওঠে। তাতে দিন-কে-দিন ব্যথা-বেদনা আঁকিবুঁকি কাটে। শীর্ণ চিবুকের আশপাশে যে-কটা ফিকে দাড়ি অসংযত দৌর্বল্যে ঝুলে থাকে, তাতে মাহাত্ম্য ফোটাতে চায়, কিন্তু ক্ষুধার্ত চোখের তলে চামড়াটে চোয়ালের দীনতা ঘোচে না। কেউ কেউ আরও আশা নিয়ে আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ে।...কিন্তু কেতাবে যে বিদ্যে লেখা তা কোন এক বিগত যুগে চড়ায় পড়ে আটকে গেছে। চড়া কেটে সে-বিদ্যেকে এত যুগ অতিক্রম করিয়ে বর্তমান স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে এমন একটা লোক আবার নেই। অতএব কেতাবগুলোর বিচিত্র অক্ষরগুলো দূরান্ত কোনো অতীতকালের অরণ্যে আর্তনাদ করে।
কিন্তু এরপরও যে খোদাতায়ালার প্রতি তাদের আস্থার ঘাটতি হয়, তা কিন্তু নয়; বরং গ্রাম্য সহজ-সরল মানুষের এই ধর্ম বিশ্বাসকে পুঁজি করে মঞ্চে আবির্ভূত হয় মজিদের মতো ধূর্ত ধর্ম ব্যবসায়ী। আমজনতার সীমাহীন দারিদ্র্যের ভেতরেই সে গড়ে তোলে ক্ষমতা, সচ্ছলতা ও ভোগবাদের এক অটল প্রাসাদ। অবশ্য এই প্রাসাদ সব সময় নিষ্কণ্টক থাকে না, আক্কাস ও জমিলার মতো বিরোধী ও বিদ্রোহী সত্তার আগমন টের পাওয়া যায়। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত আক্কাস গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চায়, কিন্তু মজিদের অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা ও বিরোধিতার সঙ্গে পেরে ওঠে না। মজিদ জানে স্কুল হলে ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ পাবে, যুক্তিহীন কুসংস্কারে তাদের আর আটকানো যাবে না। অস্তিত্বের সংকট টের পেয়ে অত্যন্ত নগ্নভাবেই আক্কাসকে আক্রমণ করে। শুধু শিক্ষার বিষয় নয়, পাশের গ্রামের নতুন পীরের আগমনকেও সে অস্তিত্বের সংকট হিসেবে দেখে তীব্র প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। তার প্রভাব অন্যের সংসারের অন্দরেও চলতে থাকে, তবে তীব্রভাবে বাধা পায় জমিলার মতো সন্তানবয়সী চঞ্চল কিশোরীকে বিয়ে করে। জমিলাই শেষ পর্যন্ত মজিদের অস্তিত্বকে তীব্র চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম হয় এবং অন্যরাও যেন মেসেজ পেয়ে যায় মজিদের ক্ষমতা ও আধিপত্যের আশ্রয় লালসালুতে ঢাকা কবরখানি কতটা অন্তঃসারশূন্য।
মজিদের অস্তিত্বচেতনা এবং সেই চেতনার সংকট ‘লালসালু’ উপন্যাসের একটি মনোদার্শনিক দিক, এর সমাজবাস্তবতার দিকটি এর চেয়ে কম শক্তিশালী নয়। বরং এই ছোট্ট একটি উপন্যাসে বাস্তবতা উঠে এসেছে, অনেক বড় গবেষণাও সেই রিপোর্ট প্রকাশ করতে অক্ষম।
৩.
‘চাঁদের অমাবস্যা’র শুরু হয়েছে এভাবে—শীতের উজ্জ্বল জ্যোৎস্নারাত, তখনো কুয়াশা নাবে নাই। বাঁশঝাড়ে তাই অন্ধকারটা তেমন জমজমাট নয়। সেখানে আলো-অন্ধকারের মধ্যে যুবক শিক্ষক একটি যুবতী নারীর অর্ধ-উলঙ্গ মৃতদেহ দেখতে পায়।
যুবক শিক্ষক জ্যান্ত মুরগী খাওয়া হালকা তামাটে রঙের শেয়াল দেখেছে, বুনো বেড়ালের রক্তাক্ত মুখ দেখেছে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট-মহামারী দেখেছে, কিন্তু কখনও বিজন রাতে বাঁশঝাড়ের মধ্যে যুবতীর মৃতদেহ দেখে নাই। আলো-অন্ধকারের মধ্যে নারীর অর্ধ-উলঙ্গ মৃতদেহ দেখার ভয়ংকর অভিজ্ঞতা যুবক শিক্ষকের মনে তীব্র চিন্তাপ্রবাহ সৃষ্টি করে। চেতনে-অর্ধ-চেতনে নিজের মনের মধ্যেই সে সীমাহীন এক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বর্ণনায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যে রীতির আশ্রয় নিয়েছেন, তাকে সাহিত্যের তত্ত্বগত পরিভাষায় ‘Stream of consciousness’ বা চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহরীতি বলে। ১৮৯০ সালে উইলিয়াম জেমস তাঁর ‘প্রন্সিপল অব সাইকোলোজি’ গ্রন্থে ‘Stream of consciousness’ কথাটি ব্যবহার করেছিলেন একটি জাগ্রত মনের নিরবিচ্ছিন্ন ভাবনাপ্রবাহ এবং সচেতনতা বোঝাতে। পরবর্তীকালে এটি হয়ে ওঠে আধুনিক গল্প-উপন্যাসে ব্যবহৃত একটি ন্যারেটিভ টেকনিক বা বর্ণনাপদ্ধতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জেমস জয়েসের ‘ইউলিসিস’ (১৯২২) উপন্যাসে এই পদ্ধতির উৎকৃষ্টতম প্রয়োগ দেখা যায়। এই পদ্ধতিতে ‘লেখক চরিত্রের চেতন ও অর্ধচেতন মনে যেসব স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ভাবনা, অনুভূতি, স্মৃতি ও নানা আপাতবিচ্ছিন্ন অনুষঙ্গ ভেসে ওঠে তার সবকিছু তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এখানে ঘটনা ও কালের বাস্তব ধারাবাহিকতা ও পারম্পর্য রক্ষিত হয় না, যৌক্তিকতা কিংবা অযৌক্তিকতার বিষয়টি এখানে গুরুত্ব পায় না, চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহে ঠিক যেমনটি ধরা পড়ে তেমনটি প্রতিফলিত হয়।’
চৈতন্যের অন্তঃশীল প্রবাহরীতির এক অনন্য উদাহরণ ‘চাঁদের অমাবস্যা’। যুবক শিক্ষক আরেফ আলীর অন্তরচেতনাকে ধারণ করে ঔপন্যাসিক মনস্তত্ত্বের যে দুঃসাহসিক অভিযাত্রা দেখিয়েছেন, তাকে সমসাময়িক কথাসাহিত্যিক আবু রুশদ চরিত্রের ‘অবস্থার সঙ্গে বেমানান’ বলেছিলেন
, তবে আরেক কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক এটাকে ‘প্রায় দার্শনিক অনুসন্ধানের চেষ্টা’ বলে অভিহিত করেছেন । এবং এই দার্শনিক অনুসন্ধানের চেষ্টার ফলে উপন্যাসখানি যে সত্যিকার অর্থেই ‘Stream of consciousness’ বা চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহরীতির একটি মানদণ্ডে উন্নীত হয়েছে, এ কথা বলার অপেক্ষার রাখে না।‘চাঁদের অমাবস্যা’য় আরেফ আলীর মনোবিশ্লেষণে চৈতন্যপ্রবাহরীতির প্রয়োগ থাকলেও ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ উপন্যাসেই এই রীতির উজ্জ্বলতর প্রয়োগ রয়েছে। সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম বলেছেন, ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ বাংলা সাহিত্যে চেতনাপ্রবাহ পদ্ধতির অন্যতম সফল প্রয়াস।...জেমস জয়েস বা ডরোথি রিচার্ডসনের চমৎকারিত্ব ‘কাঁদো নদী কাঁদো তে অনুপস্থিত থাকলেও তাঁদের উদ্ভাবনী শক্তির অনেকটা আত্মস্থ করতে পেরেছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্।’
। ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ উপন্যাসের চেতনাপ্রবাহ পরিচালিত হয়েছে তবারক ভুঁইঞার গল্প ধরে, কথক ‘আমি’র (উত্তম পুরুষ) স্মৃতিচারণার ভেতর দিয়ে। স্মৃতিচারণার সূত্র ধরে গ্রোথিত হয়েছে সমগ্র কাহিনির বন্ধন। নদীর প্রবাহের মতোই প্রবাহিত হয় চেতনার অবিরাম প্রবাহ। লেখকের উক্তিতে ধরা পড়ে নদীর জলধারার বিশেষত্ব—আরো পরে মনে হয় তার মুখ দিয়ে অবলীলাক্রমে যা নিঃসৃত হয় তার ওপর সমস্ত শাসন সে হারিয়েছে, কথার ধারা রোধ করার ইচ্ছা থাকলেও রোধ করার কৌশল তার জানা নেই; বস্তুত তার বাক্যস্রোত রীতিমতো একটি নদীর ধারায় পরিণত হয়। তবে এমন একটি ধারা যা মৃদুকণ্ঠে কলতান করে, কিন্তু বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ সৃষ্টি করে না, দুর্বার বেগে ছুটে যায় না। সে ধারা ক্রমশ অজানা মাঠ-প্রান্তর গ্রাম-জনপদ চড়াই-উতরাই দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে।উপন্যাসের প্রথম দিকে তবারক ভুঁইঞার কথা শুনে কথক ‘আমি’র একবার মনে হয়েছে, ‘তার কথা আমার স্মৃতির পর্দায় কোথায় যেন হঠাৎ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।’ বস্তুত সমগ্র উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে স্মৃতির সংক্রমণে। আর দশটা উপন্যাসের মতো তাই পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত হয়নি ‘কাঁদো নদী কাঁদো’, জলধারার মতো বয়ে চলে গেছে অবিরল। স্মৃতি সঞ্চারী কথক তবারক ভুঁইঞা কাহিনির সূত্রধর হয়ে ফিরে এসেছে বারবার। প্রকৃত চিৎপ্রবাহরীতি উপন্যাসের মতোই এখানেও কাহিনি একটিমাত্র সরলরেখায় অগ্রসর হয়নি, জলের মতো ঘুরে ঘুরে এসেছে। কথক ‘আমি’র গল্প বর্ণনায় আর কথক তবারক ভুঁইঞার স্মৃতি সংক্রামে একটি কাহিনির চরিত্রেরা যেন নাগর দোলার মতো ঘুরেছে-ফিরেছে। এভাবে বেশ কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর আমরা জানতে পারি কুমুরডাঙার ছোট হাকিম ‘মুহাম্মদ মুস্তফার জন্য খোদেজা পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করেছে।’ কিন্তু এই আত্মহত্যার কথা জানানোর পটভূমি আর পঠভূমি-উত্তর ঘটনাবলি নির্মাণ করতে লেগে যায় প্রায় সারা উপন্যাস। অন্যদিকে খোদেজার পথ ধরে মুহাম্মদ মুস্তফাও একসময় আত্মহত্যা করলেও, তার আত্মহনন নয়; চৈতন্যে প্রতিফলিত স্থান ও সময়ের বিশ্লেষণই শেষ পর্যন্ত উপন্যাসের প্রাধান্য পায়। মুস্তফার চৈতন্যপ্রবাহের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে এক জটিল চেতরাপ্রবাহঋদ্ধ ভাষা উপহার দেন লেখক—
সুটকেসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে এমন সময় সেটি হঠাৎ কাঁপতে শুরু করে : সুটকেসটি যেন একটি শুষ্করক্ত গাঢ় রঙের কলিজায় পরিণত হয়েছে। সে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। হয়তো এবার দরজার নিকটে স্থাপিত লণ্ঠনের দিকে তাকায়। তবে কলিজাটি তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সেখানেও হাজির হয় এবং আকারে সহসা ছোট হয়ে লণ্ঠনের গায়ে পতঙ্গের মতো ডানা ঝাপটাতে শুরু করে। মুহাম্মদ মুস্তফা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এই আশায় যে, পতঙ্গটি পুড়ে মারা যাবে, তার চঞ্চল ক্ষুধার্ত ডানা স্তব্ধ হবে, কিন্তু পতঙ্গটি স্তব্ধ হয় না। এবার মেঝের দিকে তাকালে সেখানেও কলিজাটি দেখতে পায়; মেঝের ওপর সেটি ডাঙায় তোলা মাছের মতো ধড়ফড় করছে যেন।
সুটকেস কিংবা কলিজার এহেন বিচিত্র দৃশ্যায়ন মুস্তফার অপ্রকৃতিস্থ হৃদয়ের অবস্থা তুলে ধরে। এবং লেখকের এই বর্ণনারীতিতে পাঠকও কিছুটা সংক্রমিত হয় বৈকি। চৈতন্যের অন্তঃশীল প্রবাহরীতির প্রয়োগে এই উপস্থাপন কথাশিল্পী হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর অসাধারণ সামর্থ্যের পরিচায়ক। এমনকি নাটকের মতো একেবারে ভিন্ন ও জটিল সাহিত্য ধারাতেও যে ওয়ালীউল্লাহ্ ‘Stream of consciousness’ বা চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহরীতির প্রয়োগে সক্ষম, তার প্রমাণ ‘তরঙ্গভঙ্গ’ নাটকটি।
ওয়ালীউল্লাহ্ মূলত মনোবাস্তবতার শিল্পী। মানুষের মনের গভীরে অন্তঃশীল ফল্গুধারার মতো যে চিন্তাচেতনা নিয়ত প্রবহমান, তিনি তার নিরঙ্কুশ প্রকাশক। নিরঙ্কুশ, তবে বর্ণনায় তাঁর পরিমিতিবোধও অতুলনীয়। অসাধারণ শিল্পঋদ্ধ বর্ণনাভঙ্গিতে বিশেষ কোথাও অতিরিক্ত এক-আধটি অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহারেও সংযমী এই কথাশিল্পীর অধিকাংশ কাহিনিতেই অন্তর্বাস্তবের পাশাপাশি বহির্ববাস্তবেরও চমৎকার সমন্বয় সাধিত হতে দেখা যায়। চরিত্রের উপযুক্ত সংলাপ নির্মিতিতে যেমন পারদর্শী তেমনি সংলাপ বিরল গল্পকথনও দুর্লক্ষ্য নয়। নাগরিক ভাষা ও সংলাপেই তিনি নিম্নবিত্ত বাঙালির জীবনচিত্র নির্মাণে বিশেষ মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন। তাঁর সমগ্র সাহিত্যের খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বোধ হয় প্রগতিশীল ও স্বতন্ত্র দর্শনচেতনা। এই চেতনার দ্বারাই তিনি তাঁর প্রতিটি রচনাতেই একটি পরিষ্কার বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। অবশ্য সে বার্তা ভাষা ও ভাবগত উচ্চমার্গের কারণে খুব সাধারণ পাঠকের কাছে কখনো কখনো অস্পষ্টও থেকেছে বলে মনে হয়। তবে মৃত্যুচেতনাও ওয়ালীউল্লাহর গল্প-উপন্যাসের বড় জায়গাজুড়ে বিদ্যমান। এবং মৃত্যুর এই সর্বগ্রাসিতার মাঝেই উঠে এসেছে লেখকের স্বতন্ত্র জীবনভাবনার এক-একটি দার্শনিক রূপ।
কথাসাহিত্যে মানুষের মনঃসমীক্ষণের বিষয়টি বেশ সূক্ষ্ম ও ঝুঁকিপূর্ণ হলেও ওয়ালীউল্লাহ্ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গেই তা উতরে গেছেন। এর জন্য সহায়ক ভূমিকা রেখেছে ‘Stream of consciousness’ বা চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহরীতির সচেতন প্রয়োগ। মধ্যবিত্ত জীবনের ভাবাবেগ কাটিয়ে বস্তুসত্যে উপনীত হওয়ার মতো মনের জোর না থাকলে মনঃসমীক্ষণধর্মী রচনায় সফল হওয়ার কথা নয়।