আমার পরম প্রীতিভাজন এবং মাননীয় ইনডিপেনডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসের বজলুল মোবিন চৌধুরী, মঞ্চে উপবিষ্ট আমার স্নেহভাজন আকিমুন রহমান, সামনে ইনডিপেনডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ, আমার অতি পুরোনো-আরামদায়ক বন্ধু; এত দিন পরে দেখা হয়েছে তার সাথে। তিনি এখানে উপস্থিত আছেন। আমার খুব ভালো লাগছে, তার কারণ হচ্ছে আজকে এরা যেভাবেই হোক ‘শকুন’ বলে যে গল্পটি প্রথমে পড়ে শোনাল। এটা ষাট সালের কথা। আজকে যা-ই হোক না কেন, একসময়ে রাজশাহীতে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে, রাজশাহীর গরম তো একটা অসম্ভব ব্যপার। এই গরমের মধ্যে বুকের তলায় বালিশ দিয়ে এ-ই...দশ হাত এবং কত হবে...ছ’হাত কি আট হাত একটা ঘর। সেই ঘরে দু’টো চৌকি। তার একটিতে, ফ্যানট্যান তখন স্বপ্ন, যে মাথার ওপর ফ্যান থাকবে, বসে বুকের তলায় বালিশ দিয়ে, গল্প লিখতে বসেছিলাম, এটা বলা যাবে না। মানে, প্রত্যেকেরই নিজের কাছে মনে হয় এই ঘটনা তো বেশ মজার; লিখে রাখিনা কেন। আমিও সে রকম অবিকল একটা লিখে রেখেছিলাম। সেই দিক থেকে আমার মত, যাকে বলা যায় অশিক্ষিত গল্পকার খুব কমই এ সময় এসব গল্প লিখছে।
সাধারণত গল্পের তো নানান রকমের ব্যাপার আছে সবাই জানে, বাংলার শিক্ষকরা জানেন গল্পে এই রকম হয়, ওই রকম হয়, শেষ থাকে তারপরে চমক থাকে, তাছাড়া আরও কত রকম কি! এসবের কোনো শিক্ষা আমি নিই-ই নি। কিছু গল্প নিশ্চয়ই পড়েছিলাম, লেখক হয়ে যাওয়ার মত কিছুই না। আমি একেবারে সোজা যাকে বলা যায়, নিজের ইঞ্জিনটা নিজের স্টিম দিয়ে চালানো আরকি। সে গল্পটা যখন লিখেছিলাম, আমার ধারণা ছিল যে এটা কিছুই হয়নি। সেই গল্পটি, প্রথম আমার ঘনিষ্ঠ পাঁচ-সাতজন বন্ধুকে শোনাই, অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে আর তাদের একজনই আজ এখানে উপস্থিত। তিনি আমার সামনেই বসে আছেন। তার সঙ্গে আজকে খুব সম্ভব ছেচল্লিশ বছর পরে আমার দেখা। তো গল্পটা যখন লিখেছিলাম, সে সময়ের কথা এখন মনে পড়ছে। তখন সন্তু, ডাকনাম, আমরা সেই নামেই ডাকি। সন্তুকে আমরা বলতাম যে, আমাদের মধ্যে সবচাইতে ছেলে মানুষ, লম্বা চওড়া, বড়সড় একটা শিশু। তাতে সে খুব রাগ করত। সে আমায় কেবলই বলত যে, আপনার কথাবার্তার মধ্যে এত বার্নড এলিমেন্ট কেন থাকে? এটা তার গায়ে ছ্যাঁকা লাগার মতো হতো আরকি। সন্তু তখন এই গল্প সম্বন্ধে বলেছিল যে, এটা একটু অন্য রকম লাগছে। কিন্তু, ঠিক তেমন গল্পের মতো লাগেনি। আরেক বন্ধু বলল যে, আমি হতবাক হয়ে গেছি। আরেকজন বলল যে সবকিছু নিয়েই কি গল্প লেখা যায়! তাহলে তো বাজারের ফর্দ তৈরি করে সেটাকেও গল্প বলে চালিয়ে দিত। কত রকমের মন্তব্য যে পেয়েছিলুম এবং সব জিনিসই কত সামান্যভাবে শুরু হয় আর তারপরে কী করে এত বিরাট ব্যপার হয়ে যায়, ‘শকুন’ গল্প হয়ে যায়! এই রহস্যটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না, কী করে হয়! তো সেই দিনকার সাথে আজকের তুলনা করছি। আজকে অস্বীকার করতে পারব না যে যারা পড়লেন বা যারা পড়েছেন, তাদের হয়তো ভালো লেগেছে। মনে হয়েছে যে অন্য পাঁচটা-দশটা গল্পের মধ্যে এই গল্পটা একটু পড়ে শুনাই। সেটাই খুব অবাক লাগে আরকি। তো আজকে আমাকে যদি বলেন কী রকম করে লেখক হয়ে উঠলেন, এই বিষয়টা আমার কাছে এতই অনির্দিষ্ট একটি বিষয় যে এ নিয়ে গুছিয়ে কথা বলার তো কোনো প্রশ্নই উঠে না। যেমন, অমুক-অমুক বিষয়বস্তু ঠিক করে দেওয়া হলো প্রবন্ধ লিখার জন্য, আপনি সেইটার ওপরে লিখে আনবেন। এইটা সে রকম বিষয় কিন্তু নয়। এটা ঠিকঠাক বলার কিছু নয় এবং বলাও যাবে না কিছু। গুছিয়ে বলা তো যাবেই না।
এলোমেলো, যা মুখে আসে, যা চিন্তায় আসে তাই বলতে হবে এবং এটা খুবই ঠিক যে এটা বক্তৃতা করে বলার বিষয় না। এটা একদম কথাবর্তার মধ্য দিয়ে বলতে হবে। হ্যাঁ, একটু আগে যেটা উপাচার্য বললেন যে তোমরা বরং গোল হয়ে বসে ওকে যত রকম পারো নানান দিক থেকে প্রশ্নবিদ্ধ কর,ধর, গালাগালি কর, বল যে কিছু হয়নি। এসব করে-টরে দেখ যে যদি কিছু বের হয় আরকি। আমার মনে হয় সেটা তো আমিও অনেক স্বস্তি পাই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করলে কী রকম একটা...যাকে বলা যায় অত্যন্ত আনুষ্ঠানিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় আরকি। আমি একা বলছি আর এখানে তারা শুনছে এবং বাধ্য হয়ে শুনছে বলা যায় এই অর্থে যে কিচ্ছু বলার নেই ওদের। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি বলব, ততক্ষণ পর্যন্ত আর ওরা বলতে পারবে না। বলতে ইচ্ছে করলেও বলতে পারবে না। আমাকেই বলতে হবে। এটা তো একরকমের অনুগত হওয়ার অবস্থা। এতে তো ঠিক কাজ হয় না, পরস্পরের মধ্যে ঠিক যোগাযোগগুলো হয় না। এটা আমার মনে হয় ওই রকম আরকি, এখন একটি গল্প পড়ে শোনাই, তারপর এই গল্প শুনতে লাগল।
কিছুই বলা যায় না, শুনতে শুনতে একজনের একটু ঘুম পেয়ে যেতে পারে, হতেই পারে। একজন বলল যে, আচ্ছা, মিস করলাম, এই, এইটা কী জানি বলল কথাটা। চল ছিল বটে, একসময়, যে নিজের লেখা থেকে পাঠ। আমিও নিজের লেখা পাঠ করেছি। সেটা হতে অন্য কিছু পাওয়া যেতেও পারে কিন্তু সাহিত্য মূলত আমার মনে হয় যে. ‘একার কাছে একা’- এই রকম আরকি। যিনি কাজ করেছেন, যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই নিজেকে হাজির করছেন। তার জগৎকে হাজির করছেন। তার অভিজ্ঞতাকে হাজির করছেন। তার চিন্তাভাবনা, অনুভব, তিনি যেমন করে দুনিয়াকে দেখেছেন, যেমন দেখতে চান, যেমন তিনি মানুষের রূপ পছন্দ কিংবা অপছন্দ করেন। এ সমস্তটা তিনি খুব নিভৃতে, খুব ভালো করে লেখার চেষ্টা করেছেন। সাহিত্যিক তাই করার চেষ্টা করেন। আমি অন্তত সাহিত্য বলতে এই বুঝি। একটা গল্প বানিয়ে দিয়ে দিলাম, তারপরে কী হলো -তারপরে - ওটা ঠাকুরমার ঝুলিতে বলে। ঠাকুরমার ঝুলি তো পাওয়া যাবে না, তবে আধুনিক এই রকম ঠাকুরমার ঝুলি বাংলা সাহিত্যে প্রচুর তৈরি হচ্ছে; গাদায়-গাদায়। সেইটাই আকিমুনকে বলছিলাম যে এখন সাহিত্য পড়া আর সুখাদ্য বা সত্যিকারের খাদ্য খেতে খেতে পাঁপড় ভাজা খাওয়া , সাহিত্য প্রায় সে রকম একটা ব্যপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাতে আমার পুষ্টি হতে পারে সেইটাই তো খাদ্য। আর যেটা ওপর ওপর, সেটা তো ঠিক খাদ্য নয়, সেটা হয়তো কখনো আমরা স্পর্শ করে দেখি। যেটা খাদ্য সেটা তো আমাদের শরীরে যায়, আমাদের মস্তিস্কে যায়, আমাদের অনুভবে যায় এবং আমাদের সমস্ত কিছুর মধ্যে যায়।
-20211115183737.jpg)
সাহিত্যের সেই রকম বিকল্প নেই। যে যতই বলুক, আকাশ সংস্কৃতি ধ্বংস করতে পারে ওই জিনিসটা, যেটা সাহিত্য নয়, কিন্তু সাহিত্যের নামে চলে। সেটা তাকে ধ্বংস করতে পারে, তাকে এফেক্ট করতে পারে। একজন বলতে পারে আমি ও রকম গল্পের উপন্যাস না পড়ে বরং আমি টেলিভিশন দেখে নেব। কিন্তু টেলিভিশনে কখনোই সাহিত্যকে রূপায়িত করা যায় না। আকাশ সংস্কৃতির সাধ্যই নেই। এইটাই তার দুর্বলতা, এইটাই তার অহংকার। এটা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এবং যারা সাহিত্য পড়েন, তাদেরও আমি এই কথাটাই বলতে চাই।
এরা আমাকে বলছে যে আপনি কেমন করে লেখক হয়ে উঠলেন। আর এদিকে আমার সমস্যা, যেটা আমি নিজেই কি কনভিনসড, আমি কী লিখি ? আমি কি সত্যিই দাবি করতে পারি যে আমি একজন লেখক? তা নাহলে আমি কী রকম করে বেড়ে উঠেছি, এর কিছুই তো বলা যাবে না। শুধু এইটুকু বলা যায় যে কৃতকর্মের সুফল এবং কৃতকর্মেরও কুফল মানুষের ভোগ করতে হবে। আমি সাহিত্যের কাগজে লিখেছি, সেটা যদি কুকর্ম হয়, তাহলে আমাকে কুকর্মের ফল ভোগ করতে হবে। আর যদি তা সুকর্ম হয়, তা-ও অল্প-বিস্তর আমার কিছু হবেই। কাজ কিছুটা করেছি, তবে আমার মনে পড়ে না যে কোন একদিন স্থির করলাম যে লেখক হয়ে উঠতে হবে এবং তারপর একটা প্রক্রিয়া অনুসরণ করলাম। এ রকম ঘটনা আমার ঘটেনি। আমি জানি না যারা লেখক তাদের ঘটেছে কি না। রবীন্দ্রনাথ অনেক জটিল প্রশ্নের জবাব দিতে পেরেছেন কিন্তু আমার মনে হয় না যে রবীন্দ্রনাথ এই প্রশ্নটির জবাব দিতে পারতেন যে তিনি কবে কবি হয়ে উঠলেন।
আমরা তো দেখি উনি বোধ হয় জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই এমন কতগুলো জিনিস তাঁকে নাড়া দিচ্ছে, যেটা সচরাচর সাধারণ মানুষকে নাড়া দেয় না। ‘জল পড়ে, পাতা নড়ে’- এর মধ্যে দুলিয়ে দেবার কী আছে! এইটুকু পড়লেই সমস্ত হৃদয় আন্দোলিত হতে থাকে। যারা আন্দোলিত হতে থাকে, তারাই ভবিষ্যৎ কবি হতে পারে। কিছু আলাদা দিয়ে সে বড় হচ্ছে। হতে পারে সেটা। তা ওভাবেই হয়তো খুঁজতে হতে পারে বা অন্যেরা খুঁজে দেখতে পারে যে, আমি কী করে লেখক হলাম এবং অন্যরা যদি মানেন আমি লেখক, তবে অন্যদের খুঁজে দেখতে হবে, এ লোকটা কী করে লেখক হয়েছে। খুব অনুসন্ধানের বিষয় আরকি। আমাকে যদি বলা হয় তাহলে আমি বলব, আমি জন্মেছিলাম, ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম, কিছুদিন ছিলাম, জ্ঞান-ট্যান ছিল না, কী হয়েছিল, না হয়েছিল জানি না। তারপরে একটু একটু জ্ঞান হলো। জ্ঞান হওয়ার পরে আমি কী কী করেছি, আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কী ছিল, আমি একেবারে বলা যায় যে আজকে যেখানে আমাদের সমাজবাস্তবতা, আমাদের জীবনযাপনের ছোঁয়া, আমাদের দারিদ্র্য, সেখানে আমি প্রায় প্রক্ষিপ্ত, এ কথাটা আমাকে স্বীকার করতেই হবে।
আমি যে সমাজব্যবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছিলাম তার কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই। সমাজের যে সমস্ত নর্মস তৈরি হতে পারে, চিন্তা তৈরি হতে পারে, সংস্কার তৈরি হতে পারে সেগুলোর অধিকাংশই এখন বিদায় নিয়েছে। এবং বিদায় নিয়েছে আজকের সমাজের দিকে তাকিয়ে বলা যায়। কিন্তু আমরা যারা বেঁচে আছি, তাদের তো বিদায় দেবার কথা নয়। কাজেই আমাকে আমার জীবনের, যেভাবে জীবনটাকে আমি ভিতর দিয়ে এলাম আরকি, তা থেকে এইটুকু বলা যায়, কী করে আমি লেখক হয়ে উঠলাম। প্রথমে বলা যায় নিশ্চয়, যে পরিবেশের মধ্যে আমার জন্ম হয়েছে, তাতে করে আমার খুব...আজকে যেটাকে নাগরিক সাহিত্য বলা হয়, তা আমার হাত দিয়ে বেরোনোর কথা নয়। আমি সে জন্য, সে কাজের দিকে খুব একটা যাই-ও নি। হয়তো সেই জন্যই, আমার কাজটুকু করার জন্য বাংলাদেশের যেকোনো একটা অঞ্চলই যথেষ্ট। আমার কাছে মনে হয়নি যে, আমি যদি ঢাকার মতো নগরজীবনে যাই, তাহলে আমার খুব সুবিধে হয়, তাহলে আমি নিজেকে নিজে বুঝতে পারি যে আমি কী কাজটা করতে চাই। তাই, সেটার জন্য বেছে নিয়েছি, তখন আমার কাজের ক্ষেত্রটাও কিন্তু ঠিক করতে পেরেছিলাম।
পেছনের দিকে, যত দূর পেছনের দিকে সম্ভব তাকাই, তাতে একটা কথা মনে হয় সাধারণভাবে, এটা আমার বলা উচিত হচ্ছে কি না জানি না। সব লেখকের এরকমভাবে হন কি না, সেটাও আমি জানি না, যারা বড় মাপের লেখক। সে জন্য আমি কেন জানি না, মনে করেছিলাম, কী করে জিনিসটা বোঝাই। মানুষ নানান রকম রসের জন্য নানান রকম খাদ্য খেয়ে খেয়ে দেখে, ভালো লাগে। আমারও এ রকম কিছু একটা খাদ্য নিজের জন্য বাছাই করা হয়েছিল। স্বাভাবিক প্রবণতা থাকতে পারে, সেটাকে জীবনের রস বললে কি ঠিক হবে? জীবন তো ঠিক খাদ্য নয়। আবার একদিক থেকে ভোগ করাও বটে। জীবন একদিক থেকে ভোগ করাও বটে। আমার কেন জানি মনে হয়েছে, মানুষের জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মানুষের জীবনযাপন এবং জীবনের মধ্যে যে গভীর স্বাদ আছে, যে গভীর বৈচিত্র্য আছে সেটাতে সম্পূর্ণভাবে লিপ্ত হয়ে পড়া। এই লিপ্ততা সামলেই যদি আমার জীবনের কাজটাকে যদি যুক্ত করতে পারি, তাহলে আমার মতে, সেইটা লেখকের কাজ করা হতে পারে।
আমি বোঝাতে পারব কি না জানি না, আমি চেষ্টা করব বোঝাতে। জীবনের স্বাদের তো কোন মানে সেই, এটা একটা স্রেফ উপমা মাত্র। অমি কালকেও এক জায়গায় বলছিলাম যে, মানুষ সমাজে বাঁচে খুব সত্যি কথা, রাষ্ট্রে বাঁচে খুব সত্যি কথা, পৃথিবীর একজন নাগরিক খুব সত্যি কথা, গোটা পৃথিবী এসে আছড়ে পড়ে। তার সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্প-সংগীত আছড়ে পড়ে আপনার ওপর। আমাকে আকর্ষণ-বিকর্ষণ অনেক কিছু করে। আমাকে তৈরি করে, বদলায়। কিন্তু বাঁচি, একেবারে আমি আমার নিজস্ব চেতনাটুকু দিয়ে। এই জায়গায় মানুষ এত প্রাতিস্বিক এবং এত একা, নিঃসঙ্গ অর্থে একা বলছি না। ওটা অতিক্রম করাই মুশকিল। এই যে মানুষ একা বেঁচে থাকে, এটা প্রায় আমার কাছে দার্শনিক মনে হয়, যে যা কিছু আমরা শেষ পর্যন্ত চাই তা রেফার করে ওই ব্যক্তি মানুষটিকে। কাজেই যদি চূড়ান্ত মূল্য দিতে হয় তাহলে সেই ব্যক্তিকেই দিতে হবে।
...শেষ কথাটা বোধ হয় ব্যক্তি। আমি মনে করি না যে শেষ কথাটা ব্যক্তি বললে, আজকের পুঁজিবাদী সমাজে যে ব্যক্তির ধারণাটা, আমি সেইটা বোধ করছি, আমি তা-ও বলছি না। আর ব্যক্তিগত বললে, আমাদের তথাকথিত মার্কসিস্টরা খুবই রাগ করেন। তারা যৌথ জীবনের কথা বলেন। কিন্তু আমার মনে হয় ওভাবে মার্কসকে বা মার্কসবাদী তত্ত্বকে বা মার্কসবাদী সমাজকে ঠিকমতো বোঝা হয় না। ...আর, সেই মানুষজনের মধ্যে একেকটা ব্যক্তিই চূড়ান্তভাবে বিকশিত হওয়ার সমস্ত পথ খুঁজে পাবে। যদি কিছু বলতেই হয়, তাহলে এইখানেই কথাটা শেষ হয়। তাই বলে মার্কস কখনোই বলতেন না যে, জীবনের শেষ দুঃখ কী? ফ্রিডম ফর অল, না, ফ্রিডম ফর ইন্ডিভিজুয়াল? আমি মনে করি যে, আমরা স্বীকার করি বা না-করি, পৌঁছুই গিয়ে কিন্তু ব্যক্তি পর্যন্ত। সাহিত্যিক সেই জায়গাতে কাজ করেন আর ঠিক সেই অর্থে আরেকটা ব্যক্তির কাছে পৌঁছান। এটা কক্ষনো সকলের কাছে পাবলিক করে দেখানোর কোনো ব্যাপার না। সে জন্য সত্যজিৎ রায় যতই ‘পথের পাঁচালী’ করুন না কেন, বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাস একদম আলাদা হয়ে থাকবে।
তা আমার সেইটাই মনে হয়, আমার ছোটবেলায় যখন পশ্চিম বাংলার অদূর একটা পাড়া-গাঁ, সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা সমাজ পরিপ্রেক্ষিত। সাধারণভাবে বললে কম বলা হবে যে এটা একটা কৃষিজীবী সমাজ। অনেকে মনে করতে পারেন, কৃষিসমাজ তো সব জায়গায়। তা কিন্তু নয়। এটা একটা বিশেষভাবে কৃষিজীবী, যেটাকে সম্পূর্ণভাবে একটা বা দুটো ফসলকেন্দ্রিক কৃষিসমাজ বলতে হয়। আমি পরবর্তীকালে যখন খুলনায় ছিলাম, অনেকে বলত যে, আমি খুলনায় এসে একজনও কৃষক দেখতে পাই না। সবাই দেখি যে অনেক দক্ষিণে তাদের জমিজমা সব আছে। লোকের বাড়িতে বাগান-টাগান আছে। একদম ভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা আরকি। কিন্তু রাঢ়ে আমি যে এলাকায় জন্মেছিলাম এইটাকে সত্যিকারের অর্থে একটা কৃষিসমাজ বলতে হয়, কিন্তু কোনো সামন্ত নাই। বড় বিশাল-বিশাল যে জমিদার শ্রেণি আছে, তা নেই। ওই যে একটু আগে যে প্রবন্ধখানি পড়েছিল তাতে একটু ধারণা পাওয়া গেছে যে কেমন সমাজের মধ্যে আমি ছিলাম। খুব সীমিত জিনিস তৈরি হত, খুব বেশি হতো যেমন অল্প আউশ হতো আর আমন। জীবন-জীবিকার সমস্ত কিছু তখন এই আমন ফসলের ওপরে, আকাশের বৃষ্টির ওপর। কাজেই মানুষের সমস্ত অস্তিত্ব অধিকার করে রয়েছে এই ‘কৃষি’। এরই মধ্যে জীবনের সার্থকতা।
আচ্ছা আমি ওখানে বড় হয়েছি, তাহলে আমি ওটাকেই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে না করে কি পারি? আজকে আমি সচেতন মানুষ হিসেবে দেখতে পাচ্ছি কত দ্রুত এখন, এমনকি সেই রাঢ়েও, আজ সে কৃষিসমাজ নেই। রাঢ়ের মানুষও সবাই আর এখন কৃষক নয়। কত রকমের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি এসেছে, সম্পূর্ণ বদলে গেছে। কিন্তু একধরনের কৃষিকেন্দ্রিক সমাজ আমাকে একেবার পুরো অধিকার করে আছে, যেটা আমার সকলের সামনে স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই, যে আমি এখনো আধুনিক মানুষ হতে পারিনি। কি জানি, ভেতরে পচন ধরবে? কিন্তু আমি বাস্তবকে অস্বীকার করছি না। আমি চেষ্টা করছি যাতে বাস্তবকে ক্রমাগত নিজস্ব মৌলিকের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে ফেলা যায় আরকি। এটা করতেই হবে। সেটা আমি চেষ্টা করব।
সেই জন্যই হয়তো আমার সমস্ত লেখাতে, মোটামুটিভাবে ১৯৬০-এর পরে আরকি, ১৯৬০-এর পর থেকে আমার সমস্ত লেখাতে ‘সময়’ আর ‘জীবন’, এ দুটো জিনিসের আমরা খুব মোটা একটা শব্দ ব্যবহার করি ‘অবজেক্টিভ’ নিয়ে লিখতাম, এটা খুব ধরা পড়েছে। খুব বেশি করে, আমি যখন যেখানে ছিলাম, সেইখানেই। আমার প্রথম বইতে রাঢ়ের যে জীবনটা, আমার বাল্যকালের ‘শকুন’ গল্পটাতে। তা আমি এরকমভাবে ভীষণভাবে সময়-নির্ভর লেখক, বা সময়নির্ভর আমার লেখা হয়েছে। আমার বইগুলো সে জন্য খুবই আলাদ-আলাদা হয়েছে। সেই জন্য দেখা যায় যে আমার বাল্য-কৈশোর এবং প্রাক-যৌবনের স্মৃতিটা কীভাবে ধরা পড়েছে, এক্কেবারেই রাঢ়ের সমাজব্যবস্থা, রাঢ়ের মানুষ, সেখানেও আমার স্থির এবং ধ্রুব লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের জীবন, মানুষের জীবনযাপনের রস, অত্যন্ত ঘন-গভীর-জটিল সেই রস।
সেইটাই আমার মনের মধ্যে কাজ করেছিল। একটু যৌবনে পৌঁছে যখন আমাদের দেশ ছাড়তে হলো, আমি থাকলাম এমন একটা জায়গায় যেন আমি আমার প্যারাডাইস থেকে নির্বাসিত হয়েছি। বলতে গেলে ৪৭-এর পর থেকে এই নির্বাসনটা শুরু হয়েছিল। এটা আজকের ছেলেরা বুঝবে না, কারণ তাদের মনের জগতে এই জিনিসটা নেই। আমার আজকে মনে হয় আমি কী নিয়ে লিখব? আমি যা নিয়ে লিখব তাতে কি কারও আগ্রহ তৈরি হবে? এটা আমাদের জন্য সাহিত্যে বড় প্রশ্ন।
এই যে সাম্প্রদায়িকতার ব্যপারটা একটু আগে পড়া হলো, এখানে যারা শুনল, তারা কি এ ব্যাপারটাকে জেনুইন, সত্যকারের একটা জিনিস বলে মনে করল? কারণ, বাস্তবের, সমাজের কিন্তু এই চেহারাটা নেই। আমি একটা অন্য রকমের ব্যপার, একটা নেশা, ডালে-চালে মেশা একটা জীবনের কথা বলতে চেয়েছি। ...সাম্প্রদায়িকতা ঘটল, ঘটিয়ে তোলা হলো বলে। আমরা যেমন বাজার দখল করব, কি ব্রিজ দখল করব, কি রাষ্ট্র দখল করব বলে যে আমরা একটা প্রোগ্রাম নিই, ঠিক তেমনি করে, ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটিয়ে তোলা হলো। এটাকে ঠিক সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে যুক্ত করা ঠিক হবে না। কারণ, সেই জন্যই আমি ভাবি, আমার এই যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আসছি, আমার প্রথম জীবনের সমস্ত স্মৃতি এবং আমার মনে হয়, যদি হিসেব করা যায় তাহলে উৎপাদন ব্যবস্থা, বণ্টন ব্যবস্থা, পারিবারিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক, সবই বোধ হয় খুঁজলে পাওয়া যাবে। আর, ওগুলো বর্ণনার জন্যই আমি কিন্তু লিখতে চাই নাই।
জীবনের যে মজাটা আরকি, এই মজাটা যেমন করেই হোক বার করতে হবে। মজা বার করার একটা ব্যাপার আছে। আমাদের দেশে ইয়ে ছিল, কী বলে ...কতবেল। কচি গাছে থাকলেও আর আমাদের ধৈর্য ধরত না। কচি কচি কতবেল, কোনো লাভ নাই, সেইটাকে পেড়ে নিয়ে এসে এইবারে সেটাকে মজানো হবে। কী রকম করে? তাতে একটা ফুটো করে, তার ভেতর দিয়ে নানান-রকমের মশলা-টশলা ঢুকিয়ে দিয়ে, ওটা একটা, মেয়েরা যেমন উল বোনে কথা বলতে বলতে, ঠিক তেমনিভাবে হাতে আছে, মজানো হচ্ছে আরকি। ঘুটে-ঘুটে, ঘুটে-ঘুটে শেষ পর্যন্ত ওটাকে মজিয়ে ফেলে ভাঙা হলো, দেখা গেল যে কিচ্ছু হয়নি। ফাঙ্গাস-টাঙ্গাস পড়ে একদম নষ্ট হয়ে গেছে, ফেলে দিতে হলো। তা আমার মনে হয় জীবনটাকে এ রকম একটা মজানোর ব্যাপার আছে। সেই লক্ষটায় আমি সেখানটায়। কষ্ট-দুঃখ-দারিদ্র্য আছে, কিন্তু আমার কেবলই মনে হয় যে, বিপ্লব দ্বারা, নতুন রাষ্ট্রের দ্বারা, নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এগুলো যাবে। কিন্তু জীবনের মজা কিন্তু এগুলোর মধ্যেই। সবচাইতে দরিদ্র, সবচাইতে নির্যাতিতর মানুষও ফিকফিক করে যে কেন হাসে এটা আমি দেখেছি। এটা আশ্চর্য লাগে আরকি! মানুষের মৃত্যুর মধ্যেও মজা। আমাদের গ্রামে এক বুড়ি ছিল। সে বুড়ি, যেকোনো কারণেই হোক নামাজ-রোজা করত না। তো সে বুড়ি মারা যাচ্ছে, আর বাঁচবে না। তখন তার পাশে একজন বলছে যে ‘আল্লাহ বলো’। তখন বুড়ি বলছে যে ‘বেজার লাগে’। মরবার সময় একজন বুড়িকে বলছে আল্লাহ বলো, আর সে বুড়ি বলছে বেজার লাগছে। আমার কাছে এটা এমন অদ্ভুত মনে হয়েছে। আচ্ছা এই বুড়ির কি মৃত্যু ভয় ছিল না! আচ্ছা, বুড়ি কি এই পরিমাণে স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ যে সে আল্লাহর নামও নেবে না, কারণ তার বিরক্ত লাগছে ও কথা বলতে? মরবার আগে আল্লাহর নাম বলতে বিরক্ত লাগছে!
মানুষের সমাজবদ্ধ জীবনের দিকে তাকালে কত অজস্র ব্যাপার পাওয়া যায়। এটাকে প্রকাশ করা মুশকিল, এটাকে এক অর্থে ‘মজারু’ শব্দটা দিয়ে বলা চলে। আমি আগাগোড়া এই মজারুর ব্যাপারটা, আর বাকি যেটা শ্রেণি নির্যাতন, দুঃখ, দারিদ্র্য, ভীষণ অমানবিকতা এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করতেই হবে, সে ইঙ্গিত বারবার আমি করি। কিন্তু এগুলোর ভেতরেও কিন্তু মানুষের জীবনযাপনের দৈনন্দিন এবং ব্যক্তিগত যে ভয়ানক মজা আছে, সেটা যদি না পাওয়া যায়, তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা আমাদের জীবনের অনেকটা লুস করছি। এখন একজন মানুষ সকালবেলা উঠে তার একেবারে প্রথম কাজ হচ্ছে দাড়িটা কাটা, দাড়িটা কেটে একটু লোশন মেখে, সামান্য একটু কিছু খেয়ে, গাড়ি চালিয়ে (এটা আমাদের উপাচার্য সাহেবের জীবনের ধরনটা আমি মনে করি) একবার অফিসে গিয়ে বসলেন। গত দিনটা কেমন? এই আজকের দিনটা যেমন, তেমনি। আগামী দিনটা কেমন? আজকের দিনটা যেমন, তেমনি আরকি। আর কোনো কন্ট্যাক্ট নেই। কত সুন্দর জীবন। কিন্তু আমার মনে হয় যে, মজা কই? মজা খুঁজলে তো ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়তে হবে। ভীষণভাবে ঢুকে পড়তে হবে, সে তাড়া বোধ করতে হবে।
হয়তো যখন সাহিত্য পড়েন, তখন মনে হয় যে জীবনের ওই মজাটা পুষিয়ে দিতে পারবে সাহিত্য। যা-ই হোক, আমি আর কত কথা বলব। কথা বললে কিন্তু কথা চলতেই থাকবে। সেটার তো কোনো দরকার নেই। অত কথা বলবার দরকার নেই। কারণ, আমার গুছিয়ে বলবার কিছুই নেই। এ রকম এলামেলো কথাই আমি বলেই যাব। কাজেই আমি থেমেই যাই।
আজকে আমি খুব উত্তেজিত বোধ করছি, তার কারণ বন্ধুর সঙ্গে এত দিন পরে দেখা। এটা উনিও কিছু বললেন না তো, আমিও আর কিছু বলব না। বলার কিছু নেই। আমি ঢাকায় আসি, কিছুতেই যোগাযোগ হয় না। যোগাযোগ করতে পারি না। এটা, ওই, জীবনের বদমায়েশি ছাড়া আর কিছু নয়। আমরাও ওই বদমায়েশিতে চলে গিয়েছি। দেখা হয় না, যোগাযোগ হয় না। কিছুদিন আগে আমরা আকিমুনের একটা অসাধারণ উপন্যাসের পাঠচক্র করলাম, আকিমুনের জন্য। সেটা বোধ হয় ছেলেরা জানে। তখন আকিমুনের সঙ্গে আলাপ হলো। আকিমুন উপলক্ষ্য তৈরি করে ফেলল যে, কোনো কথা নেই আপনি ঢাকায় এলেই আপনাকে সোজা গ্রেপ্তার করা হবে আরকি। তো ঠিক তাই করেছে এবং এটা সম্ভব হয়েছে।
আজকাল বহু জিনিস সম্ভব করে তুলতে পারা যায় না। এটা সম্ভব হয়েছে। আবার আপনাদের উপাচার্যের সঙ্গে দেখা হলো এবং আমার এটা একটা বড় প্রাপ্তি যে আপনারা সবাই বসে আছেন এবং আমি কথা বলছি। কিন্তু যদি কেউ না-ও থাকত তাহলে যথেষ্টই ছিল... আমার বন্ধু আরেফিন, উনি এসে হাজির হলেন। সব মিলিয়ে আমার আজকে খু-উ-উ-ব ভালো লাগছে আরকি। খুব। এবং গল্প-গুজব করতেই আমার ইচ্ছে করছে। নিজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতেও খুব একটা পছন্দ করি না। আর তারপর কিছু বলারও নেই।
মোটামুটি লেখক বলে যাকে স্বীকার করা হয়, তাহলে তার উৎসটা কোথায়। এখন এইটার প্রতি আমি কেন আকৃষ্ট হলাম, আমার গ্রামের আরেকটা ছেলে সে চাষবাস করেই গেল, কিম্বা লেখাপড়া শিখে অন্য কিছু করল। এইটা যে কেন হলো, এইটা বলা খুব কঠিন। অর্থাৎ সেখানে বোধ হয় কিছু আলাদা পোকামাকড় মাথায় থাকে। কিছু লোকের মাথায় পোকা নড়ে, তারা কবিতা লেখে, গল্প লেখে। বেশ কিছুদিন পরে হয়তো পোকামাকড়কে মেরেও ফেলে আবার এদিক-সেদিক চলেও যায়। আর বাকি লোকেরা স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করেন। কাজেই আমি কী করে লেখক হয়ে উঠলাম বলতে গেলে ওটাই বলতে হবে যে, কিছু পোকামাকড় নিশ্চয়ই মাথায় কাজ করেছে আরকি। যার ফলে ওদিকে নজরটা গেল এবং ওদিকে নজর গিয়ে মনে হলো যে সাহিত্যই যথেষ্ট মানুষের বেঁচে থাকার জন্য। সাহিত্য পড়া কিন্তু একদিক দিয়ে বলা যায় মানুষ অকর্মণ্য হয়ে যায়, নিজের উদ্যম নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য যতই পড়িবে ততই শিখিবে না বলে, যতই পড়িবে ততই মূর্খ হইবে, এটাও কিন্তু বলা যায় আরকি। মানে নিজে সম্পূর্ণ অপারগ হয়ে গেলে তখন সাহিত্য-শিল্প অন্যান্য বই ইত্যাদি পড়া দরকার। নইলে খুব বেশি দরকার হবে না। নিজের ইয়ে দিয়েই চালানো যায় আরকি।
তা আমরা পড়ি, প্রচুর পড়াশোনা করে নিজেদের এক অর্থে খুবই সমৃদ্ধ করে তুলি। তা আমার মনে হলো যে সাহিত্য যথেষ্ট, আর কোনো সঙ্গী, সাথি লাগবে না। এখন আমার তো পূর্ণ অবসর, চারিপাশ থেকে লেখ-লেখ-লেখ করে, আর লিখতে আমার এত বেজার লাগে, মানে একদম ভালো লাগে না। আর কেবলই মনে হয় যে এত লেখা মানুষ লিখে গেছে, এত সুন্দর, আমার এই নন সেন্সগুলো লেখার কি প্রয়োজন আছে! কোনো দরকার তো নেই। আমাদের এই বাংলাদেশেরই, বাংলা সাহিত্যেই যেসব কাজ হয়ে গেছে, তাতে সহসা লেখক হতে ইচ্ছে হওয়াটা উচিত হয়নি। কিন্তু পোকামাকড় কাজ করে তো কিছু করার নেই। তারা ঠেলাঠেলি করে এবং সেই জন্য কোনো রকমে শেষ পর্যন্ত লেখকই হয়ে উঠতে হলো। আরেকজনের হলো না কেন? হয় তো, ওই মজাটার প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ হলো না। এইটা যে কেন হয়, সেটা আমাদের সমাজবিজ্ঞানী যদি বলতে পারেন, এইটা কেন হয়? কিছু লোকের পোকা কাজ করে, কিছু লোকের কেন করে না? একই অবস্থার মধ্যে কেউ লেখক হয়ে যায়, কেউ আবার লেখক হয় না। কেউ কবি হয়ে যায়, কেউ কবি হয় না। কেউ ব্যবসা চালিয়ে যায়। কেন হয় এ রকম?... আমার কাছে মনে হয় মানুষ কবি, মানুষ ভাবুক, মানুষ অনুগতশীল, মানুষ হৃদয়বান, মানুষ নিষ্ঠুর। সমস্ত জিনিস একসঙ্গে করে এই মানবিক অস্তিত্বটাকে ব্যাখ্যা করা, তার মধ্যে ঢোকা—এইটাই তো সাহিত্যের কাজ।


-20211115183851.jpg)




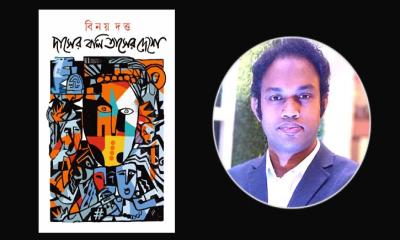






























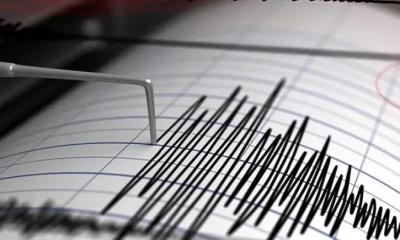









-20231109105053-20250402121817.jpg)

-20250329161133.jpeg)

