‘সাহিত্যিকের হৃদয় ছিল তাঁর, দার্শনিকের মস্তিষ্ক ছিল, আর ছিল বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি।’ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সম্পর্কে বলেছিলেন ড. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তবে যে কথাটি অনুক্ত থেকে গেছে, যা রামেন্দ্রসুন্দরের সব কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রক, তা হচ্ছে—স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রেম। তাঁর যেকোনো পদক্ষেপ, যেকোনো উদ্যোগের পেছনে মূল ভূমিকা পালন করেছে তাঁর সুগভীর দেশপ্রেম। রামেন্দ্রসুন্দরের শিক্ষাচেতনা ও বিজ্ঞানচেতনার পশ্চাৎভূমিও তৈরি করেছিল দেশপ্রেম। সংগত কারণেই তাঁর সমসাময়িক এবং আগে-পরের যেকোনো শিক্ষাবিদের শিক্ষাচিন্তার সঙ্গে তাঁর শিক্ষাচিন্তার যে ব্যবধান তা, তাঁদের দেশপ্রেমের মাত্রাভেদ ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে তাঁর বিজ্ঞানচিন্তা ছিল একেবারেই ভিন্ন। বলা চলে বিজ্ঞানচিন্তার এই ঘরানার পথিকৃৎ ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। প্রথাগত অর্থে তিনি কোনো বিজ্ঞানী ছিলেন না। বিজ্ঞানের কোনো সূত্র আবিষ্কারে মনোনিবেশ করেননি। যেমনটি করেছিলেন আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু, সত্যেন বসু কিংবা মেঘনাদ সাহা। আবার বিজ্ঞানবিষয়ক লেখক বলতে আমরা সচরাচর সে ধরনের লেখক বুঝে থাকি, যারা বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার ব্যাখ্যা করেন, বিজ্ঞানতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন, রামেন্দ্রসুন্দর সে ধরনের লেখক ছিলেন না। তিনি বিজ্ঞানকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছিলেন। ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ’ নামক একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—‘বিজ্ঞান বিজ্ঞান আমরা বিজ্ঞান চর্চ্চা করিব। যেন পদার্থবিদ্যা, আর রসায়নশাস্ত্র আর দেহতত্ত্ব লইয়াই বিজ্ঞান! যেন কলের গাড়ীতে আর টিনের কানিস্তারেই বিজ্ঞান সীমাবদ্ধ! মানবত্ত্ব যেন বিজ্ঞানের পরিধির বাহিরে ইতিহাসালোচনা যেন বিজ্ঞানের সীমার বহির্গত! বিজ্ঞান—বিশেষ জ্ঞান। যাহা কিছু জ্ঞানের বিষয়,তাহা বিজ্ঞানের বিষয় আব্রহ্ম স্তব পর্য্যন্ত।’
এ থেকে বোঝা যায় শিক্ষায় যেমন তিনি সামগ্রিকতাবোধের অধিকারী ছিলেন, বিজ্ঞানেও ঠিক একই মনোভাব পোষণ করতেন। সে কারণে বলা চলে তাঁর বিজ্ঞানচেতনা, তাঁর শিক্ষাচিন্তারই একটি প্রশাখা, কিংবা একটি সম্প্রসারিত রূপ।
২.
শিক্ষাজীবনে অত্যন্ত কৃতী ছাত্র ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। পরবর্তী জীবনে শিক্ষকতাতেও অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর পারিবারিক জীবন থেকে শিক্ষা-সাহিত্য ও স্বদেশপ্রেমের এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার যে প্রেষণা তিনি লাভ করেছিলেন, তা তাঁর কর্মজীবনে উৎসাহ জুগিয়েছে নিরন্তর।
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জন্ম ১৮৬৪ সালের ২০ আগস্ট। পিতা গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী এবং মাতা চন্দ্রকামিনী দেবী। তাঁর জন্মস্থান ‘জেমো’ নামক গ্রামে পৈতৃক বাসভিটায়। তাঁদের পরিবারে শিক্ষা ও সাহিত্যের বাতাবরণ বরাবরই ছিল। তাঁর পিতা গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী ‘বঙ্গবালা’ নামে একটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। এছাড়া ‘দ্রৌপদীনিগ্রহ’ নামে একটি নাটক রচনার কথাও জানা যায়। তবে তাঁর সবচেয়ে বেশি উৎসাহ ছিল সামাজিক ক্রিয়াকর্মে ও দেশের কাজে। রামেন্দ্রসুন্দরের ওপর তাঁর পিতার প্রভাব পড়েছিল প্রচণ্ড। ‘পুণ্ডরীক কূলকীর্ত্তিপঞ্জিকা’ গ্রন্থে পিতার স্বদেশানুরাগ, জ্ঞানস্পৃহা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন—‘স্বদেশের কথা কহিবার সময় তাঁর কণ্ঠস্বরের বিকৃতি ও লোমহর্ষঘটিত। স্বভাবপ্রদত্ত মেঘমন্দ্র স্বরে উদ্দীপনার ভাষায় তাঁহার অষ্টমবর্ষীয় জ্যৈষ্ঠ পুত্রটির মনে স্বদেশভক্তি সঞ্চারিত করিবার জন্য কতই না প্রয়াস পাইতেন। গণিতে, বিজ্ঞানে বিশেষতঃ সিদ্ধান্ত জ্যোতিষে তাঁর স্বাভাবিক অনুরক্তি ছিল। ইংরাজী না জানিয়াও জ্যোতিষশাস্ত্রে গভীর অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যক্রমে সেই অসাধারণ ধীশক্তি যথোচিত ফলোৎপাদনে অবকাশ পায় নাই।’
১৮৮১ সালে কান্দি ইংরেজি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। পরীক্ষায় প্রথম হলেন। সেই সঙ্গে উচ্চশিক্ষার জন্য পেলেন সরকারি বৃত্তি মাসিক পঁচিশ টাকা।
পরবর্তী শিক্ষাক্ষেত্র কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ। ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন। যদিও সরকারি বৃত্তি বহাল রইল মাসিক পঁচিশ টাকা হারে। ১৮৮৬ সালে বিএ পরীক্ষায় বিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করলেন। এবার বৃত্তি পেলেন মাসিক চল্লিশ টাকা। পরের বছর, অর্থাৎ ১৮৮৭ সালে প্রথম স্থান অধিকার করলেন এমএ পরীক্ষাতেও। এমএ পরীক্ষায় তাঁর বিষয় ছিল পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্র। সে সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের শিক্ষক ও পরীক্ষক ছিলেন মি. পেডলার। তিনি রামেন্দ্রসুন্দরের রসায়নের উত্তরপত্র দেখে মন্তব্য করেছিলেন—‘আমি এ যাবৎ যত রসায়নের উত্তরপত্র দেখেছি, তার মধ্যে এটাই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ।’
এই পেডলার সাহেবেরই উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় তিনি ‘প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ’ বৃত্তির জন্য পরীক্ষা দেন। ১৮৮৮ সালে তিনি পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রে ওই বৃত্তি লাভ করেন। মূলত গবেষণাকর্মের জন্য প্রদত্ত ওই বৃত্তির পরিমাণ তৎকালীন আট হাজার টাকা। এরপরে কিছুদিন রামেন্দ্রসুন্দর প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরেটরিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তবে তাঁর কর্মজীবন মূলত শুরু হলো ১৮৯০ সালে। অধ্যাপক নয়, পরীক্ষক হিসেবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের পরীক্ষক নিযুক্ত হলেন তিনি।
যদিও বাংলার বাইরের বিভিন্ন কলেজ ও প্রতিষ্ঠান থেকে রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে লোভনীয় সব চাকরির প্রস্তাব আসছিল, তিনি সেসব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি স্থির করেছিলেন বাংলাই হবে তাঁর কর্মক্ষেত্র। অবশেষে ১৮৯২ সালে তিনি কলকাতা রিপন কলেজে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি এই কলেজের অধ্যক্ষও নিযুক্ত হয়েছিলেন। বিজ্ঞানের এই কৃতি ছাত্রটি শিক্ষক হিসেবেও ছিলেন অসাধারণ। তাঁর পাঠদান পদ্ধতি এতই আকর্ষণীয় ছিল যে, অন্যান্য কলেজের ছাত্ররাও তাঁর লেকচার ক্লাসে ভিড় জমাতেন। প্রত্যক্ষ ছাত্ররা তাঁর পাঠদানের বিবরণ লিখে গেছেন। তাঁদের ভাষ্য থেকে জানা যায় তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি অত্যন্ত বিশিষ্ট ছিল। রসায়নবিদ্যা পড়াতে গিয়ে তিনি সরাসরি বিষয়ের অবতারণা করতেন না। প্রথমে রাসায়নিক পরীক্ষা দেখিয়ে ছাত্রদের কৌতূহল উদ্রিক্ত করতেন। তারপর পরীক্ষিত বিষয়গুলো খুবই সরলভাবে ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতেন। পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে অঙ্কের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গি। কিন্তু তিনি অনেক সময়ই গণিতের সাহায্য ছাড়াই পদার্থবিজ্ঞানের জটিল তত্ত্বসমূহ প্রাঞ্জল ভাষায় ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হতেন। যদিও তখন শিক্ষার মাধ্যম ছিল সম্পূর্ণ ইংরেজি, তবু তিনি যতদূর সম্ভব মাতৃভাষায় অর্থাৎ বাংলায় পাঠদানের পক্ষপাতী ছিলেন। নিজেই বলতেন—‘অধ্যাপকের আসনে বসিয়া বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যাপনা যদি আপনারা অপরাধ বলিয়া গণ্য করেন, তাহা হইলে আমার মত অপরাধী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সঙ্ঘ মধ্যে খুঁজিয়া মিলিবে না।’
তিনি পাঠদানের সময় ছাত্রদের কল্পনাশক্তি যতখানি সম্ভব উদ্দীপিত করার চেষ্টা করতেন। ব্যবহার করতেন নিজেদের চারপাশের উপমা। যেমন সৌরজগতের উৎপত্তি বোঝাতে গিয়ে বলতেন—‘একটি কয়লার পৃথিবী গড়িয়া ছত্রিশ ঘণ্টায় পোড়াইতে পারিলে যে পরিমাণ তাপ জন্মে, সূর্য্যপৃষ্ঠে প্রতি বর্গফুট হইতে প্রতি ঘণ্টায় সেই পরিমাণ তাপ নিয়ত বিকীর্ণ হইয়া যাইতেছে।’ আবার ‘পরমাণু’ সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে বলতেন—‘এক ফোঁটা জলকে যদি কোনরূপে বড় করিয়া আমাদের পৃথিবীর সমান করিতে পারি, যে পৃথিবীর পরিধি পঁচিশ হাজার মাইল, সেই পৃথিবীর সমান করিতে পারি, তবে সেই জলের ফোঁটার এক একটি অণু এক একটা বেলের মত বড় দেখাইবে।’
অর্থাৎ বিজ্ঞান শিক্ষাকে বিভিন্ন উপাত্ত, অঙ্কের গোলকধাঁধা থেকে বের করে ছাত্রদের সামনে মনোগ্রাহীভাবে উপস্থিত করে, তাদের মন থেকে বিজ্ঞান শিক্ষার ভীতি দূর করার জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না।
৩.
রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞানচেতনাকে যদি আমরা সূত্রাকারে উপস্থিত করতে চাই, তাহলে তাঁর বিজ্ঞানমানসকে প্রথমে বিবেচনায় আনতে হবে। বুঝতে হবে বিজ্ঞান বলতে তিনি কী বুঝতেন, বিজ্ঞান কাদের জন্য, বিজ্ঞানের কোন রূপটির তিনি পূজারি ছিলেন এসব কিছু বিবেচনায় নিয়ে আমরা রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞানভাবনাকে সূত্রায়িত করার চেষ্টা করব।
ক. বিজ্ঞান শুধু বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানের শিক্ষক-ছাত্র কিংবা বিজ্ঞানসেবীর একচেটিয়া সম্পদ—এই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করেন রামেন্দ্রসুন্দর। বিজ্ঞান নিয়ে যা কিছু ভেবেছেন তিনি, যা কিছু লিখেছেন তিনি, সবকিছুই সকলের জন্য। কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য নয়। ১৩২০ সালে কলকাতার টাউন হলে একটি বক্তৃতায় তিনি বলেন—‘বিজ্ঞানমন্দিরে যাহাঁরা সাধক, তাঁহারা যে ভাষা ব্যবহার করেন, তাহা অন্যের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। সাধনামন্দিরের বহির্দ্দেশে আসিয়া প্রাকৃতজনের নিকট তাহাদের বোধ্য ভাষার আত্মপ্রকাশে তাঁহারা স্বভাবতঃ সঙ্কোচবোধ করেন; অথচ তাঁহাদের সাধনালব্ধ ফলের আস্বাদনের প্রত্যাশায় অসংখ্য নরনারী মন্দিরের বাহিরে উর্দ্ধমুখে ও শুষ্কহৃদয়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, তাহা তাঁহারা দেখিতেছেন। তাহাদিগকে বঞ্চিত করিলে চলিবে না।’
এই ‘ঊর্ধ্বমুখী ও ‘শুষ্কহৃদয়ে অপেক্ষমাণ’ জনগোষ্ঠীর কথা চিন্তা করেই কলম ধরেছিলেন তিনি। বুঝেছিলেন, মাতৃভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক লেখা সহজ ও প্রাঞ্জলভাবে উপস্থিত না করলে এই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত করার আর কোনো পথ নাই। উল্লেখ্য, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনার গোড়াপত্তন করেছিলেন ইউরোপীয় মিশনারিরা। কিন্তু তাঁদের ভাষা ছিল কৃত্রিম ও জটিল। ভাষার কৃত্রিমতা দূর করে এদেশীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে সর্বপ্রথম জনপ্রিয় করে তোলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। এছাড়া উল্লেখ করা যায় রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম। রামেন্দ্রসুন্দরের পার্থক্য এখানেই যে তিনি নিজে যেমন বাংলায় বিজ্ঞানবিষয়ক লেখা লিখেছেন, তেমনি অন্যদেরকেও নিরন্তর প্ররোচিত করেছেন। তাঁর প্ররোচনায় অনেকেই উৎসাহিত হয়েছিলেন বাংলায় বিজ্ঞানবিষয়ক রচনায় প্রবৃত্ত হতে। তবে অন্যরা সচরাচর দুরূহ ও জটিল বিষয়কে সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলেন। দুরূহ ও জটিল বিষয়কে প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার যে বিপুল ক্ষমতা আছে, তা রামেন্দ্রসুন্দরই প্রথম প্রমাণ করেছেন।
খ. যদিও বিজ্ঞান চরিত্রগতভাবেই মৌলবাদের বিরোধী, তবু খোদ বিজ্ঞান নিয়েই কেউ কেউ মৌলবাদী হয়ে পড়েন। তাঁদের ধারণা, বিজ্ঞানে যে প্রশ্নের উত্তর নেই, তা অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। রামেন্দ্রসুন্দর এই প্রবণতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি এই ধরনের মানসিকতাকে তীব্র আক্রমণ করেছেন ‘বিজ্ঞানের পুতুলপূজা’ ও ‘মায়াপুরী’ প্রবন্ধে। বিজ্ঞানের সাধক হিসেবে তিনি জানতেন বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতাগুলোকে। সাপেক্ষ বা খণ্ডিত সত্য নয়, নিরপেক্ষ ও অখণ্ড সত্যকেই চিরদিন খুঁজে বেড়িয়েছেন তিনি। এই অখণ্ড সত্যের সন্ধান শুধু বিজ্ঞানের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না, তাও তিনি বুঝেছিলেন। তই তিনি বিজ্ঞানের পাশাপাশি পথ খুঁজেছেন দর্শনেও। অর্থাৎ রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞানচিন্তা শুধু অবিমিশ্র বিজ্ঞান নয়, তাতে মিশেছিল দার্শনিকের জিজ্ঞাসা ও প্রজ্ঞা।
রামেন্দ্রসুন্দর সত্যের শ্রেণিবিভাগ করে নিয়েছিলেন। কতকগুলো সত্য আমরা মানতে বাধ্য। এরা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। আর কতকগুলো সত্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের ওপর নির্ভর করে আমরা মেনে থাকি। এরা সাপেক্ষ সত্য বা আপেক্ষিক সত্য বা ব্যবহারিক সত্য। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন এইভাবে যে, প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা এক হিসেবে সত্য। তাই বলে প্রকৃতি যে সব সময় ও চিরকাল একই নিয়মে চলবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমাদের ভুয়োদর্শন অনুযায়ী সত্যের চেহারাও পরিবর্তিত হয়। এই জগতে স্বতঃসিদ্ধ সত্য হচ্ছে ‘আমি আছি।’ আমার অস্তিত্ব বজায় রাখতে গেলে আরও কয়েকটি সত্যের ওপর নির্ভর করতে হয়, তারা হলো ব্যবহারিক বা আপেক্ষিক সত্য। আবার ব্যবহারিক সত্যের মধ্যে প্রধান হচ্ছে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা। তিনি সত্যিকারের বিজ্ঞানসাধক ছিলেন বলেই বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিতে তাঁর কোনো দ্বিধা ছিল না। তিনি লিখেছেন—‘জীবন রহিত জড় দ্রব্যে কখন কিরূপে জীবনের আবির্ভাব হইল, জীবের মধ্যে কিরূপে সুখ-দুঃখের বেদনাবোধ আবির্ভূত হইল, কিরূপে তাহার মধ্যে চেতনার সঞ্চার হইল, চেতনা ও জীব কিরূপে আবার বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচারশক্তি লাভ করিল, এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। ডারুইনবাদী দেখাইয়াছেন, জীবের জীবনরক্ষার্থে এই সকল ব্যাপারের আবশ্যকতা আছে; অতএব জীব যখন জীবন ধারণ করে, তখন তাহাতে এই এই সকল ব্যাপার ঘটিলে ভাল হয় ও ফলেও তাহা ঘটিয়াছে। কিন্তু জগদযন্ত্রকে যন্ত্র হিসাবে দেখিলে ঐ ঐ ব্যাপারের কিরূপে আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার সম্যক উত্তর পাওয়া যায় নাই।’
আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে একই সঙ্গে যুক্তি ও অনুভূতির মাপকাঠিতে তিনি দর্শন করতে চেয়েছেন। কিন্তু যখনই এই বিজ্ঞানদর্শনের সাহায্যে তিনি জগৎ তত্ত্বের মূল রহস্যের উত্তর খুঁজেছেন তখনই বিজ্ঞানের অপারঙ্গমতা তাঁর চোখে পড়েছে। তাই তিনি ‘মায়াপুরী’ প্রবন্ধে লেখেন—‘এই কাল্পনিক জগত আমারই কিম্ভুতকিমাকার খেয়াল হইতে উদ্ভূত; আমি কিন্তু ঠিক উল্টা বুঝিয়া আপনাকে ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ ও সঙ্কুচিত করিয়া উহার অধীনতা পাশে আবদ্ধ ভাবিতেছি। এই বন্ধনের বৃত্তান্ত লইয়া বিজ্ঞানশাস্ত্র; কিন্তু এই বন্ধন যখন কাল্পনিক বন্ধন, তখন বিজ্ঞান শাস্ত্রের এইখানে গোড়ায় গলদ।’ সেই সার্বিক সত্যের খোঁজে বিজ্ঞান থেকে না পাওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে তিনি প্রবেশ করেছিলেন দর্শনের রাজ্যে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রজ্ঞা তাঁকে পথ খুঁজতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু সেখানেও সব প্রশ্নের তিনি উত্তর পাননি। এবার তিনি উত্তর খুঁজতে গেলেন শাস্ত্র এবং বেদের কাছে। তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন, আট বছর ধরে অনুবাদ করলেন ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। কিন্তু তবু উত্তর পেলেন না। তখন এই মহান পরিব্রাজক ফিরে এলেন বিজ্ঞানেরই রাজ্যে। মনে এই আশা, যে প্রশ্নগুলো তিনি জমা রেখে যাচ্ছেন, ভাবীকালের বিজ্ঞান সেগুলোর উত্তর পৌঁছে দেবে পরবর্তী মানব প্রজন্মের কাছে।
অর্থাৎ রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে বিজ্ঞান শুধু বিজ্ঞান নয়—বিজ্ঞানদর্শনও।
গ. বাংলায় বিজ্ঞানের পরিভাষা নিয়ে কিন্তু সবচেয়ে বেশি চিন্তা ও পথনির্দেশ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। তিনি সব সময় ‘বাঙ্গালীর স্বভাবের উপযোগী’ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের ভাষা সংকলন করতে চেয়েছিলেন।
বিজ্ঞানের বিভিন্ন বাংলা ভাষ্যে তিনি ইংরেজি শব্দ গ্রহণ করারও পক্ষপাতী ছিলেন। তবে সর্বক্ষেত্রে শুধু ইংরেজি শব্দকে বাংলা অক্ষরে ও বানানে লিখে পরিভাষা নির্মাণের বিরোধী ছিলেন তিনি। পরিভাষার ক্ষেত্রে সরলতা ও শ্রুতিমধুরতাতে অত্যন্ত জোর দিতেন রামেন্দ্রসুন্দর। ব্যাকরণ ও ব্যুৎপত্তির খুঁটিনাটি ত্যাগ করে প্রয়োজনবোধে আভিধানিক শব্দকে পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করা বা অভিধানবহির্ভূত নতুন শব্দ সৃষ্টি করার ব্যাপারেও তিনি সুপারিশ করেছেন। তবে যেখানে সুন্দর ও শ্রুতিমধুর সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দ বর্তমান রয়েছে, সেখানে বাংলায় নতুন শব্দ সৃষ্টি করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তিনি লিখেছিলেন ‘শব্দ সৃষ্টি করা দুরূহ; প্রাচীন শব্দের নতুন পারিভাষিক অর্থ দেওয়া ভিন্ন বৈজ্ঞানিক লেখকের গত্যন্তর নাই।’ রামেন্দ্রসুন্দর স্থায়ী বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সমর্থক ছিলেন। পরিভাষার আকস্মিক ও মৌলিক পরিবর্তন তিনি সমর্থন করেননি।
পদার্থের গুণের বা ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে পরিভাষা প্রণয়ন তিনি সমর্থন করেননি। আবার অনেক ক্ষেত্রে একই অর্থ বোঝাতে বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহৃত হতো। এই ত্রুটি ইংরেজি ভাষাতেও বিদ্যমান। এতে তার তীব্র আপত্তি। তিনি বলেছেন—‘প্রত্যেক শব্দ একটি বিশিষ্ট অর্থ ব্যবহার করিবে; সেই শব্দটি আর দ্বিতীয় অর্থে প্রয়োগ করিবে না এবং সেই অর্থে দ্বিতীয় শব্দের প্রয়োগ করিবে না। এই হইল বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মূলসূত্র।’ অর্থাৎ সুবিধা, শ্রুতিমধুরতা, সরলতা, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির দিকে লক্ষ রেখে ব্যাকরণ ও বুৎপত্তির খুঁটিনাটি ত্যাগ করে সুনির্দিষ্ট ও বাঁধাধরা অর্থে বিজ্ঞানের ভাষার ব্যবহার করাকেই রামেন্দ্রসুন্দর সর্বোত্তম মনে করতেন।
৪.
ভারতবর্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে দুইটি ধারা সমান্তরালে বহমান ছিল। একদিকে বৈদিক রীতির টোল, চতুষ্পাঠীকেন্দ্রিক সংস্কৃত-বাংলা শিক্ষাপদ্ধতি, অন্যদিকে মাদ্রাসা-মক্তব ভিত্তিক ফারসি-বাংলা শিক্ষাপদ্ধতি। ইংরেজরা প্রবর্তন করল আধুনিক ধারার নামে ইংরেজি শিক্ষাপদ্ধতি। ইংরেজি শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছিল এদেশের মানুষকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত করতে নয়। এর উদ্দেশ্য ছিল মূলত দুইটি। প্রথমত, শাসনকাজ পরিচালনায় ইংরেজদের সহযোগিতা করার মতো কেরানিকুল তৈরি করা, দ্বিতীয়ত লর্ড মেকলে-কথিত সেই রকম একদল মধ্যবর্তী শ্রেণি তৈরি করা যারা গাত্রাবরণে হবে ভারতীয় কিন্তু মনে-মজ্জায় হবে বৃটিশ। এই শিক্ষার বিষময় ফল ফলতে দেরি হয়নি। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি এই পাশ্চাত্য শিক্ষা দেশবাসীর মনে যে নতুন আশা ও আনন্দ সঞ্চারিত করেছিল, শতাব্দের শেষের দিকে এসে দেখা গেল সমাজজীবনের সর্বত্র একটা হতাশা ও বিষাদের ভাব ফুটে উঠেছে। প্রাথমিক আশা ও আনন্দ তখন তিরোহিত। এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের মূল্যায়ন প্রকাশিত হয়েছে ‘সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার’ নামক প্রবন্ধে। তিনি সেখানে জানাচ্ছেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রণালী আমাদের দেশে সফল হয়নি। কারণ, আমাদের জাতীয়তার ভিত্তির ওপর এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত নয়। এবং সে কারণেই তা অস্বাভাবিক। বাঙালির জীবন ও স্বভাবের সঙ্গে এই শিক্ষার সংযোগ ঘটেনি। ফলে দেখা যাচ্ছে, একদিকে বিলেতি শিক্ষা আমাদের কাজে লাগেনি, অন্যদিকে আমরা ইতোমধ্যেই আমাদের জাতীয় প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী বর্জন করেছি।
রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, তৎকালীন বাঙালির জাতীয় ব্যাধি এটাই। ‘ইংরেজী শিক্ষার পরিণাম’ প্রবন্ধে তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, ইংরেজি শিক্ষার ফলে আমরা ভাঙতে শিখেছি, কিন্তু গড়তে শিখিনি। শিক্ষার সামগ্রী আমাদের প্রচুর মিলেছে, কিন্তু আমরা সেগুলোকে কাজে লাগাতে পারিনি। আমরা শুধু অন্ধভাবে অনুসরণ করেছি, প্রদত্ত জিনিসকে নিজেদের মতো করে নিতে পারিনি। এর জন্যে রামেন্দ্রসুন্দর দায়ী করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীকে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের পক্ষে ১৯১৭ সালে স্যান্ডলার কমিশন গঠিত হলে, তিনি কমিশনকে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন—এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা দেয় না, শুধু পরীক্ষা নেয়। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য এখানে কখনোই বাস্তবায়িত হয়নি।
তাঁর শিক্ষাচিন্তার সারসংক্ষেপ করলে দাঁড়ায়:
ক. শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য স্বদেশপ্রীতি জন্মানো। স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশবাৎসল্য জাগাতে হলে সমাজের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করা দরকার। সমাজের কোথায় কী আছে, অনুরাগীর দৃষ্টি নিয়ে তা খুঁজে দেখতে হবে। অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের মতো মমত্বপূর্ণ হৃদয় নিয়ে অনুসন্ধান করতে হবে বিভিন্ন সামাজিক গলদের। তারপর সমাজের প্রাচীন ইতিহাস যথাসাধ্য তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমাদের সমাজের বিকাশের ও পরিণতির পথ খুঁজতে হবে। এজন্য সেই শিক্ষা প্রয়োজন, যা স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতির জন্ম দেয়।
খ. পাশ্চাত্য শিক্ষা থেকে যেটুকু উপকৃত আমরা হয়েছি, সেই উপকারের বিনিময়ে প্রকৃতপক্ষে অনেক বেশি মূল্য দিতে হয়েছে আমাদের। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। আত্মমর্যাদাবোধ ও অপরের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের জীবন থেকে কমে গেছে। জীবনের মহত্ত্ব ও সম্ভ্রমবোধের মূল্য দিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে কিনতে হয়েছে আমাদের। তাই আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের দৃঢ় অভিমত হচ্ছে—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রকার শিক্ষাপ্রণালীর সম্মিলিত রূপই কেবল বাঙালিদের জন্য সঠিক শিক্ষাপদ্ধতি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।
গ. বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য মুক্ত মানুষ তৈরির জন্য উপযুক্ত পাঠদান। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ব্যস্ত থাকে শুধু পরীক্ষা গ্রহণ নিয়ে। শিক্ষার মান কমে যাওয়া নিয়ে কথা উঠলে বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাপদ্ধতিকে আরো কঠোর করাকেই এর একমাত্র সমাধান মনে করে। রামেন্দ্রসুন্দর প্রশ্নপত্রের সংস্কার ও যুগোপযোগী করার পক্ষপাতী। এ ব্যাপারে তিনি প্রশ্নের নমুনা কেমন হওয়া উচিত, তা পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে উপস্থাপন করেন। পাশাপাশি মেধাবী ছাত্ররা যেন পরবর্তী সময়ে শিক্ষকতায় আকৃষ্ট হন সে ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলেন, বলেন ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক উন্নত করার কথা।
এছাড়া শিক্ষাখাতে ব্যয়-বরাদ্দ বাড়ানোর দাবিও তিনি তুলেছিলেন, কেননা বরাদ্দ ছিল প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল।
ঘ. মাতৃভাষায় সকল বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যাপারে তিনি সবসময়েই সুপারিশ করে গেছেন। কিন্তু ভগ্নহৃদয়ে এটাও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ইংরেজ রাজত্বে তা কখনোই সম্ভব হবে না। আর তাই স্বাধীনতার জন্য কামনাও তাঁর বেড়ে চলছিল।
রামেন্দ্রসুন্দর শিক্ষাবিষয়ক যে সব প্রবন্ধ লিখেছেন এবং বক্তৃতা দিয়েছেন, সেগুলি বিশ্লেষণ করলে ধারণা করা যায় যে, সমাজ ও জাতীয় জীবনের ইতিহাস, বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখে বিজ্ঞানমনস্কতা, স্বদেশপ্রীতি ও সংস্কৃতিবিকাশের অনুকূল একটি শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তাঁর পক্ষপাত ছিল।
আমরা যে জাতিগতভাবে বিজ্ঞানমনস্কতা, রুচিশীলতা, মননচর্চা থেকে ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে যাচ্ছি, তার অন্যতম কারণ দেশে উপযুক্ত শিক্ষাদর্শনের অভাব এবং স্বাধীন জাতির উপযোগী শিক্ষা-অবকাঠামো নির্মাণের প্রতি অনীহা। কিন্তু জাতি হিসাবে টিকে থাকতে হলে সেই শর্ত আমাদের পূরণ করতেই হবে। সেই কারণেই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বা তাঁর মতো অন্যান্য শিক্ষাচিন্তকের কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে বারবার।


-20210909132255.jpg)




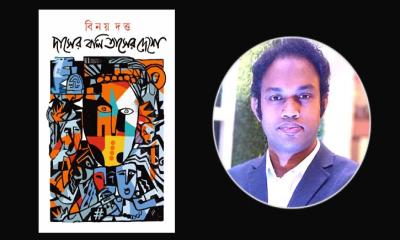
































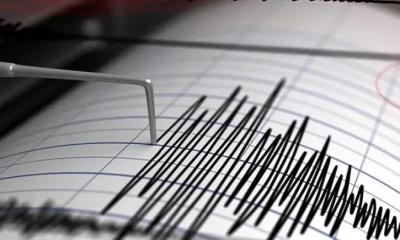







-20250327140635.jpeg)



