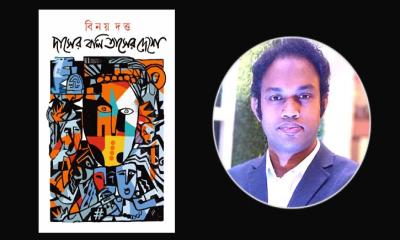গতিময় জীবন এবং জগৎ। যতক্ষণ তা জীবিত, ততক্ষণ তা পরিবর্তনশীল। নানা সময় এবং পরিপ্রেক্ষিতে জীবিত মানুষের মানসিকতা বদলায়, বিশ্বাস বদলায়, বদলায় জীবন এবং জগৎকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি। এই পরিবর্তনই বৈজ্ঞানিক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘজীবী জীবনে সতত এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জগৎ এবং জীবনকে উপলব্ধি করেছেন, যার প্রভাব রয়েছে তাঁর সাহিত্যের নানা শাখা-প্রশাখায়। প্রচলিত ধারণায় যেকোনো বিশ্বাসের স্থিতাবস্থাই প্রতিক্রিয়াশীলতা।
রবীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠার শুরু উপনিষদ দিয়ে। ভোরে উঠে মহর্ষি পিতার মুখে উপনিষদের মন্ত্র শুনে শুনে বালক বয়সেই রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের শিক্ষাকে তাঁর অন্তরে ধারণ করেছিলেন ,তাতে তিনি জীবনভর প্রভাবিত ছিলেন বটে। কিন্তু প্রতিনিয়ত নব নব সত্য তাঁর সম্মুখে উন্মোচিত হয়েছে এবং নির্দ্ধিধায় “না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ” বলে তাকে গ্রহণ করেছেন।
ভাববাদী রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিজীবনের ঊর্ধ্বে সাহিত্যে বারবার নানা সত্যে জেগে উঠেছেন। কবিতায়, গানে, ছোটগল্পে ব্যক্তিগত চিঠি এবং গদ্যে তাঁর নব নব ভাবগত আত্মোপলব্ধি প্রাণ পেয়েছে শব্দে এবং বাক্যে। তাঁর বিশাল সৃষ্টিসম্ভারের সাহিত্যের সব কটি মাধ্যম বিদ্যমান। সব মাধ্যমের মধ্যে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম তাঁর নাট্যসাহিত্য। সেখানে তিনি চরমভাবে রাজনৈতিক। কিন্তু কোনোভাবেই সেই রাজনীতি বক্তৃতা কিংবা স্লোগানের মতো সরাসরি কিংবা উচ্চকিত নয়। বরং অসাধারণ এক রূপক সংকেতের মোড়কে পুরো বিশ্বের রাজনৈতিক কাঙ্ক্ষাকে তিনি ব্যক্ত করে গেছেন নাটকগুলোতে।
রবীন্দ্রনাথের নাটকের সংখ্যা ষাটের বেশি। কিন্তু সাধারণে কবি রবীন্দ্রনাথ, গীতিকবি রবীন্দ্রনাথ, গল্পকার রবীন্দ্রনাথ এমনকি চিত্রকর রবীন্দ্রনাথকেও যেভাবে জানে, ঠিক সেভাবে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ যেন ততখানি আদৃত নন, যতখানি উচিত ছিল। গভীর রাজনৈতিক দর্শনের পাশাপাশি তাঁর নাটকগুলোতে রয়েছে গান, নৃত্যসহ কৌতুকময়তাও। গীতিনাট্য থেকে শুরু করে নৃত্যনাট্য, নাট্যের সব কটি শাখা স্পর্শ করেছেন তিনি। সেদিক থেকে এগুলোর কারণেও তাঁর নাট্যসৃষ্টিগুলো আরও অধিক মনোযোগ এবং চর্চা দাবি করে। অথচ রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁর রচিত সব কটি নাটক মঞ্চস্থই হয়নি। তিনি নিজেই এমন ধারণা পোষণ করতেন যে, তাঁর সব নাটক মঞ্চোপযোগী নয়। একাধারে অভিনেতা ও নাট্যপ্রয়োগকর্তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নিজের একাধিক নাটক নিজে নির্দেশনা দিয়েছেন, অভিনয়ও করেছেন। আবার অনেক নাটক শুধু লিখেই ক্ষান্ত দিয়েছেন। সচেতনভাবেই মঞ্চায়ন এড়িয়ে গেছেন।
তখন রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসাত্মক নাটকগুলো, যেমন চিরকুমার সভা, শেষরক্ষার বেশ কয়েকটি মঞ্চায়ন হয়েছিল বটে, তাঁর ট্র্যাজেডি নাটক বিসর্জনও মঞ্চস্থ হয়েছিল কিন্তু তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাট্যরচনা ডাকঘর, রক্তকরবী, রাজা, অচলায়তন মুক্তধারা নাটকগুলো মঞ্চায়নের খবর পাওয়া যায় না।
মঞ্চনাটক দর্শককেন্দ্রিক শিল্পমাধ্যম। হয়তো ধারণা ছিল তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, গুরুত্ববহ এবং রাজনৈতিক দর্শন সমৃদ্ধ নাটকগুলো রূপক ও প্রতীকী সংলাপের আবছায়া ভেদ করে দর্শকপ্রিয়তা অর্জন করবে না। কিংবদন্তি শিশির কুমার ভাদুড়ীও রবীন্দ্রনাথের অনন্য নাট্যসৃজন রক্তকরবী মঞ্চস্থ করার সাহস করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ১৩ বছর পর আরেক কিংবদন্তি শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় কলকাতার বহুরূপী নাট্যদল রক্তকরবী মঞ্চস্থ করে দর্শককে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আজকের বাংলাদেশেও রক্তকরবী সর্বাধিক মঞ্চস্থ রবীন্দ্রনাটক রক্তকরবী।
মূলত অচলায়তনের সঙ্গে মুক্তধারার যে বিপরীত সম্পর্ক, রবীন্দ্রনাথের নাটক সেই অচলায়তন থেকে মুক্তধারার পথে উৎসারিত। এজন্যই তাঁর নাটকগুলো প্রবলভাবে রাজনৈতিক সচেতন। অচলায়তন রচিত হয়েছে ১৯২২ সালে, মুক্তধারাও তাই। ১৯২২ সালে। এই নাটক দুটিরই মূল প্রতিপাদ্য জীবনের জড়তা আর তার থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। ব্যক্তিমানুষ তো কেবলই ব্যক্তিমানুষ নয়। সমাজ এবং রাষ্ট্রের অংশ। সমাজ এবং রাষ্ট্রে তার যে অবরুদ্ধ অবস্থা, তা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা চিরকালীন।
রবীন্দ্রনাটক উপসংহারে সব সময় ইতিবাচক। আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু... তবু তাঁর নাটকে জীবন জেগে থাকে। জীবনের সংকটময় বাস্তবতা রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করতেন না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জীবনকেই জয়ী করতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সব কটি নাটকে মানুষের উত্থান গেয়েছেন মনুষ্যত্বের পরাজয়ের বিপরীতে। তাঁর নাটকে মুক্তির জন্য মানুষ উন্মুখ, কিন্তু জীবনের পরতে পরতে প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করা সহজ নয়। এই কাঠিন্যকে অতিক্রম করার প্রয়াসে রবীন্দ্রনাথ আশ্রয় নিয়েছেন রূপক ও সংকেতের। রবীন্দ্রনাথের নাটকে এই যে রাজনৈতিক দর্শন, এই দর্শন ব্যক্ত করার জন্য যে সংকেত ও রূপকের ব্যবহার, তা সত্যি সব সময় সাধারণের বোধগম্য হয়ে ওঠেনি। ফলে রবীন্দ্রনাথের কালোত্তীর্ণ অনেক নাটকই হয়তো রয়ে যায় সাধারণ দর্শকের বোধগম্যতার বাইরে।
রক্তকরবী রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ নাটক। নাটকটির রচনাকাল ১৯২৬। এ নাটকের অন্তর্গত দর্শন ভীষণভাবে রাজনৈতিক। শাসক ও শোষকদের সর্বগ্রাসী লোভের কবলে প্রকৃতির অকৃত্রিমতা। কিংবা যন্ত্রের দাপটের কাছে মানুষের অসহায়ত্ব। এই লড়াই সর্বকালীন। রবীন্দ্রনাথ যখন রক্তকরবী লিখছেন, তখন এই লড়াইয়ের পক্ষ-বিপক্ষ যা ছিল, সময়ের সঙ্গে তা হয়তো বদলে গেছে। কিন্তু লড়াই চলমান। কৃত্রিমতার সঙ্গে প্রকৃতির, যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের।
রবীন্দ্রনাথ ঠিক কোন ধরনের শোষককে রূপকের মোড়কে উপস্থাপন করেছেন, তা নাটকে অস্পষ্ট। রাজা বলে যাকে তিনি চিহ্নিত করেন, তা কোনো ব্যক্তিমানুষ নয় মোটেই। বরং তা একটি ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থায় অর্থলিপ্সা, পুঁজির আধিপত্যের কাছে মনুষ্যত্ব একেবারেই গৌণ। রবীন্দ্রনাথ নিজে রক্তকরবী সম্পর্কে বলেন, “মাটি খুঁড়ে যে পাতালে ধন খোঁজা হয় নন্দিনী সেখানকার নয়, মাটির উপর তলে যেখানে প্রাণের, যেখানে রূপের, যেখানে প্রেমের লীলা নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সেই সহজ সৌন্দর্যের।”
নন্দিনী এবং রক্তকরবী আসলে একই, তারাই প্রকৃতি,স্বাভাবিক, প্রবহমান। যে স্বাভাবিকতা মকররাজের যক্ষপুরীতে অনুপস্থিত। সেখানে নাগরিকেরা আত্মপরিচয় হারিয়েছে,হারিয়েছে মানুষের আনন্দ বেদনার স্বাভাবিক প্রবণতা। সবাই সম্পদ আহরণের যন্ত্র, সবাই একটা সংখ্যা। প্রকৃতির প্রতিরূপ নন্দিনী তার স্বভাবগুণেই ব্যবস্থাটাকে ভাঙতে চায়। কোনো ভয়ভীতি অস্ত্র নিয়ে নয়, ভালোবাসা দিয়ে। রাজাকে সে জানায়, “আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমার সঙ্গে লড়াই।” নিজের গড়া সিস্টেমে রাজা নিজেই বন্দি। সে নিঃসঙ্গ। তার কোনো বান্ধব নেই। নিজের গড়া ব্যবস্থায় তার নিজেকে বন্দি থাকতে হয় নিরাপত্তার কারাগারে। যে সর্দার ও মোড়লরা তার চারপাশে রয়েছে তারা তার পক্ষে কাজ করে, আবার তাকে পাহারাও দেয়, ঘিরে রাখে। কিন্তু রাজার জন্য তাদের ভালোবাসা নেই, আবেগ নেই, তারা কেবল পাহারা দেওয়ার যন্ত্র বৈ নয়। কী আশ্চর্য মেটাফর, এই সময়েও কত প্রাসঙ্গিক এই রাজতন্ত্রের ফাঁপা কিন্তু লোভী ভাবমূর্তি। আমাদের এ যুগের শাসকের বিশ্বস্ত প্রতিমূর্তি। অথচ এই যক্ষপুরীর বাইরেই জীবন্ত প্রকৃতি, সেখানে কৃষিকাজ চলে, সেখান থেকে ডাক আসে : “পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয়রে চলে আয়, আয়।”
সোনা খুঁড়ে তুলেছে খোদাইকাররা,এই সম্পদের প্রতি রাজার লোভ প্রচণ্ড। কিন্তু নন্দিনীর প্রতি আকর্ষণও সে অস্বীকার করতে পারে না। বিদ্রোহী রঞ্জন রাজ্যের যান্ত্রিকতাকে মানে না, বিশু পাগলাও তাই। রঞ্জন আর বিশু পাগলাকে শাস্তি দিতে চায় রাজা কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুন্দরের জয় হয়, রাজা বের হয়ে আসে নন্দিনীর পিছু পিছু। জয় হয় প্রকৃতির। যন্ত্র হেরে যায় প্রকৃতির কাছে।
রক্তকরবীর এই যন্ত্র আর প্রকৃতির লড়াই সমকালীনতা অতিক্রম করে চিরকালীন হয়ে উঠেছে। এই যে প্রাণপ্রাচুর্যের প্রতীক নন্দিনীর আহ্বানে যন্ত্রনির্ভর, ধনলিপ্সু রাজার মুক্তি এই কাঙ্ক্ষা নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের। এটাই তাঁর বার্তা, এটাই প্রত্যাশা তাঁর।
১৯২২-এ লেখা তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাটক মুক্তধারা। উত্তরকূট শিবতরাইয়ের ওপর কর্তৃত্বপরায়ণ।এই কর্তৃত্বের কারণ জলের প্রবাহ। জলের স্বাভাবিক ধর্ম নিচের দিকে প্রবাহিত হওয়া। সেই প্রবাহ বাঁধ দিয়ে রুদ্ধ করে উত্তরকূট। আর এর প্রতিক্রিয়ায় শিবতরাইয়ের উদ্ভূত বিদ্রোহ দমনে উত্তরকূটের যুবরাজ অভিজিৎকে শিবতরাইয়ের শাসনকর্তা করে পাঠায়। দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজারা খাজনা দিতে অস্বীকৃতি জানালে রাজা রণজিৎ নির্দয় হয়ে উঠে, দুর্ভিক্ষ হয়েছে বলে রাজার প্রাপ্য তো বন্ধ হতে পারে না।
জলের প্রবাহের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে অন্যের ওপর কর্তৃত্ব করার যে রাজনীতি বর্তমানকালে বিশ্বজুড়ে দেখা দিয়েছে, এবং আজকের দিনে তেলের জন্য যে হাহাকার, জলের রূপকে সেই যুদ্ধের কথা রবীন্দ্রনাথ সেই ১৯২২ সালে লিখে গেছেন। দূরদর্শিতায় আর ভবিষ্যৎ দর্শনে নাটকগুলোতে অসাধারণ রূপক সংকেতের আশ্রয় নিয়েছেন। যেখানে রাশিয়া ইউক্রেনের জায়গায় অবলীলায় উত্তরকূট কিংবা শিবতরাই বসিয়ে দেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের মানসাকাঙক্ষার প্রতিফলনে নাটকের সমাপ্তি ঘটে জলস্রোতের বাঁধ ভাঙা শব্দের ভেতর দিয়ে।
বাঁধ ভাঙার গান শুনি তাসের দেশেও। এই বাঁধ অবশ্য জলপ্রবাহের নয়, নিয়মকানুন শৃঙ্খলের। নাটকের শেষের যে গান, ‘বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, বন্দী প্রাণমন হোক উধাও’ চিরকালীন মুক্তিকাঙ্ক্ষার সুর। জনগণের ভেতর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, তার বাস্তবায়ন প্রথাগত নেতৃত্ব দিয়ে সম্ভব নয়। প্রয়োজন নতুন চিন্তা ও নেতৃত্বের; তাসের দেশ এই সত্যের দিকেও ইঙ্গিত করছে।
রবীন্দ্রনাথের আরেকটি নাটক ডাকঘর। (১৯১২),ছোট্ট অমলের সেখানে বেরিয়ে পড়ার আকাঙ্ক্ষা। অমল মুক্তির ডাক শুনতে পায়, সে অস্থির মুক্তির জন্য, কিন্তু বন্দিত্বই তার ভাগ্য। ছাড়া পাওয়ার কোনো উপায় নেই। নিঃসন্তান মাধব দত্ত অমলকে দত্তক হিসাবে নিয়েছে। অমল এখন গ্রাম্য কবিরাজের চিকিৎসাধীন, যে কবিরাজ তার চলাফেরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছে। সে জানালার পাশে বসে থাকে, দূরের পাহাড় দেখে, পাহাড় ঘেঁষে পথ দেখে,দূরের গ্রাম। দইওয়ালাকে দেখে, বালকদেরকে দেখে যারা মাঠে যাচ্ছে খেলা করতে, সুধাকে দেখে, যে মালিনীর মেয়ে। তাদের সঙ্গে তার ভাব হয়। অমলের দুঃখ তারা বুঝলেও কেউ বাইরে নিয়ে যেতে পারে না। যারা বুঝলে অমল মুক্তি পেতে পারে, বোঝে না কেবল তারা। কবিরাজ এবং মোড়ল। অমলের অসুখ বেড়ে গেলে একসময়ে জানালার পাশে বসে থাকা বন্ধ হয়ে যায়। মাধব দত্তের ধারণা জানালার পাশে রোজ রোজ বসে থেকেই তার ব্যামোটা বেড়ে গেছে। অমল বলে, “আমার ব্যামোর কথা আমি কিছুই জানি নে, কিন্তু সেখানে থাকলে আমি খুব ভালো থাকি।”
এরই মধ্যে অমল দেখে নতুন ডাকঘর বসেছে। ঠাকুরদাকে সে জানায়, “প্রথমে যখন আমাকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে রেখে দিয়েছিল তখন আমার মনে হয়েছিল যদিন ফুরাচ্ছে না, আমাদের রাজার ডাকঘর দেখে অবধি আমার রোজই ভালো লাগে।” সে আশা করে রাজার কাছ থেকে তার নামে চিঠি আসবে। শেষ পর্যন্ত এক রাতে রাজদূত এসে উপস্থিত হয়। রাজকবিরাজও আসে। দরজা জানালা সব খুলে দিতে বলে। অমলের ঘুম পায়। সে ঘুমিয়ে পড়ে। হয়তো অমলের মৃত্যু হয়েছে। ঘুম হোক আর মৃত্যুই হোক, সামান্য মানুষের বন্দিত্ব থেকে অমল যে মুক্তি পেয়েছে।
অচলায়তন ও ১৯১২ সালে লেখা। উভয় নাটকেই মানুষের বন্দিত্ব। ডাকঘরে একজন বালক, অচলায়তনে একটি জনগোষ্ঠী আটকা পড়ে আছে। অচলায়তনে কোনো কিছুই সচল নয়। জ্ঞানও সেখানে অবরুদ্ধ। অচলায়তন কেবল বাইরের নয়, ভেতরেরও অচলায়তন। ভেতরের অচলায়তনও ভাঙতে হবে।
রবীন্দ্রনাথের একেবারে প্রথম দিকের নাটক বিসর্জন, ১৮৯০ সালে লেখা। সেখানেও সুন্দর অসুন্দরের বিরোধ। শেষ পর্যন্ত অপর্ণা অর্থাৎ সুন্দরের জয় হয়। জয়সিংহকে হারিয়ে রঘুপতি অপর্ণার মধ্যে নিজের জননীকে দেখতে পায়, পাষাণের কালীমূর্তিকে সে গোমতী নদীতে নিক্ষেপ করে। অপর্ণা তাকে পিতা বলে সম্বোধন করে মন্দির থেকে বের হয়ে আসতে বলে। ভিখারিণী অপর্ণার অন্য কোনো সম্পদ নেই স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা ছাড়া। রঘুপতি ধার্মিক নয়, ধর্মব্যবসায়ী। তার আসক্তি ছিল ক্ষমতায়। গোবিন্দমাণিক্যের ভেতর একজন সন্ন্যাসী ছিল, এমনটা বলা যায়; কিন্তু তিনি যে স্ত্রীর অনুরোধ, পুরোহিতের ষড়যন্ত্র, প্রজাদের অসন্তোষ সবকিছুকে উপেক্ষা করে জীব বলিদান নিষিদ্ধ করে দিয়ে ‘সহস্র বছর ধরে’ প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন সেই শক্তিটা পেলেন কোথায়? পেয়েছেন ওই অপর্ণার কাছ থেকেই। রাজার নিজের উক্তি এই রকমের : ‘বালিকার মূর্তি ধরে/ স্বয়ং জননী মোরে বলে গিয়েছেন/ জীবরক্ত সহে না তাঁহার?’ জয়সিংহ পারতো মন্দির ত্যাগ করে অপর্ণার সাথে পথে চলে আসতে, রক্তকরবীর রাজা যেমনভাবে বেরিয়ে এসেছে নন্দিনীর পিছু পিছু, কিন্তু কিশোর জয়সিংহের ভেতর অতটা শক্তি ছিল না। চূড়ান্ত বিচারে মন্দিরের দেবী মা কালীও পরাভূত হয়েছে অপর্ণার কাছে। অপর্ণার কারণেই নিষিদ্ধ হয়েছে জীববলিদান, পাষাণ মূর্তি নিক্ষিপ্ত হয়েছে নদীতে। অপর্ণা যেন রক্তকরবীর নন্দিনীর অন্য রূপ নন্দিনী একজন রাজাকে মুক্ত করেছে, পুরোহিততন্ত্রের আধিপত্যকে পরাভূত করে। অপর দিকে অপর্ণা মুক্ত করতে পেরেছে একটি রাজ্যকে। রবীন্দ্রনাথের সময়ে দাঁড়িয়ে পশুহত্যার বিরুদ্ধে এই রায় দেওয়া এক দুঃসাহসিক কাজ।
‘রাজা’ নাটকে অন্ধকার ঘরে যে রাজা থাকেন, রানির সঙ্গে তার মিলন অন্ধকারেই হয়। রানি রাজাকে আলোতে দর্শন করতে চায়, রাজা রাজি হয় না। অন্যদিকে সুরঙ্গমা রাজার দাসী, সে কিন্তু রাজাকে দেখতে পায় সেবার মধ্য দিয়ে, শুধু রানি, রাজাকে যে একান্ত আপন ও নিজের মতো করে পেতে চায়। সুদর্শনা রাজাকে দেখতে চায়, বুঝতে চায় না। রাজা জানেন সুদর্শনা তাঁর রূপটাকে সহ্য করতে পারবে না। তিনি জানতেন যে রানি তার বাহ্যিক রূপটাকেই দেখবে, শাসকরাজার রূঢ়তা দেখবে। ভেতরের রূপ দেখার ক্ষমতা রানির নেই। রাজার রূপ নিয়ে নানা ধরনের ব্যাখ্যা হতে পারে, সুদর্শনার উদ্দেশে রাজার যে গান, তা সর্বজনীন : “আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব।”
রাজা শাসক, তাঁকে শাসন করতে হয়। এবং শাসনের ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর হতে হয় বৈকি। এ নাটকের রাজনৈতিক দর্শনটি উল্লেখযোগ্য। দেশের শাসক, নিজেকে সর্বসাধারণের কাছ থেকে নিজেকে আড়ালে রাখতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। রাজা থাকবেন, তিনি লক্ষ করবেন সমস্ত কিছু, মানুষের অগ্রগতিকে প্রতিহত করে যে শক্তি তার বিরুদ্ধে সমবেত প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন। কিন্তু সমস্যার স্থায়ী সমাধান তো কেবল শত্রুপক্ষের তাৎক্ষণিক পতনে ঘটবে না, তার জন্য যা আবশ্যক, সেটি হলো সব মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা।
শিক্ষার মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তনে রবীন্দ্রনাথের আস্থা অবিচল ছিল। কিন্তু শিক্ষা নিজেই যখন শাসক গোষ্ঠীর শাসনের হাতিয়ার হয়ে যায় তখন তার দশাটা কী হয় সে ছবি অচলায়তন, মুক্তধারা ও তাসের দেশে বিশেষভাবেই রয়েছে। যথার্থ শিক্ষার জোর আছে। কিন্তু শিক্ষাকেও মুক্ত করা চাই। এবং মুক্ত করবার সেই লক্ষ্যে বলপ্রয়োগ যে অপরিহার্য রবীন্দ্রনাথ তা মানেন।
খুবই ছোট একটি নাটক ‘রথের রশি’ (১৯৩২)। কিন্তু যেমন নান্দনিক বিচারে, তেমনি দার্শনিক বিবেচনায় এ নাটক এক অনন্যসাধারণ রচনা। রথটি সময়ের রথ। ব্যবস্থা তাকে অনড় করে দিয়েছে। কিন্তু রথটিকে চলতে হবে, মানুষের সভ্যতা থেমে যেতে পারে না, তাকে ভবিষ্যতের দিকে চলতেই হবে। সেই যে অগ্রগতি সেটা অসম্ভব করে তুলেছে এতকাল যারা রথের যাত্রী ছিল তারাই। রাজা, পুরোহিত, সৈনিক, ধনিক, সবাই ব্যর্থ হয়েছ। নতুন শক্তি শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছায়, শূদ্র শক্তি। তারা একসঙ্গে যখন টান দিয়েছে রথের রশিতে রথ তখন জেগে উঠেছে, এবং প্রবল বেগে এগিয়ে গেছে। প্রচলিত, প্রতিষ্ঠিত পথ যখন থেমে যাবে নতুন পথ তৈরি হবে। ওই যে শূদ্রদের টানে রথ চললো এর তাৎপর্য কেবল এই নয় যে বর্ণভেদ প্রথা ভেঙে না পড়লে সভ্যতার মুক্তি নেই; তাৎপর্যটি আরও গভীর। শূদ্রের রূপকে রবীন্দ্রনাথ শ্রমিক শ্রেণিকেই নিয়ে এসেছেন। এরাই চাষ করে এবং অন্ন জোগায়, এরাই তাঁত বোনে, রথও এরাই টেনেছে। কিন্তু এতকাল এদের স্থান ছিল নিচে, রথের চাকার তলায় পড়ে পিষ্ট হওয়াই ছিল এদের নিয়তি।
রবীন্দ্রনাথের নাটক রাজনৈতিক ও রূপক সাংকেতিকতার দিক থকে তাৎপর্যপূর্ণ তাদের নান্দনিক ও ঐতিহাসিক মূল্য কোনোটাই আর এ যুগে অস্বীকার করার জো নেই।