জাতীয়তাবাদ, জাতিসত্তা ও তৎসম্পৃক্ত জাতীয় জাগরণের বিষয়সমূহ আধুনিক সমাজ থেকে উদ্ভূত। বিশেষত ইউরোপীয় উৎপাদনব্যবস্থা কৃষি থেকে শিল্পে উন্নীত হওয়ার পর যে শিল্প শ্রমিক, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও তৎসম্পৃক্ত পেশাজীবী শ্রেণি তথা বুর্জোয়া-পেটি বুর্জোয়া শ্রেণি বিকশিত হয়; এবং তাদের মাধ্যমে রাজতান্ত্রিক শাসনকাঠামোর পরিবর্তে যে গণপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, সেই চেতনাধারার নিরিখেই শিল্পায়িত রাষ্ট্রসমূহে বিকশিত ও গঠিত হয় স্বতন্ত্র ধারার জাতিসত্তা। ভারতীয় ভৌগোলিক কাঠামোভুক্ত এ বাংলায় ইউরোপের আদলে শিল্প সমাজ গড়ে ওঠেনি। ফলে জাতিগত জাগরণের লক্ষ্যে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের সূচনা পর্যায়ে ও পরবর্তী শত বছরেও বিকশিত হয়নি আধুনিক ধারার জাতিসত্তা।
প্রকাশ থাকে যে সেই মহাভারতের সময় থেকে আজকের বাঙালি অধ্যুষিত (উভয় বঙ্গ) এ অঞ্চলে একটি সংহত সমাজের উপস্থিতি ছিল। দ্রৌপদীর স্বয়ম্ভর সভায় ছিল বঙ্গীয় রাজকুমারের প্রতিনিধিত্ব। ২৩ শত বছর আগে মৌর্যদের রাজধানী মগধে রপ্তানি হতো এ অঞ্চলের সুতি ও সিল্ক বস্ত্র। আদিকালে এ অঞ্চল থেকে সুদূর সিংহল ও আধুনিক ভিয়েতনামের মধ্যাঞ্চলে গিয়ে গিদ্বিজয়ী বাঙালি বীর সন্তানেরা প্রতিষ্ঠা করেছিল রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। পরবর্তী পর্যায়ের মুসলিম শাসকদের শাসনামলে ভৌগোলিকভাবে সংহত হলেও জাতিসত্তা বিকাশের বিষয়টি অধরাই রয়ে যায়। শুধু বাংলাতেই নয়, পুরো উপমহাদেশজুড়ে যে বর্ণবাদী সমাজ বিরাজ করছিল, হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলিম শাসকনির্বিশেষে কেউই তার ভিত নাড়াতে পারেনি। তদুপরি এতদঞ্চলে যেমন ধর্মভিত্তিক জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটেনি, তেমনি বিকাশ ঘটেনি শ্রেণিভিত্তিক রাষ্ট্রচেতনার। অতঃপর ইতিহাসের এক বাঁকে সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলে অবরুদ্ধ হতে হয় এখানকার আপামর জনগোষ্ঠীকে। স্রষ্টার প্রতি সমর্পিত হয়ে পরিতুষ্ট থাকতে হয় তাদের। পেটে ক্ষুধা নিয়ে প্রয়োজনে নির্বিবাদে আলিঙ্গন করতে হয় মৃত্যুকে। কিছু ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে এহেন চেতনাগত নিস্পৃহতা বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বিরাজিত ছিল এই অচলায়তনে। কুখ্যাত ৫০-এর মন্বন্তরের সময় খাবারে পূর্ণ দোকানগুলোর সম্মুখে অভুক্ত লোকের ঝাঁক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেও কেউ বেঁচে থাকার তাড়নায় খাবারের দোকানগুলোতে হামলে পড়েনি। সেই সাহস, সেই চেতনা, সেই স্পৃহা তাদের মধ্যে জাগরিত হয়নি। আজন্ম লালিত ধর্মীয় মূল্যবোধ, ভাববাদী ভাবনাধারা ও ভীরুতা তাদের বেঁচে থাকার পথ সন্ধানে করেছে নিরুৎসাহিত-জীবনকে নিক্ষেপ করেছে নিষ্পেষণের জাঁতাকলে।
একই অবস্থা দেখা গিয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন-শোষণের সূচনা পর্যায়ে। কোম্পানির লোকদের অতিমুনাফা লোভী আগ্রাসনের ফলে সৃষ্ট ১৭৭১ সালের মহাদুর্ভিক্ষ সূচিত হওয়ার প্রারম্ভেই গ্রামীণ সমাজের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ খাদ্যাভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ধনবান পরিবারগুলোর একটি বড় অংশ পরিণত হয় নিঃস্ব ভিখারিতে। বাংলার প্রায় প্রতিটি জেলায় দৃশ্যমান হয়ে ওঠে এহেন বিপর্যস্ততা। বিত্তবান ও সংগতিসম্পন্ন জমিদারদের অনেকেই সে সময় নিঃস্ব জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে অভিপ্রেত খাজনা আদায়ে ব্যর্থ হয়ে ইংরেজ কোম্পানির কোপানলে পড়ে হারিয়েছিল জমিদারি। কেউ কেউ হয়েছিল কারারুদ্ধ। প্রকাশ থাকে যে ‘যে সকল প্রাচীন পরিবার মোগলদের অধীনে আংশিক স্বাধীনতা ভোগ করতো এবং ব্রিটিশ সরকার পরে যাদের জমিদার বলে মেনে নিয়েছিলেন, তাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। নিম্নবঙ্গের দুই-তৃতীয়াংশ প্রাচীন সম্ভ্রান্ত সামন্ত পরিবারের পতন ১৭৭০ সাল থেকেই শুরু হয়েছিল।’ (হান্টার। পৃষ্ঠা: ৪৭-৪৮) জাতীয়তাবাদী চেতনার নিস্পৃহতার কারণেই একটি বিদেশি কোম্পানির পক্ষে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল ও এ ধরনের আগ্রাসী শোষণ ব্যবস্থা চলমান রাখা যে সম্ভব হয়েছিল; সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণের অবকাশ নেই। দুর্ভিক্ষপীড়িত বাঙালি জাতির এহেন বিপর্যয়কর অবস্থায় নিপতিত হওয়া প্রসঙ্গে উইলয়াম হান্টার লিখেছেন, ‘বাঙালিদের দুঃখ-দুর্দশার একটি গূঢ়তম কারণ আছে। তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের একটি দৃঢ় মনোভাব থাকলে কখনোই তাদের ওপর এমন একটানা অত্যাচার হতে পারতো না।’ (প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা: ৬৬) পরবর্তী সময়েও দীর্ঘকাল জাতীয়তাবাদী চেতনার অনুপস্থিতি হেতু এ জাতিকে হতে হয়েছে নিষ্পেষিত ও নিগৃহীত।
ভাববাদী ধারায় আবিষ্ট এ অচলায়তনের জনগোষ্ঠীর কাছে জীবনধারণের আবশ্যিক অনুষঙ্গগুলো বরাবরই অনাদৃত ছিল। কোনো ঘটনারই কার্যকারণ সম্পর্ক সন্ধানে তারা কখনো তেমনভাবে কৌতূহলী হয়নি। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও পরবর্তী পর্যায়ের মুসলিমরা স্রষ্টার ওপর সব দায় চাপিয়ে নিজেরা থেকেছে নিষ্ক্রিয়-নিষ্প্রাণ। রোগে, শোকে, দুর্ভিক্ষে ও শোষণে জর্জরিত হয়ে দুর্ভাগ্যকে নিয়তির লিখন মনে করে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তুলেছে। জীবনবিমুখ সুরধারায় মাতোয়ারা হয়ে সুখের সন্ধান করেছে। ‘সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই’ বাণীটি হৃদয়ে ধারণ করেও মানুষ হতে সচেষ্ট হয়নি। সাব হিউমান হিসেবেই জীবনকে টেনে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে ধ্বংসের প্রান্তসীমায়। বিষয় জ্ঞানহীন এহেন জাতিগত নিরাসক্ততার নিগূঢ় উন্মোচনকালে কমরেড মুজফ্ফর আহমদ লিখেছেন, ‘...ভারতবর্ষ একটি অভিশপ্ত দেশ, নিরবচ্ছিন্ন অভিশাপ এর সকল দিককে ঘিরে রেখেছে। এদেশে প্রাচীনকালে বড় বড় ঋষিরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা নাকি বলে গিয়েছেন জীবনটা নিছক মায়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাঁদের মতে জীবনে বিয়োগের অঙ্কটা যতই বাড়ানো যায়, ততই নাকি পুণ্যের কাজ করা হয়, আর যোগের অঙ্ক বাড়ালে হয় পাপ, এমন বড় পাপ যে তার কোনোকালে ক্ষমা নেই। পরে এলেন মুসলমানরা। তাঁরাও নিয়ে এলেন গোটা কতক থিওলজি অর্থাৎ ব্যবস্থাশাস্ত্রের কেতাব। কাজেই ব্যবস্থা-দাতা অর্থাৎ মোল্লার সংখ্যা এদেশে খুব বেড়ে গেল। এই মোল্লারা শেখাচ্ছেন, পৃথিবীর দুঃখ-কষ্টটা কিছুই নয়। কোনোরকম করে দুনিয়ার এ দু’দিনের জীবনটা দুঃখ-কষ্টে কাটালেই হ’ল, তারপরে, পরকালে অক্ষয় স্বর্গে অনন্ত জীবন, আর অনন্ত সুখ। মোটের উপর, সাধু-সন্ন্যাসী-গুরু-পুরোহিত ও মোল্লা-মৌলবী-ফকিরগণ ভারতের জনসাধারণের হৃদয় হ’তে সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার বিলোপ-সাধন করে দিয়েছেন। এঁদের ফাঁদে পড়ে ভারতের কৃষাণ ও শ্রমিকগণ বাকীর লোভে হাতে-পাওয়া জিনিষটা খুইয়ে বসে আছে। (লাঙল। ১৪ জানুয়ারি, ১৯২৬। পৃষ্ঠা: ৫-৬)
পাশ্চাত্যের আর্থসামাজিক কাঠামো পরিবর্তিত হয়েছে উৎপাদিকা শক্তির পরিবর্তনের প্রভাবে। বিজ্ঞানের নানামুখী আবিষ্কারের সাথে সাথে সেই সমাজে সাধিত হয়েছে যুগোপযোগী পরিবর্তন। সামন্ত সমাজের গর্ভে জন্ম নেয়া পুঁজিবাদী সমাজ বিকাশের সাথে সাথে শোষণের আঙ্গিক যেমন পরিবর্তিত হয়েছে, তেমন পরিবর্তিত হয়েছে জীবনমুখী চিন্তনের। শিল্পপতিদের উৎপাদন ব্যবস্থা চলমান রাখার স্বার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে স্বাধীন মানুষ তথা আধুনিক শ্রমিক। ভূমিদাস ব্যবস্থা এরই প্রবাহে হয়েছে অবলুপ্ত। পুঁজিবাদের ঊষালগ্নে এই স্বাধীন শ্রমিকরা পুঁজি বাজারের বৃহত্তর বলয়ে শৃঙ্খলিত থাকলেও অচিরেই হয়ে ওঠে রাজনৈতিক অঙ্গনের অত্যাবশ্যক অংশীদার। সাম্য-মৈত্রী-ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের প্রয়োজনে হয়ে ওঠে অধিকারসম্পন্ন মানুষ। নিজেদের অধিকার সম্পর্কে হয়ে ওঠে সচেতন। লড়াই-সংগ্রামের এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণ হয়ে ওঠে রাষ্ট্র কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা হয়ে পড়ে সংকুচিত। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, উপমহাদেশের সামাজিক পরিবর্তন সেভাবে সাধিত হয়নি। পাশ্চাত্যের মতো এখানকার রাজতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামো জনগণের মাধ্যমে অবলুপ্ত কিংবা সাংবিধানিক পরিধিতে আবদ্ধ হয়নি। তা উৎপাটিত হয়েছে বৈদেশিক আগ্রামী শক্তির মাধ্যমে। সমাজ পরিবর্তনের ধারাও সেভাবে এগোতে পারেনি। শাসনব্যবস্থা পরিবর্তিত হলেও সমাজব্যবস্থা কখনো পরিবর্তিত হয়নি। সামন্ত সমাজ থমকে থেকেছে সামন্ত সমাজেরই অতলে। এখানে যেমন পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেনি, তেমনি বিকশিত হয়নি আধুনিক শ্রমিক ও পেশাজীবীসহ সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণি। ফলে বেঁচে থাকার স্পৃহাও জাগ্রত হয়নি। ভাঙেনি ভারতের আবহমানকালের অচলায়তন। এ বিষয়ে আলোকপাতকালে ওই একই প্রবন্ধে কমরেড মুজফ্ফর আহমদ লিখেছেন: ‘ভারতের প্রাণশক্তি হচ্ছে ভারতের চাষী আর মজুরগণ। এঁদের সংখ্যা শতকরা ৯৫ জনের কম নয়। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা এঁদের চাওয়া-না-চাওয়ার উপরে নির্ভর করছে। এঁরা আপনাদের পাওয়া ষোল আনা বুঝে নিতে বদ্ধপরিকর না হলে ভারতের বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন কিছুতেই সাধিত হতে পারে না। কিন্তু এঁদের জীবনে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই যদি না জন্মে তবে কিসের জন্যে এরা পাওয়ার দাবী জগতের সম্মুখে পেশ করতে যাবেন?’ (প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা: ৫) এই অচলায়তন ভাঙার জন্য কমরেড মুজাফফর শিক্ষিত সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। শুধু ভারতের স্বাধীনতা নয়, নিজেদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা, অধিকারের কথা জানান দেয়ার আবশ্যকতার অনিবার্যতাও অনুভব করেন তিনি। এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘তাদের বোঝাতে হবে, তাদের শ্রমের ধনে তাদের ভোগের অধিকার ষোল আনা রয়েছে, সে অধিকার ত্যাগ করে তারা পৌরুষের পরিচয় না দিয়ে কাপুরুষতার পরিচয়ই দিচ্ছে, মনুষ্যত্ব হতে তারা বহু দূরে সরে পড়েছে। এককথায়, জীবনে খাওয়া-পরার তীব্র আকাঙ্ক্ষা যতদিন না আমাদের দেশের কৃষক ও শ্রমিকগণের প্রাণে জাগবে ততদিন আমাদের অবস্থার পরিবর্তন কিছুতেই হবে না। পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি না হলে পরিবর্তন কেনই বা হবে। (প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা: ৫-৬) সংগত কথা বলেছেন কমরেড মুজাফফর। সাধারণ জনগোষ্ঠী-সমাজের প্রান্তজনেরা তথা কৃষক, শ্রমিক ও সর্বহারারা যদি নিজেদের পরিবর্তিত করে জীবনমুখী করে না তোলে, জেগে না ওঠে, তাহলে কে তাদের জাগাবে? কে জোগাবে নিরন্নর জন্য অন্ন। এ জন্য মুখ্যত পুরহিততন্ত্রকে দায়ী করেছেন কমরেড মুজফ্ফর আহমদ। তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছেন, ‘কপট সাধু-সন্ন্যাসী ও মোল্লা-মৌলবী প্রভৃতির দুষ্ট আওতা হতে ভারতের কৃষক ও শ্রমিক জীবনকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে না পারলে আমাদের উদ্ধারের আশা একেবারেই নেই। এ অবস্থায় আমাদের শুধু যে দাসত্বের ঘৃণিত জীবন বহন করতে হবে, তা নয়, আমাদের জীবন দিনকে দিন যেমন ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, তাতে আমরা ধরাবক্ষ হতে একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যাব।’ (প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা: ৫-৬) ৯৮ বছর আগে বাঙালি জাতির জীবনবিমুখতার কারণে সন্ধানে তিনি যেমন মোল্লাতন্ত্রকে দায়ী করেছিলেন। আজকের আর্থসামাজিক প্রগতির প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রেও একই কথা সমভাবে প্রযোজ্য।
এ অঞ্চলের ধর্ম প্রভাবিত সংস্কারাচ্ছন্নতায় সৃষ্ট স্থবিরতার কারণেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বেঁচে থাকবার আবশ্যকীয় পাথেয় সন্ধানের প্রয়োজন বোধ করেনি। দাসত্বের দেয়ালে অবরুদ্ধ হয়ে অবনত থেকেও তারা দেয়াল ভাঙার স্বপ্নে হতে পারেনি বিভোর। অধঃপতিত হতে হতে হারিয়েছে অস্তিত্ব, তবু উঠে দাঁড়াতে শেখেনি, উঠে দাঁড়াতে পারেনি। এ সমাজের এই নির্মম বাস্তবতা নজরে পড়েছিল মহান দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের পর্যবেক্ষণে। এ বিষয়ে তাঁরা লিখেছেন, ‘ঐ সব লক্ষ লক্ষ শ্রমপরায়ণ পিতৃতান্ত্রিক ও নিরীহ সামাজিক সংগঠনগুলি অসংগঠিত হয়ে চূর্ণ চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, ডুবছে দুর্দশার এক সমুদ্রে, সে সংগঠনের সদস্যদের কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে যুগপৎ তাদের প্রাচীন সভ্যতা ও জীবিকার্জনের বংশানুক্রমিক উপায়’ দেখতে এটা মানবিক অনুভূমির কাছে যতই পীড়াদায়ক হোক না কেন, এ কথা যেন না ভুলি যে এইসব শান্ত সরল (idyllic) গ্রাম গোষ্ঠীগুলি যতই নিরীহ মনে হোক, প্রাচ্য স্বৈরাচারের তারাই ভিত্তি হয়ে এসেছে চিরকাল, মনুষ্য মানসকে তারাই যথাসম্ভব ক্ষুদ্রতম পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে, তাকে বানিয়েছে কুসংস্কারের অবাধ ক্রীড়নক, তাকে করেছে চিরাচরিত নিয়মের ক্রীতদাস, হরণ করেছে তার সমস্ত কিছু মহিমা ও ঐতিহাসিক কর্মদ্যোতনা।...এই নিষ্ক্রিয় ধরনের অস্তিত্ব থেকে অন্যদিকে তার পাল্টা হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে বন্য লক্ষ্যহীন এক অপরিসীম ধ্বংসশক্তি এবং হত্যা ব্যাপারটিকেই হিন্দুস্থানে পরিণত করেছে এক ধর্মীয় প্রথায়। যেন না ভুলি যে ছোট ছোট এই সব গোষ্ঠী ছিল জাতিভেদ প্রথা ও কৃতদাসত্ব দ্বারা কলুষিত, অবস্থার প্রভুরূপে মানুষকে উন্নত না করে তাকে করেছে বাহিরের অবস্থার অধীন, স্বয়ং-বিকশিত একটি সমাজ ব্যবস্থাকে তারা পরিণত করেছে অপরিবর্তমান নিয়তিরূপে এবং এইভাবে আমদানি করেছে প্রাকৃতিক পশুবৎ পূজা, প্রকৃতির প্রভু যে মানুষ তাকে হনুমানদেবরূপী বানর এবং শবলাদেবীরূপী গরুও আর্চনায় ভূলুণ্ঠিত করে অধঃপতনের প্রমাণ দিয়েছে। (মার্কস, এঙ্গেলস। উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে। পৃষ্ঠা: ৪০-৪১) একদিকে ধর্মান্ধতা, অন্যদিকে জীবনবিমুখ নিস্পৃহতার কারণে শেষ পর্যন্ত এ অঞ্চলের লোকেরা শ্রেণিগত চেতনার আলোকে আলোকিত হতে পারেনি। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটিয়ে ব্রিটেনের রানি শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করলেও শোষণের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়নি। তদুপরি এর পর থেকে সীমিত পরিসরের শিক্ষা বিস্তারের ফলে যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল, তা-ও সুপথে বিকশিত হয়নি, হতে দেওয়া হয়নি। এ পর্যায় হতে অনুসৃত সরকারের ‘ডিভাইড অ্যান্ড রুল’ পলিসির মাধ্যমে দুটি প্রধান ধর্মগোষ্ঠীকে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়। অতঃপর এরা ক্রমশ একে অপরের শত্রু হয়ে শক্তি সঞ্চয় করলেও জীবনমুখী লড়াইয়ের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে পারেনি। একদিকে বেপথে শক্তি নাশ করেছে, অন্যদিকে অচলায়তন ভেঙে নিজেদের দাঁড় করাতে পারেনি। নিস্পৃহ জীবনের চোরাবৃত্তে নিজেদেরকে নিজেরাই করেছে নিক্ষেপ। করে রেখেছে অবরুদ্ধ।
এহেন প্রকৃতির এই নিস্পৃহ জাতিকে জাগিয়ে তোলার এক মহাব্রত নিয়ে দৃশ্যপটে ধূমকেতুর মতো উপস্থিত হয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি একাধারে ছিলেন কবি, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, গল্পকার, নাট্যকার, অভিনেতা, ঔপন্যাসিক ও সংগীতজ্ঞ। সাহিত্য ও শিল্পের সব ধারাতেই তিনি ছিলেন জাতীয় স্বাধীনতা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে সোচ্চার। এ জন্য তাঁকে জেল জুলুমসহ নানামুখী নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছিল। এ কথা স্বীকৃত যে তিনিই প্রথম বাঙালি, যিনি ব্রিটিশ অধীনতা থেকে ভারতকে স্বাধীন করার জন্য স্বরাজের পরিবর্তে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন ১৯২২ সালে। এর পূর্বে বিহারের উর্দু কবি হসরত মোহানী (১৮৭৫-১৯৫১) ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের আহমেদাবাদ অধিবেশনে এ ধরনের আহ্বান জানিয়েছিলেন ১৯২১ সালে। এ বিষয়ে ‘ধূমকেত’-তে কবি লিখেছিলেন, ‘সর্বপ্রথম, ‘ধূমকেতু’ ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ টরাজ বুঝি না, কেননা, ও-কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম ক’রে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-রক্ষা, শাসনভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে তাতে কোনো বিদেশীর মোড়লী করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী ক’রে দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করছেন, তাঁদেরকে পাততাড়ি গুটিয়ে, বোচকা পুঁটলি বেধে সাগর পারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তাঁরা শুনবেন না। আমাদেরও এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকুকে দূর করতে হবে’। (নজরুলের প্রবন্ধ সমগ্র। পৃষ্ঠা: ১১১) কমরেড মুজফফরের মতো কবি নজরুল ইসলামও এ জাতিকে জাগিয়ে তোলার তাগিদ অনুভব করেছেন প্রবলভাবে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে নিজ নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন। বলেছেন, ‘তোমার লাঙল তোমাকে শিক্ষা দিচ্ছে তোমার প্রাপ্য বুঝে নিতে। এস ভাই কৃষক, এস ভাই শ্রমিক, আমরা সকলে মিলে আজ আমাদের জন্মগত অধিকারের দাবি করি। আমরা শুধু তৃপ্ত নিশ্বাস আর চোখের জল ফেলতে দুনিয়াতে আসিনি। আমরাও অন্নবস্ত্র চাই, সুখ-শান্তি চাই। আর মনে রেখো ভারতের কল্যাণের অকল্যাণের জন্য আমরাই সর্ব্বতোভাবে দায়ী। কালকে যারা আসবে তারা যেন আমাদের নামে দায়িত্বহীনতা ও কর্তব্যে অবহেলার ভীষণ অভিযোগ না আনতে পারে। (লাঙল। ৪ঠা মার্চ, ১৯২৬)
প্রকাশ থাকে যে ভারতের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যখন সীমিত পরিসরের স্বায়ত্বশাসন তথা স্বরাজ নিয়ে সরব, ব্রিটিশদের উচ্ছিষ্ট আস্বাদনের জন্য উদগ্রীব। তখন ২৩ বছরের তরুণ কবি নজরুলই সমস্ত ভীরুতা ও সমঝোতা নাকচ করে দিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সোচ্চার হয়ে ওঠেন। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি বাঙালিদের জেগে ওঠার আবশ্যকতা অনুভব করেন প্রবলভাবে। বাঙালি জাতির ইতিহাস ঐতিহ্যের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি জাতীয়তাবাদী চেতনার তাৎপর্য তুলে ধরেন, সে নিরিখেই বাঙালিদের স্বাধীনসত্তা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে বৈদেশিক শাসক ও দেশীয় শোষকদের বিতাড়নের কথা বলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি (৮১) বছর পূর্বে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ২৯ বছর পূর্বে) ‘বাঙালির বাংলা’ প্রবন্ধে লেখেন, ‘বাঙালি যেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলতে পারবে, ‘বাঙালির বাংলা’, সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে। সেদিন একা বাঙালিই ভারতকে স্বাধীন করতে পারবে। বাঙালির মতো জ্ঞান-শক্তি ও প্রেম-শক্তি (ব্রেন সেন্টার ও হার্ট-সেন্টার) এশিয়ায় কেন, বুঝি পৃথিবীতে কোনো জাতির নেই।’ (নজরুলের প্রবন্ধ সমগ্র। পৃষ্ঠা: ২২৮) একই প্রবন্ধে তিনি বাঙালি জাতির জীবন বিমুখতা ও নিস্পৃহতার বিষয়টিও তুলে ধরেন। এ বিষয়ে বলেন, ‘কিন্তু কর্ম-শক্তি একেবারে নেই বলেই তাদের এই দিব্যশক্তি তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাদের কর্ম-বিমুখতা, জড়ত্ব, মৃত্যুভয়, আলস্য, তন্দ্রা, নিদ্রা, ব্যবসা-বাণিজ্যে অনিচ্ছার কারণ। তারা তামসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে চেতনা-শক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে।’ (নজরুলের প্রবন্ধ সমগ্র। পৃষ্ঠা: ২২৮) বাংলার অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্য সম্ভারে বিমোহিত কবি অতঃপর বলেন, ‘বাংলার জল নিত্য প্রাচুর্যে ও শুদ্ধতায় পূর্ণ। বাংলার মাটি নিত্য-উর্বর। এই মাটিতে নিত্য সোনা ফলে। এত ধান আর কোনো দেশে ফলে না। পাট শুধু একা বাংলার। পৃথিবীর আর কোনো দেশে পাট উৎপন্ন হয় না। এত ফুল, এত পাখি, এত গান, এত সুর, এত কুঞ্জ, এত ছায়া, এত মায়া আর কোথাও নেই। এত আনন্দ, এত হুল্লোড়, আত্মীয়তাবোধ পৃথিবীর আর কোথাও নেই।’ (নজরুলের প্রবন্ধ সমগ্র। পৃষ্ঠা: ২২৯) অতঃপর একই প্রবন্ধে বাঙালিদের দুর্বলতাগুলো তুলে ধরে; পুরো জাতিকে জাগিয়ে তোলার প্রত্যয়ে বলেন, ‘বাঙালি সৈনিক হতে পারলো না। ক্ষাত্র শক্তিকে অবহেলা করলো বলে তার এই দুর্গতি’ তার অভিশপ্তের জীবন। তার মাঠের ধান পাট রবি ফসল তার সোনা তামা লোহা কয়লা, তার সর্ব ঐশ্বর্য বিদেশী দস্যু বাটপাড়ি করে ডাকাতি করে নিয়ে যায়, সে বসে বসে দেখে। বলতে পারে না ‘এ আমাদের ভগবানের দান, এ আমাদের মাতৃ-ঐশ্বর্য ! খবরদার, যে রাক্ষস একে গ্রাস করতে আসবে, যে দস্যু এ ঐশ্বর্য স্পর্শ করবে, তাকে ‘প্রহারেণ ধনঞ্জয়’ দিয়ে বিনাশ করবো, সংহার করবো।’ (নজরুলের প্রবন্ধ সমগ্র। পৃষ্ঠা: ২২৯) পরিশেষে তিনি জাতীয় মুক্তি ও শোষণের অবসান ঘটাবার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘বাঙালিকে, বাঙালির ছেলেমেয়েকে ছেলেবেলা থেকে শুধু এই এক মন্ত্র শেখাও :
‘এই পবিত্র বাংলাদেশ
বাঙালির’ আমাদের।
দিয়া ‘প্রহারেণ ধনঞ্জয়’
তাড়াব আমরা, করি না ভয়
যত পরদেশী দস্যু ডাকাত
‘রামা’দের ‘গামা’দের।’
বাংলা বাঙালির হোক! বাংলার জয় হোক! বাঙালির জয় হোক।’ (নবযুগ ৩রা বৈশাখ, ১৩৪৯)। (নজরুলের প্রবন্ধ সমগ্র। ২৩০) এ প্রবন্ধটি কবি নজরুল তাঁর সম্পাদিত ‘নবযুগ’ পত্রিকায় লিখেছিলেন আজ থেকে ৮০ বছর আগে। ৩ বৈশাখ, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে। তার তিন মাস পর থেকেই কবি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অতঃপর সম্বিৎহারা হয়ে বাকি জীবন পার করেন। কবি শুধু এ প্রবন্ধেই নয়, সৃষ্টিশীল সময়ের পুরোটাই জাতিগত জাগরণের জন্য খরচা করেছেন। লিখেছেন ব্রিটিশবিরোধী কবিতা; ‘আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।’ এ কবিতার জন্য পরিশেষে তাঁকে কারারুদ্ধও হতে হয়। তিনি বর্ণবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বীজ উৎপাটন করে একটি মানবিক সমাজ বিনির্মাণের ডাক দিয়েছেন। বলেছেন, ‘গাহি সাম্যের গান’/ যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান/যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান’। দেশমাতৃকাকে দখলমুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে লিখেছেন, ‘দুর্মদ দুরন্ত যৌবন চঞ্চল/ ছাড়িয়া আসুক মা-র স্নেহ অঞ্চল/বীর সন্তানদল করুক সুশোভিত মাতৃ-অঙ্ক।’ তাঁর মতো করে কেউ এভাবে বাঙালি জাতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য সাহিত্যাঙ্গনে সোচ্চার ছিলেন না। যে কারণে ব্রিটিশ সরকার তাঁর ৫টি কাব্যগ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করেছিল। সে সময় ব্রিটিশদের আর কোনো উপনিবেশে এমনটা ঘটেনি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বাঁধনহারা কবির প্রসঙ্গে বলেছিলেন, কাজী নজরুল বাংলা সাহিত্যে বসন্ত এনেছে।
রাজনৈতিক অঙ্গনেও কবি সমানভাবে সোচ্চার ছিলেন। ‘শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়’র পক্ষ থেকে উত্থাপন করেছিলেন কৃষক শ্রমিকের বেঁচে থাকার দাবি-দাওয়া। এ সমস্ত সংগঠনের তাৎক্ষণিক সাফল্য দৃষ্টিগ্রাহ্য না হলেও এ ধরনের তৎপরতা ও উদ্যোগের মাধ্যমেই ভবিষ্যৎ আন্দোলন সংগ্রামের বীজ রোপিত হয়েছিল। বাংলায় গড়ে উঠেছিল একটি সচেতন সংগ্রামী সমাজ। এ সংগঠনের উদ্দেশ্য, কর্মনীতি-সংকল্প ও দাবির বিষয়ে বলা হয়েছিল: ‘১। আধুনিক কলকারখানা, খনি, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ট্রামওয়ে, ষ্টীমার প্রভৃতি সাধারণের হিতকারী জিনিস, লাভের জন্য ব্যবহৃত না হইয়া দেশের উপকারের জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং এতৎ সংক্রান্ত কর্ম্মীগণের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সম্পত্তি রূপে পরিচালিত হইবে।
২। ভূমির চরম স্বত্ব আত্ম-অভাব-পূরণ-ক্ষম স্বায়ত্ত-শাসন-বিশিষ্ট পল্লীতন্ত্রের উপর বর্ত্তিবে’ এই পল্লী-তন্ত্রে ভদ্র শূদ্র সকল শ্রেণীর শ্রমজীবীর হাতে থাকিবে।’ (লাঙল। ১৬ ডিসেম্বর, ১৯২৫। পৃষ্ঠা: ১১-১৩)
শ্রমিক শ্রেণির দাবির বিষয়ে বলা হয়েছিল, ‘(ক)জীবন-যাত্রার পক্ষে যথোপযুক্ত মজুরির একটা নিম্নতম হার আইনের দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া। (খ) প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ শ্রমিকের পক্ষে সপ্তাহে সাড়ে পাঁচ দিন খাটুনি চরম বলিয়া আইন করা; নারী এবং অল্প বয়স্ক ছেলেপিলের জন্য বিশেষ সর্ত্ত নির্দ্ধারণ করা। (গ) শ্রমিকগণের আবাস, কাজের সর্ত্ত, চিকিৎসার বন্দোবস্ত প্রভৃতি বিষয়ে কতকগুলি দাবী মালিকগণকে আইন দ্বারা করিয়া পূরণ করানো। (ঘ) অসুখ, বিসুখ, দুর্ঘটনা, বেকার অবস্থা এবং বৃদ্ধ অবস্থায় শ্রমিকগণকে রক্ষা করিবার জন্য আইন প্রণয়ন। (ঙ) সমস্ত বড় কলকারখানায় লাভের ভাগে শ্রমিকগণকে অধিকারী করা। (চ) মালিকগণের খরচায় শ্রমজীবীগণের বাধ্যতামূলক শিক্ষা। (ছ) কলকারখানার নিকট হইতে বেশ্যালয়, নেশার দোকান উঠাইয়া দেওয়া। (জ) শ্রমিকগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা। (ঝ) শ্রমিক-সঙ্ঘগুলিকে আইনত মানিয়া লওয়া এবং শ্রমিকদের দাবী পূরণের জন্য ধর্ম্মঘট করিবার অধিকার স্বীকার করা।’ (লাঙল। ১৬ ডিসেম্বর, ১৯২৫। পৃষ্ঠা: ১১-১৩) কৃষক সমাজের দাবির বিষয়ে বলা হয়েছিল, ‘(ক) ভূমি-কর সম্বন্ধে একটা ঊর্দ্ধতম হার বাঁধিয়া দেওয়া এবং বাকি খাজনার সুদ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সুদের হারের সহিত সমান নির্দ্ধারণ করা; (খ) (i) জমিতে কায়েমী স্বত্ব (i i) উচ্ছেদ নিরোধ (i i i) অন্যায় এবং বে-আইনি বাজে আদায় বন্ধ (i v) স্বেচ্ছায় বিনা সেলামিতে হস্তান্তর করার অধিকার (v) গাছ কাটা, কুয়ো খোঁড়া, পুকুর কাটা, পাকা বাড়ী করার বিনা সেলামিতে অধিকার। (গ) জল-করে মাছ ধরিবার নির্দ্ধারিত সর্ত্ত। (ঘ) মহাজনের সুদের চরম হার নির্দ্ধারণ। (ঙ) কো-অপারেটিভ কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপনের দ্বারা কৃষককে ঋণদান এবং মহাজন ও লোভী ব্যবসাদারগণের হাত হইতে কৃষককে উদ্ধার। (চ) চাষের জন্য যন্ত্রপাতি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের মারফৎ কৃষকের নিকট বিক্রয় অথবা ব্যবহারের জন্য ভাড়া দেওয়া। মূল্য অথবা ভাড়ার টাকা কিস্তীবন্দী হিসাবে অল্প অল্প করিয়া লওয়ার বন্দোবস্ত। (জ) পাটের চাষের কৃষকের উপযুক্ত লাভের বন্দোবস্ত।’(লাঙল। ১৬ ডিসেম্বর, ১৯২৫। পৃষ্ঠা: ১১-১৩)
নিস্পৃহ বাঙালি জাতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য কবির সার্বিক লড়াই সর্বমহলে প্রসংশিত হয়েছিল ব্যাপক পরিসরে। ১৫ ডিসেম্বর, ১৯২৯ সালে কোলকাতার এলবার্ট হলে (এখনকার কফি হাউস) জাতির পক্ষ থেকে কবি নজরুল ইসলামকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর ভাষণের একাংশে বলেন, ‘ফরাসি বিপ্লবের সময়কার কথা, একখানি বই পড়িতেছিলাম। তাহাতে লেখা দেখিলাম, সে সময় প্রত্যেক মানুষ অতি-মানুষে পরিণত হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস, নজরুল ইসলামের কবিতা পাঠে আমাদের ভাবী বংশধরেরা এক একটি অতি-মানুষে পরিণত হইবে।’ (ইসলাম। নজরুল জীবনী। পৃষ্ঠা: ৪০২) আদতেও নজরুলের সৃষ্টিশীলতার প্রভাবে বাঙালিরা অতি মানবে পরিণত হয়েছিল। পরিতাপের বিষয় পরবর্তী সময়ে বাঙালিরা আর ঐক্যবদ্ধ থাকেনি। বিভাজিত হয়েছে। একই ভাষাভাষী, সংস্কৃতি ও ভূখণ্ডের অধিবাসী হয়েও তারা ধর্মীয় পরিচিতি পরিহার করে কবি নজরুলের অভিপ্রেত একক জাতিসত্তা গড়ে তুলতে পারেনি। শোষিত শ্রেণিরা সমবেত হয়ে গাইতে পারেনি শেকল ভাঙার গান। থামাতে পারেনি উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল।
অতঃপর হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাগিয়ে তোলেন জাতিকে, বিভাজিত বাঙালিদের গরিষ্ঠ অংশকে নিয়ে গঠন করেন কবি নজরুলের অভিপ্রেত বাঙালি জাতির জাতিসত্তা। বিনির্মাণ করেন বাঙালির বাঙলা। তাঁর নেতৃত্বে বাঙালির ক্ষাত্রশক্তি জাগরিত হয়, বিতাড়িত হয় নব্য শোষক রামা ও গামারা। প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙালি জাতির স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। অতঃপর জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে কবি কাজী নজরুল ইসলামের অবদান স্বীকৃত হয়। কবিকে বাংলাদেশে আনয়নের পর বঙ্গবন্ধু বলেন, ‘কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন বাঙালি জাতির জাতিসত্তা বিনির্মাণের ঐতিহাসিক রূপকার।’
সহায়ক গ্রন্থ-তথ্য উৎস
১. ইসলাম, রফিকুল। ২০১৫। নজরুল জীবনী। ঢাকা। কবি নজরুল ইনস্টিটিউট
২. নজরুলের প্রবন্ধ সমগ্র। ২০১৬। সম্পাদনা: মুহম্মদ নূরুল হুদা-রশিদুন্ নবী। ঢাকা। কবি নজরুল ইনস্টিটিউট
৩. মার্কস্, এঙ্গেলস্। ঔপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে। ১৯৭১। মস্কো। প্রগতি প্রকাশন
৪. রহমান, শেখ মুজিবুর। ২০১৭। কারাগারের রোজনামচা। ঢাকা। বাংলা একাডেমি
৫. লাঙল। ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪ জানুয়ারি, ১৯২৬
৬. হান্টার, ডব্লিউ। ২০০২। পল্লী বাংলার ইতিহাস। অনূদিত: ওসমান গনি। ঢাকা। দিব্যপ্রকাশ







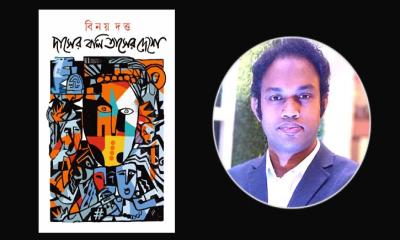
































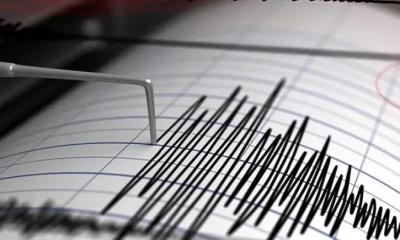







-20250327140635.jpeg)



