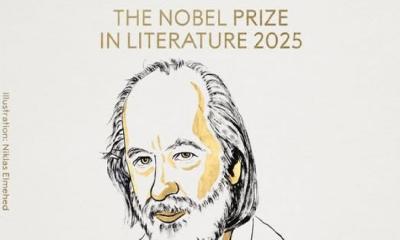এখনকার সরকারি দলিল-দস্তাবেজ দেখলে, আজ থেকে একশো বছর পরে, যে-কেউ বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে কাশ্মিরি জাতিটাই বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গি উগ্র গোষ্ঠীমাত্র, ফিলিস্তিনিরা জন্মসূত্রে সন্ত্রাসী হয়েই জন্ম নেয় এবং তারা মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ইসরায়েলের অস্তিত্ব পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার জন্য হেন অপকর্ম নাই যা করতে পিছপা হয়, তামিলরা সন্ত্রাসী জাতি, তারা শ্রীলঙ্কাকে এশিয়ার সুইজারল্যান্ড হয়ে উঠতে দেয়নি, মুসলিমরা পৃথিবীর সবচেয়ে সহিংস ধর্মীয় জাতি যারা শুধুমাত্র ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে আমেরিকার টুইন টাওয়ার গুঁড়িয়ে দেয়। আর পৃথিবীতে একমাত্র সভ্য ও মানবীয় জাতি হচ্ছে মার্কিনীরা, ফলে তাদের হাতেই ন্যস্ত পৃথিবীর অভিভাবকত্ব, এবং এটি অত্যন্ত ন্যায্য ও ইতিহাসসম্মত।
ইতিহাসের দর্শন কাকে বলে? তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কী? ইতিহাসের দর্শনকে কত শ্রেণীতে ভাগ করা যায়? ইতিহাসের দর্শন চর্চার উপকারিতা কী? ‘ইতিহাসের দর্শন’ ধারণাটির উৎপত্তির ইতিহাস ও কারণ কী?— ইত্যাকার প্রশ্ন অ্যাকাডেমিশিয়ানদের জন্য তোলা থাকুক। আমাদের মতো ঘা খাওয়া মানুষরা শুধু দেখে যে ইতিহাস কীভাবে ক্ষমতাশালীদের স্বার্থে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত ও একপেশে হতে থাকে। ঘা খাওয়া মানুষ বলতে সবসময়ই ঘা খাওয়া মানুষ। বর্তমানেরও। ইতিহাসেরও। আরো অনেকদিন পর্যন্ত ভবিষ্যতেও যে ঘা খেয়ে যেতে হবে, তা এখন ভবিষ্যদ্বক্তা না হয়েও বলা যায়। বর্তমানের ঘা না হয় সহ্য করে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু ইতিহাসের ঘা যখন জন্মান্তরের পাপের ফল হিসাবে নিরন্তর খেয়ে যেতে হয়, তখন তা জীবনকে শুধু অসহ্যই করে তোলে না, বরং হীনম্মন্যতার অতলেও ডুবিয়ে রাখে। এই ইতিহাসের ঘা আসে ইতিহাসের হাত ধরেই, ইতিহাস-রচয়িতার হাত ধরেই, ইতিহাসের দর্শনের হাত ধরেই।
তাই ঘা খাওয়া মানুষদের শুধু ইতিহাসকে প্রশ্ন করলেই চলে না, ইতিহাসের দর্শনকেও তার প্রশ্নবিদ্ধ করতে হয়। যে দর্শন ইতিহাসের অলক্ষ্য নির্মাতা, সেই দর্শনকে প্রতি-আক্রমণ না করলে ইতিহাসের আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। তাই আমরা শুধু কী বলা হয়েছে সেটাকেই প্রশ্ন করি না, কে বলেছে কোন শ্রেণীর দৃাষ্টভঙ্গি থেকে বলেছে, কার পক্ষে ও কার বিপক্ষে বলেছে, কোন দর্শনের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে বলেছে—সেই প্রশ্নগুলিও সামনে তুলে আনি।
এইখানেই মার্কসবাদীদের সততা। কারণ মার্কসবাদী নিজেই মার্কসবাদী নামে পরিচিত ইতিহাস-বীক্ষাকেও প্রশ্ন করতে পারে, প্রশ্নের সঠিক উত্তর না পেলে তাকে ভেঙে আবার নতুন বীক্ষার সন্ধানও করতে পারে। এই কাজ করতে গিয়ে বারবার প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে নিজের দর্শন, এমনকি বিলুপ্তির মুখোমুখি হতে পারে দর্শন। কিন্তু তাতে ভীত হয় না মার্কসবাদী। কারণ তার প্রয়োজন, মার্কসবাদ নয়—সত্য।
একটা কথা প্রথমেই পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো যে আমাদের দেশে মার্কসের চিন্তাধারা বলতে এমন একগুচ্ছ ভাবনাপুঞ্জকে বোঝানো হয়ে থাকে যাকে স্ট্যালিনের আমলে ‘মার্কসবাদ’ আখ্যা দিয়ে প্রচার করা হয়েছিল পৃথিবীব্যাপী। সেই অর্থে এটিকে কেউ কেউ ‘অফিসিয়াল মার্কসবাদ’ বলে অভিহিত করে থাকেন। বাংলাদেশে যারা মার্কসবাদের পক্ষে কথা বলেছেন, তাঁরা মূলত এই অফিসিয়াল মার্কসবাদের পক্ষেই বলেছেন। যারা বিরোধিতা করেছেন এবং করছেন, তারাও এই অফিসিয়াল মার্কসবাদেরই বিরোধিতা করছেন। অফিসিয়াল মার্কসবাদে কার্ল মার্কসকে প্রায় ধর্মপ্রণেতার জায়গাতে বসানো হয়েছিল। কিন্তু মার্কস নিজে যেমনটি চেয়েছিলেন, অর্থাৎ তাঁকে যারা বৈজ্ঞানিক হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত, তাঁরা মনে করে যে—সমাজের বিবর্তন বিষয়ে মার্কস যে কাজ করে গেছেন, তার সঙ্গে তুলনীয় চিন্তা তাঁর জীবদ্দশাতে তো বটেই, তাঁর পরবর্তীকালেও আর কেউ করতে পারেননি। তবে তার অর্থ এই নয় যে তাঁর প্রতিটি কথাকে অভ্রান্ত বলে ধরে নিতে হবে। এবং মার্কসের অনুগামী বলে যারা নিজেদের ঘোষণা করেননি, এমন অনেক চিন্তকদের কাজ থেকেও গ্রহণ করার মতো অনেক কিছুই রয়েছে।
‘অফিসিয়াল মার্কসবাদে’ মার্কসবাদের অন্যতম ভিত্তি হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছিল ‘ঐতিহাসিক বস্তুবাদ’কে। সেখানে বলা হয়েছে, একটি উৎপাদন ব্যবস্থা তার পূর্ববর্তী উৎপাদন ব্যবস্থাকে শুধুমাত্র অনুসরণই করে না; বরং পূর্ববর্তী উৎপাদন ব্যবস্থা তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপই পরবর্তী উৎপাদন ব্যবস্থার জন্ম দেয়। অর্থাৎ ‘উৎপাদন ব্যবস্থা’ ধারণাটির মধ্যেই কিছু নিয়মের ধারণা নিহিত রয়েছে। যে নিয়ম অনুসারে কোনো একটি উৎপাদন ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটে, তা বিকশিত হয়, তারপরে তা অবনমনের পথে নামে, সবশেষে অবলুপ্ত হয়ে পরবর্তী উৎপাদন ব্যবস্থার জন্ম দেয়। উৎপাদন ব্যবস্থার যে ধাপগুলির কথা অফিসিয়াল মার্কসবাদের ‘ঐতিহাসিক বস্তুবাদ’ জোরেশোরে বলেছে সেগুলি হচ্ছে— ১. আদিম সাম্যবাদী কৌমসমাজ ২. দাসসমাজ ৩. সামন্ততন্ত্র ৪. পুঁজিবাদ ও ৫. সমাজতন্ত্র। ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত ‘ডায়ালেকটিক্যাল অ্যান্ড হিস্টোরিক্যাল মেটেরিয়ালিজম’ গ্রন্থে স্ট্যালিন এই তত্ত্বকে গ্রন্থিত করেন। একই কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় বুখারিনের ‘হিস্টোরিক্যাল মেটেরিয়ালিজম’ গ্রন্থে। পরবর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির পক্ষ থেকে, এমনকি চীনের পার্টির পক্ষ থেকেও, যত প্রচারমূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, সবগুলিতেই এই ধারণাটিকে এমন বিতর্কহীনভাবে গ্রহণ করা হয়েছে যে, যার ফলে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের এই স্ট্যালিনীয় প্রকল্পটিকে মার্কসীয় ইতিহাসচিন্তার অন্যতম মূলস্তম্ভ হিসাবে সারা পৃথিবীতেই গ্রহণ করা হয়।
গত শতকের ষাটের দশকে কয়েকজন মার্কসবাদী তাত্ত্বিক এই তত্ত্বের দিকে প্রশ্নের আঙুল উঁচিয়েছিলেন বটে, তবে তাঁদের চিন্তা সক্রিয় মার্কসবাদীদের তখন তেমন একটা প্রভাবিত করতে পারেনি। এখন, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে, মার্কসের মূল ও অসম্পাদিত রচনাবলী হাতে পাওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে যে, যে অপরিবর্তনীয় পরম্পরার কথা স্ট্যালিনের বইতে পাওয়া যায়, ঐ প্রকার অমোঘতা-সমন্বিত কোনো দাবি মার্কসের লেখায় আদৌ পাওয়া যায় না।
যাবে কেমন করে? আদতে তো পৃথিবীর কোথাও এমন থাকবন্দি হয়ে উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশ ঘটেনি।
বাস্তবত বিশ্লেষণ করার আগে মার্কসের লেখা থেকে কিছুটা সাক্ষ্য সংগ্রহ করে নেওয়া যাক। মার্কস তাঁর সবিশেষ প্রসিদ্ধ ‘প্রিফেস টু দি কন্ট্রিবিউশানস টু দি ক্রিটিক অফ পলিটিক্যাল ইকনমি’ গ্রন্থে সমাজ পরিবর্তনে ধাপের ধারণার কথাটি লিখেছেন। সেই সঙ্গে এই বইতে পাওয়া যাচ্ছে দাসসমাজ, সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদ— এই তিনটি ধাপের অস্তিত্বের স্বীকৃতি। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে এই গ্রন্থে তিনি এক ‘এশিয়াটিক’ সমাজের উল্লেখ করেছেন, যা স্ট্যালিন ও ‘ঐতিহাসিক বস্তুবাদ’পন্থীরা বেমালুম চেপে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপের ইতিহাস প্রসঙ্গে মার্কস যে পরম্পরার কথা বলেছেন, তা তিনি ভারতবর্ষ, চীনসহ পশ্চিম ইউরোপের বাইরের কোনো দেশ সম্পর্কে প্রয়োগ করেননি। এইসব দেশ সম্পর্কে মার্কস সম্পূর্ণ ভিন্ন এক উৎপাদন ব্যবস্থার কথা ভেবেছিলেন, যাকে বলা যেতে পারে ‘এশিয়াটিক মোড অফ প্রোডাকশন’। আবার মার্কস যখন কেল্ট, স্লাভ প্রভৃতি নৃ-গোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনা করেন, তখন তাদেরও যে বিশেষ ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল তা উল্লেখ করতে ভোলেন না। অনেক বিশ্লেষক তো মনে করছেন যে মার্কসকে অনুসরণ করে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সমাজের জন্য পৃথক পৃথক উৎপাদন ব্যবস্থার কথা ভাবা খুবই সম্ভব। পশ্চিম ইউরোপেই সামন্ততন্ত্রের অবনমন এবং পুঁজিবাদের বিকাশের মধ্যে ছিল কয়েকশ’ বছরের ব্যবধান। সেই কারণে কোনো কোনো মার্কসবাদী গবেষক এখন পশ্চিম ইউরোপের ইতিহাসের মধ্যেই সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদের অন্তর্বর্তীকালের জন্য একটি উৎপাদন ব্যবস্থার নাম প্রস্তাব করেছেন, যা উদ্ভূত হয়েছিল সামন্ততন্ত্রের সাথে বাণিজ্যের সংমিশ্রণে।
মার্কস তাঁর ইতিহাসের পরম্পরার গবেষণাক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন পশ্চিম ইউরোপকে। তাঁর বই ‘গ্রুন্ডরিখ’ এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি চিন্তা ধারণ করে রেখেছে। মনোযোগের সাথে ‘গ্রুন্ডরিখ’ বিশ্লেষণ করলে অন্তত ৪টি পরম্পরার সন্ধান পাওয়া যায়। ১. আদিম সাম্যবাদী কৌম সমাজ— দাস সমাজ। ২. আদিম সাম্যবাদী কৌম সমাজ— এশিয়াটিক উৎপাদন ব্যবস্থা। ৩. আদিম সাম্যবাদী কৌম সমাজ— সামন্ততন্ত্র ও এশিয়াটিক উৎপাদন ব্যবস্থার মিশ্রণ। ৪. আদিম সাম্যবাদী কৌম সমাজ— সামন্ততন্ত্র— পুঁজিবাদ।
প্রথম পরম্পরাটি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে দেখা গিয়েছিল। লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে এই পথ পরবর্তীকালের সামন্ততন্ত্রে গিয়ে পৌঁছায়নি। দ্বিতীয় পরম্পরাটি ভারতবর্ষ ও চীনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তৃতীয় পরম্পরাটি রাশিয়াসহ বিভিন্ন স্লাভ ভূখণ্ডে দেখা গেছে। চতুর্থটি প্রযোজ্য শুধুমাত্র পশ্চিম ইউরোপের ক্ষেত্রে। প্রথম তিনটি পরম্পরার কোনোটিই আপন গতিতে পুঁজিবাদে গিয়ে উপনীত হয়নি। পুঁজিবাদে উপনীত হয়েছে শুধু চতুর্থটি। কিন্তু সেটি আবার দাস সমাজব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যায়নি। অর্থাৎ মার্কস-এর গবেষণা অনুযায়ী দাস ব্যবস্থা থেকে ইউরোপে পুঁজিবাদের উদ্ভব ঘটেনি। ঘটেছিল জার্মান কৌম সমাজ থেকে।
শেষে শরণ নিতে হয় রবীন্দ্রনাথেরই— ‘সকল দেশের ইতিহাস যে একই পথে চলবে, এই ভুল ধারণা না ভাঙলেই নয়।’
২.
মানুষের জীবন, ফলত মানুষের সমাজ, কোনোদিনই একমাত্রিক নয়। তার অর্থ হচ্ছে ইতিহাসও কখনো একমাত্রিক হতে পারে না। অথচ যে কোনো ইতিহাসের দর্শনই একমাত্রিক। সেই একমাত্রিক দর্শন নিয়ে ইতিহাসের দিকে তাকানো মানে অন্ধের হস্তিদর্শন। ধর্মতন্ত্রবাদীরা মনে করে যে মানুষ যা কিছু করে, তা তার আনুষ্ঠানিক ধর্মমতকে কেন্দ্রে স্থাপন করেই করে। সেই অনুসারে ধর্মে ধর্মে বিভেদটাই সত্য। আবার ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ইতিহাস বলে যে বিভেদ নয় সমন্বয়টাই সত্য। দুই পক্ষই নিজ নিজ বক্তব্যের সমর্থনে ইতিহাস থেকে কিছু উদাহরণ তো টেনে আনতেই পারে। ধরা যাক এই উপমহাদেশে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের কথা। ইংরেজরা যাকে বলে ‘সিপাহি বিদ্রোহ’। ইসলামপন্থী ইতিহাসে তাকে দাবি করা হয় ‘মুসলমানদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের যুদ্ধ’ বলে। আর কার্ল মার্কস তাকে আখ্যা দিয়েছেন ‘প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ’।
সেই যুদ্ধ বা বিদ্রোহকালেরই একটি ঘটনা। ১৮৫৭ সালের ৭ জুন। এলাহাবাদের চেল এলাকার ছোট একটি গ্রাম বারওয়ারি। সেখানে ইংরেজ রেলকর্মীদের একটি ছাউনি ছিল। রেলপথ বসানোর কাজে তারা সেখানে অবস্থান করছিল। স্থানীয় জমিদার নায়েব বখ্শের নেতৃত্বে স্থানীয় অধিবাসীরা আক্রমণ চালাল ইংরেজদের ওপর। জীবন বাঁচাতে ইংরেজরা আশ্রয় নিল উঁচু পানির ট্যাংকের ওপর। নিচে তাদের ঘেরাও করে রইল বিদ্রোহী গ্রামবাসী। অনেক কাকুতি-মিনতি করায় ভারতবর্ষীয় দরদি প্রাণ শেষ পর্যন্ত গলে গেল। তখন রফা হলো যে ইংরেজদের হত্যা না করে ছেড়ে দেওয়া হবে। বিনিময়ে তারা বিদ্রোহীদের কিছু টাকা-পয়সা দেবে। এই পর্যন্ত ঠিকই ছিল। কিন্তু যেই টাকা ভাগ-বাঁটোয়ারার প্রসঙ্গ উঠল, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহীদের নিজেদের মধ্যে কোন্দল। তখন ন্যায়সম্মত বণ্টনের দায়িত্ব বর্তাল সেই ইংরেজদের হাতেই। ইংরেজরা বলল যে হিন্দু এবং মুসলমানরা দুই আলাদা সারিতে বসুক। আলাদা সারি তৈরি হলে দেখা গেল হিন্দু আর মুসলমানদের সংখ্যা সমান সমান। তখন ইংরেজরা হিন্দু আর মুসলমান দুই দলকেই আলাদা আলাদা ভাবে পাঁচশো টাকা করে দিয়ে দিল। তারপরে সেই ইংরেজদের নামে ধন্য ধন্য। এতবড় জটিলতার কত সুন্দর আর সুষ্ঠু সমাধান করে দিল ইংরেজরা। তখন হিন্দুও বলে মুসলমানও বলে— সত্যিকারের রাজার জাত থাকলে তা হচ্ছে ইংরেজরা!
এই ঘটনা কার পক্ষে যায়। বিদ্রোহে যোগ দেওয়া, ইংরেজদের ঘেরাও করা, তাদের তাড়িয়ে পানির ট্যাংকের ওপরে তোলা পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান একসাথে। এখানে ধর্মসমন্বয়ের অসামান্য কাণ্ডটি ঘটে গেছে। এই পর্যন্তের ঘটনা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ইতিহাসের দর্শনের সাথে একেবারে টাঁয়ে টাঁয়ে মিলে যায়। কিন্তু যেই বখরার প্রসঙ্গ সামনে এলো, সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ফিরে পেল তার হিন্দুসত্তা, আর মুসলমান ফিরে পেল তার মুসলমানসত্তা। পুরো ঘটনাটিকে নিজের পক্ষে কাজে লাগানোর কোনো ফর্মুলা না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী এবং ধর্মাশ্রয়ী— দুই ইতিহাসেরই আকর গ্রন্থ থেকেই উধাও করে রাখা হয়েছিল ঘটনাটির বিবরণ।
নাড়কেলবেড়ের জঙ্গনায়ক তীতুমীর তাঁর বাঁশের কেল্লার জন্য ইতিহাসে খ্যাত। ইসলামি ধর্মতন্ত্রপন্থী ইতিহাস তীতুমীরকে ওহাবী, ফরায়েজী, ধর্মসংস্কারক এবং ইসলাম পুনরুদ্ধারের যোদ্ধা বলেই প্রচার করতে চায়। এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহও নেই যে ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের গৌরব পুনরুদ্ধারও তীতুমীরের কার্যক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তিনি নিজে ও তাঁর সহযোদ্ধারা হিন্দুদের থেকে আলাদা পোশাক পরতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা দাঁড়ি রাখতেন, মাথা কামাতেন, আর হিন্দুরা যেভাবে ধুতি পরে সেভাবে না পরে, অর্থাৎ ধুতির কাছা না দিয়ে তহবন্দের (আজকের ভাষায় লুঙ্গির) মতো করে পরতেন। হিন্দুরা, বিশেষ করে হিন্দু জমিদার এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা তীতুমীর এবং তাঁর সঙ্গীদের বলত ‘নেড়ে আর দেঁড়ে’। মুসলমানদের কাছা খুলে ধুতি পরার কারণ হিসাবে তারা প্রচার করেছিল যে তীতুমীর বাহিনীর সবার অণ্ডকোষ বড় হয়ে ঝুলে গেছে ষণ্ডের মতো, তাই তারা ধুতিতে কাছা দেয় না। তীতুমীরও যে এসব হিন্দু সাম্প্রদায়িক জমিদারদের নানাভাবে উচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন সে তথ্যও আমাদের জানা আছে। কিন্তু যে তথ্যটি এই দুই ধর্মতন্ত্রী ইতিহাস এবং ইংরেজ সরকারি ইতিহাস চাপা দিয়ে রাখতে চায়, সেটি হচ্ছে ইংরেজ আমলে এদেশে সত্যিকার অর্থে একমাত্র সফল আন্দোলন ‘নীল বিদ্রোহে’ তীতুমীর বাহিনীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের ঘটনা। কোনো ইতিহাসেই স্পষ্টভাবে তুলে আনা হয় না এই তথ্যটি যে তীতুমীর নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষকের সংগ্রামে জঙ্গি-নেতৃত্ব দেবার জন্য বিশেষ এক বাহিনীই গড়ে তুলেছিলেন, যার নাম ছিল ‘হামকল বাহিনী’। নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষকের সকল জঙ্গি আক্রমণে হামকল বাহিনীর সদস্যরা থাকতেন সম্মুখ সারিতে। ১৮৬০ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই নীলকরদের বিরুদ্ধে অনেকগুলি জঙ্গি হামলা সংঘটিত হয়। ছোটলাটের কাছে তার একটা তালিকা পাঠায় ইংরেজ অফিসাররা। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল— ১. মোল্লাহাটি কুঠি আক্রমণ করে সহকারী ম্যানেজার ক্যাম্পবেল সাহেবকে প্রচণ্ড প্রহারের পর মৃত মনে করে মাঠের মধ্যে ফেলে যাওয়া, ২. খাজুরার কুঠি লুট করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া, ৩. লোকনাথপুরের কুঠি আক্রমণ, লুট ও অগ্নিসংযোগ, ৪. চাঁদপুরের গোলদার কুঠির নীলের গোলা আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া, ৫. খাড়াগোদা কুঠির পরিশোধিত নীল চিত্রা নদীতে ফেলে দেওয়া, ৬. ঘোলদারি কুঠির সমস্ত গোলা ভেঙে ফেলা ও কর্মচারিদের বেদম প্রহার করে কুঠি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া, ৭. শানঘর, মধুয়া এবং সিন্দুরিয়া নীলকুঠির কনসার্নের সকল নীলের আবাদ নষ্ট করে ফেলা, ৮. নাটুদহ ও রানাঘাটে সকল ইউরোপীয় কুঠিমালিক ও তাদের পরিবারের লোকদের অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।
নীল বিদ্রোহের সময় গ্রামে গ্রামে কৃষক বাহিনী যে প্রতিরোধ ব্যূহ রচনা করে, তার পেছনে ছিল হামকল বাহিনীর সুদক্ষ রণকৌশল। ১৮৬০ সালের ‘ইন্ডিয়ান ফিল্ড’ নামক মাসিক পত্রিকায় পাদ্রী ফ্রিদরিক ফন লেখেন— ‘কৃষক যোদ্ধাগণ ছয়টি বিভিন্ন কোম্পানিতে নিজেদের সজ্জিত করেছিল। ১ম কোম্পানি তীরন্দাজদের নিয়ে গঠিত হয়। ২য় কোম্পানি গঠিত হয় প্রাচীনকালের ডেভিডের মতো ফিঙা দ্বারা গোলক নিক্ষেপকারীদের নিয়ে। ৩য় কোম্পানি ইটওয়ালাদের নিয়ে, যারা আমার বাড়ি থেকে ইট কুড়িয়ে নিয়ে গেছে। ৪র্থ কোম্পানি বেলওয়ালাদের নিয়ে গঠিত। এদের কাজ হলো নীলকরদের লাঠিয়াল বাহিনীর মস্তক লক্ষ করে শক্ত কাঁচা বেল ছুঁড়ে মারা। ৫ম কোম্পানি গঠিত হয় থালা-ওয়ালাদের নিয়ে। তারা ভাত খাওয়ার কাঁসা ও পিতলের থালাগুলি আনুভূমিকভাবে চালাতে পারে। এতে যে শত্রুনিধনের কাজটি উত্তম রূপেই করা সম্ভব হয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ৬ষ্ঠ কোম্পানি গঠিত ছিল রোলা-ওয়ালাদের নিয়ে। খুব উত্তমরূপে পোড়ানো খণ্ড অথবা অখণ্ড মাটির বাসন ও পাত্র ছিল এদের অস্ত্র। এই কোম্পানির সৈনিক ছিল প্রধানত স্ত্রীলোকগণ। বাঙালি রমণীরা এই অস্ত্র উত্তমরূপেই ব্যবহার করতে জানে। নীলকরদের একদল লাঠিয়াল যখন একটি গ্রাম আক্রমণ করেছিল তখন সেই গ্রামের রমণীবৃন্দ এই অস্ত্রদ্বারা তাদের অভ্যর্থনা জানায়। ফলে লাঠিয়ালরা রক্তাক্ত দেহে ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে বাধ্য হয়।
এ ছাড়া আরো একটি কোম্পানি তৈরি হয় যারা লাঠি চালাতে জানে তাদের নিয়ে। তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কোম্পানি বল্লমধারী বাহিনী নিয়ে গঠিত ছিল। একজন বল্লমধারী ১০০ জন লাঠিধারীকে পরাজিত করতে পারে।’ (দেখুন: নীলবিদ্রোহের নানাকথা। মুহম্মদ ইউসুফ হোসেন। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা। নভেম্বর ১৯৯০। পৃষ্ঠা নম্বর— ৫৩)। এই লাঠিধারী এবং বল্লমধারী বিদ্রোহীরা ছিলেন মূলত তীতুমীরের হামকল বাহিনীর সদস্য। চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে হামকল বাহিনীর দুইটি প্রধান ঘাঁটি ছিল হুলিয়ামারী ও চাঁন্দুরে গ্রামে। হুলিয়ামারীর যে অঞ্চলে হামকল বাহিনীর ব্যারাক ছিল সেই অংশ পরবর্তী সময়ে তীতুদহ নামে অভিহিত হয়। হামকল বাহিনীর অনেক সদস্যই ছদ্মবেশে নীলকুঠিতে ছোট ছোট পদে চাকুরি করতেন। তারাই গোপনে কুঠির যাবতীয় সংবাদ নিজেদের ব্যারাকে পাঠাতেন। সিন্দুরিয়া কুঠির কুঠিয়াল উইলিয়াম শেরিফের প্রধান সহিস রইস খাঁ ছিলেন এমনই একজন ছদ্মবেশী হামকল যোদ্ধা। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল সৈয়দ সদরুদ্দিন। চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে সবচেয়ে বড় যে নীলজঙ্গ সংঘটিত হয়, যেখানে তিরিশ হাজার কৃষক যোদ্ধা ঐ জেলার সকল নীলকরের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে সকল নীলকুঠি উচ্ছেদ করতে সক্ষম হয়েছিল, সেই যুদ্ধে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন ছিলেন এই হামকল যোদ্ধা সৈয়দ সদরউদ্দিন ওরফে রইস খাঁ। (দেখুন: প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা নম্বর ৭১)।
এক নীল বিদ্রোহের ইতিহাসই না কত ভাবে লেখা হয়েছে! হিন্দু ধর্মতন্ত্রী ইতিহাসবিদের লেখায় সৈয়দ সদরউদ্দিনের কোনো চিহ্নই নেই। সেখানে চুয়াডাঙ্গা নীলজঙ্গের তিন প্রধান কুশীলব হচ্ছেন তিন হিন্দু জমিদার— সাধুহাটির জমিদার মথুরানাথ আচার্য, পথহাটির দিকপতি মজুমদার, এবং চণ্ডীপুরের জমিদার শ্রীহরি রায়। সত্যি বটে, এই তিন জমিদার একপর্যায়ে কৃষকদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু তা তারা নীলচাষ উচ্ছেদের জন্য দাঁড়াননি। তারা জড়িত হয়েছিলেন ইংরেজদের তাড়িয়ে নিজেরা লাভবান হওয়ার জন্য। কেননা তারা নিজেরাও ছিলেন নীলকুঠির মালিক এবং নীলের ব্যবসায়ী।
নীল বিদ্রোহের ইতিহাসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে কিছু কিছু তথ্য ইচ্ছাকৃতভাবে চেপে যাওয়ার প্রবণতা। এটি বিশেষভাবে করা হয়েছে আমাদের বাংলার কয়েকজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির বিতর্কিত কার্যকলাপ আড়াল করে রাখার জন্য। তাদের মধ্যে রয়েছেন মহান রাজা রামমোহন রায়(!), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ তদানীন্তন বাংলার গৌরব প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, এবং প্রসন্ননাথ ঠাকুর। উপরোক্ত তিনজনই ছিলেন নীলকুঠির মালিক এবং নীলের ব্যবসায়ী। এই তিন মহান বাঙালি ছাড়াও নীলকর হিসাবে ইংরেজদের মতোই কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন ঘোড়াখালির জমিদার অবনীমোহন বসু, নলডাঙ্হার রাজা প্রমথভূষণ, পোতাহাটির আশুতোষ গাঙ্গুলী, ইংরেজদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কালীপ্রসন্ন সরকার, শ্রীকোল বোয়ালিয়ার হরিচরণ সাহা এবং আরো অনেক বাঙালি এবং দেশীয় নীল কুঠিয়াল। রামমোহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম আরো বিশেষভাবে নীলচাষের সাথে যুক্ত এই কারণে যে তাঁদের ওকালতি ছাড়া বাংলায় নীলচাষের কোনো আইনগত ভিত্তিই তৈরি হতো না। এই আইনগত ভিত্তির কারণেই লক্ষ লক্ষ কৃষক অবর্ণনীয় দুর্দশার শিকার হয়েছিলেন, হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন, হাজার হাজার রমণী সম্ভ্রম হারিয়েছিলেন। তিন বাঙালি মহাপুরুষের ওকালতি সফল না হলে ইতিহাস অন্য রকম হতে পারত।
ব্যাপারটি খোলাসা করে বলা যাক। এই দেশে নীল ব্যবসার প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে জমিদার যে শুধু জমির ওপরেই কর্তৃত্ব করত তা-ই নয়, প্রজার জানমাল, ইজ্জত-সম্ভ্রমেরও মালিক ছিল তারাই। নীলকররা টাকার বিনিময়ে জমি কিনে নীল চাষ করতে পারলেও রায়তকে তো জোর করে কাজে লাগাতে পারত না। কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন অনুসারে রায়তের ওপর এক জমিদার ছাড়া আর কারো হুকুম চলবে না। তাছাড়া জমিদার টাকার বিনিময়ে জমি বা তালুক পত্তনি দিতে পারত না। তখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর নীলকরদের কাছে জমিদারদের তালুক পত্তনি দেওয়ার অধিকার চাইলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে। তিনি প্রচার করলেন— ‘আলস্য অনভিজ্ঞতা ও ঋণের জন্য দেশীয় জমিদারগণ জমি পত্তনি দিতে উদগ্রীব। কারণ ইহাতে তাঁহারা জমিদারি চালাইবার দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন এবং জমি পত্তনিদারের মতো একটি নিশ্চিত আয়ের সাহায্যে রাজধানীতে কিংবা কোনো একটি বড় শহরে বসবাস করিতে পারেন।’
ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে নীলকররা যে স্মারকলিপি পেশ করেন তাতে রামমোহন রায় লিখেছিলেন— ‘নীলকর সাহেবদের সম্পর্কে আমি আমার মত সবিনয়ে উল্লেখ করছি। বাংলা বিহার উড়িষ্যার বিভিন্ন জেলা আমি পরিদর্শন করেছি। আমি দেখেছি, নীলচাষের নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান অন্যান্য অঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের তুলনায় উন্নততর।... নীলকরদের দ্বারা হয়তো সামান্য কিছুটা ক্ষতি সাধিত হতে পারে, কিন্তু সরকারি বা বেসরকারি যত ইউরোপীয় এখানে আছে তাদের যে কোনো অংশের তুলনায় নীলকর সাহেবগণ এদেশীয় সাধারণ মানুষের কল্যাণই বেশি করছেন।’ (দেখুন: পার্লামেন্টারি পেপারস। ভলিউম ৩৬। পৃষ্ঠা ২৭)।
প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর লিখলেন— ‘আমি দেখেছি, নীলের চাষ এদেশের মানুষের পক্ষে সবিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছে। জমিদারগণের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষকদেরও উন্নতি যথেষ্ট সাধিত হয়েছে। যে অঞ্চলে নীলের চাষ নেই সেই অঞ্চলের তুলনায় নীলচাষ এলাকাভুক্ত অঞ্চলের মানুষ অধিকতর সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছে।... আমি কেবল জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করে একথা বলছি না। প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই আমি একথা পেশ করছি।’ (দেখুন: প্রাগুক্ত)।
ইংরেজদের আস্থাভাজন রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর গংদের ওকালতি বৃথা যায়নি। ১৮১৯ সালে পাশ করা হলো ‘অষ্টম আইন’। এই আইনে জমিদারদের নিজেদের জমিদারির ভিতরে পত্তনি তালুক দেবার অধিকার প্রদান করা হলো। ১৮৩৩ সালে বাংলাদেশে ইংরেজদের জমি ও জমিদারি ক্রয় করার অধিকার প্রদান করে ‘চতুর্থ আইন’ পাশ করা হলো। এই আইনের সুবিধা নিয়ে বেঙ্গল ইন্ডিগো কোম্পানি এক বছরের মধ্যেই কেবল চুয়াডাঙ্গা, ঝিনেদা, রানাঘাট এবং যশোর অঞ্চলেই ৫৯৪টি গ্রামের জমিদারি কিনে নিয়ে ব্যাপকভাবে নীলচাষ করতে শুরু করে। কেবল নীলচাষ বা নীলব্যবসাতে অংশগ্রহণের কারণেই নয়, বরং বাংলায় সর্বনাশা নীলচাষের আইনগত ভিত্তি গড়ে দেবার কাজে রামমোহনের মতো মহাপুরুষরা যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, তা জনসমক্ষে তুলে ধরতে তাঁর সবচেয়ে বড় ভক্তও অস্বস্তি বোধ করেন। তাই বেশিরভাগ ইতিহাসে অকথিত থেকে যায় এইসব তথ্য। ইতিহাসের এই দর্শনকে কী নামে অভিহিত করা যায়?
৩.
সবশেষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রসঙ্গ।
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কি একটি জনযুদ্ধ ছিল? বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যে দুই নিয়মিত বা ট্রাডিশনাল সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ ছিল না, তা মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জীবিত সকলেরই জানা। এতটাই জানা যে তার সপক্ষে কোনো প্রমাণ বা দলিল উপস্থিত করারই প্রয়োজন নেই। যে যে বৈশিষ্টের কারণে একটি যুদ্ধ জনগণের যুদ্ধ হয়ে ওঠে, সেগুলি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মতো আর কোনো যুদ্ধেই এত প্রকটভাবে উপস্থিত ছিল না। ফলে প্রকৃত একটি জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হওয়ায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, এবং বাংলাদেশের মানুষ এক বিরল গৌরবের অধিকারী। কিন্তু ইতিহাস নির্মাণের ছলচাতুরি এই গৌরব থেকে ভবিষ্যতের বাঙালিকে বঞ্চিত করে ফেলবে এমন আশংকা এখনই দেখা যাচ্ছে। আর এই ইতিহাস নিজের ইচ্ছামতো লেখার চাতুরি শুরু হয়েছে, অন্য কোনো সরকারের সময় নয়, খোদ শেখ মুজিব সরকারের সময় থেকেই।
১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের মূল্যায়ণের জন্য যে পদক-তালিকা ঘোষিত হয়, তাতে সুস্পষ্টভাবেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে জনযুদ্ধের সম্মান থেকে সরিয়ে দেবার প্রক্রিয়া সূচিত হয়েছে। চারটি খেতাব দেওয়া হয় মোট মাত্র ৬৭৬ জনকে। তারমধ্যে আবার ৫২০টিই দেওয়া হলো সশস্ত্র বাহিনীতে নাম লেখানো মুক্তিযোদ্ধাকে। সর্বোচ্চ পদক ‘বীরশ্রেষ্ঠ’ দেওয়া হয়েছে ৭ জনকে। তাঁরা প্রত্যেকেই নিয়মিত সামরিক বাহিনীর সদস্য। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদক ‘বীরউত্তম’ দেওয়া হয়েছে ৬৮ জনকে। তাদের মধ্যে ২ জন ছাড়া বাকি ৬৬ জনই সামরিক বাহিনীর লোক। তৃতীয় পদক ‘বীরবিক্রম’ দেওয়া হয়েছে ১৭৫ জনকে। তাদের মধ্যে ১৪৫ জনই সামরিক বাহিনীর। সর্বশেষ পদক ‘বীরপ্রতীক’। এইক্ষেত্রে ৪২৬টি পদকের মধ্যে ৩০৫টিই সামরিক বাহিনীর মদস্যদের দেওয়া হয়েছে। লক্ষ লক্ষ নারী মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, নির্যাতিতা হয়েছেন, জীবন দিয়েছেন। কিন্তু নারীদের ভাগ্যে পদক জুটেছে মাত্র ২টি। আর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ পদক পেয়েছেন মাত্র ৫ জন।
একশো বছর পরে সরকারি ইতিহাস অনুযায়ী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দুই সামরিক বাহিনীর যুদ্ধ হিসাবে পরিগণিত হতে পারে, সেই আশংকা এখনই দেখা যাচ্ছে। আর আছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কথা। ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী ইতিহাস লেখকরা একদিন যে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে আমাদের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি উপহার হিসাবে লিখবেন, এ ব্যাপারে প্রস্তুতি এখন থেকেই চলছে। মুম্বাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি থেকে এরইমধ্যে বেশকিছু সিনেমা রিলিজ হয়েছে, যেগুলোতে বলা হচ্ছে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা হচ্ছে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের বাই প্রোডাক্ট। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর পক্ষে অংশ নেওয়া একজন সামরিক অফিসার বলছেন— মিছেই ভারতের সাংবাদিকরা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের কথা ফলাও করে লিখছে। আমাদের ভারতীয় বাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করা ছাড়া যুদ্ধে আর তেমন কিছুই করেনি বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা। (দেখুন: অসীম রায়ের আত্মজীবনী ‘জীবন-মৃত্যু’র দ্বিতীয় খণ্ড)।
৪.
এত আলাপের সারমর্ম— ইতিহাসের সম্ভবত কোনো দর্শন থাকে না; দর্শন থাকে ইতিহাস রচয়িতাদের।