বাংলাদেশিরা যেখানেই যায় না কেন, সেখানে নিজস্ব সংস্কৃতির পুনর্নির্মাণ করে কেন? ধরুন, তারা পয়লা বৈশাখ করবে, বাংলা ভাষার চলচ্চিত্র উৎসব করবে, দেশি খাবার কিংবা পোশাকের দোকান দেবে। এটা অবশ্য কেবল বাংলাদেশি নয়, চীনা, ভারতীয়, রুশ সবার বেলাতেই সত্যি। অর্থাৎ মানুষ তার নিজের সংস্কৃতি ছাড়তে চায় না। পৃথিবীর যে কোনাতেই সে যাক না কেন, নিজের সঙ্গে সে বয়ে নিয়ে যায় তার বেড়ে ওঠার অনুষঙ্গ, বয়ে নিয়ে যায় স্মৃতির ঝাঁপি। এরপর নতুন জায়গায় সে নির্মাণ করে নেয় নিজস্ব বলয়, নিজের এক টুকরো স্বস্তির আশ্রম। অতটুকুই হয়ে ওঠে তার একান্ত আপন।
আপন ও পরের এই সমীকরণ মেলাতে মেলাতে সকালে যখন বাসস্টেশনের দিকে যাচ্ছি, তখন পথে পড়ে আছে ম্যাপলপাতা। পঞ্চম দিন সকালের সূচিতে রেখেছি ‘দুনিয়াটাই পরিবার’, অর্থাৎ ‘দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ফ্যামিলি’ প্রামাণ্যচিত্রটি। বিশ্বনন্দিত ভারতের মায়েস্ত্রো চলচ্চিত্র নির্মাতা আনন্দ পটবর্ধনের ছবি। স্কশিয়াব্যাংক থিয়েটারে ছবি শুরুর আগে আনন্দ এসে দর্শক সারিতে বসলেন। ছবিটি শুরু হয় আনন্দের মা ও বাবার প্রাতর্ভ্রমণ দিয়ে। তাদের স্মৃতিচারণা দিয়ে শুরু হলেও, ছবি শুরুর একটু পরই টের পাওয়া যায় আনন্দের এই ছবি শুদ্ধ ব্যক্তিগত পরিবারের বয়ান রচনা নয়, নিজের পরিবারের সদস্যদের ভেতর দিয়ে পরিভ্রমণ করতে চেয়েছেন ভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রদায়িক গলি ও তাকে মেলাতে চেয়েছেন বর্তমানের সরণিতে। ১৮৫৭ সালে যে হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে লড়াই করেছে, তারাই কেমন করে একে অপরের প্রতিপক্ষ হয়ে গেল? আনন্দ এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন নিজের পরিবারের মানুষ ও ইতিহাসের পাতা থেকে।
আনন্দের বাবা বালু ছাড়া পরিবারের প্রায় সবাই যুক্ত ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে। বালুর এক ভাই রাউ ছিলেন অহিংস আন্দোলনের কর্মী, এ জন্য তাকে কারাভোগ করতে হয়েছে। আরেক ভাই অচ্যুত ছিলেন বিপ্লবী আন্দোলনের সক্রিয়া কর্মী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতনের জন্য তিনি আন্ডারগ্রাউন্ডে কাজ করেছেন। আনন্দের মা নির্মলা, দেশভাগের আগে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে জন্মেছিলেন, পড়াশোনা করেছেন ভারতের অসাম্প্রদায়িক শিক্ষালয়, রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। নন্দলাল বসুর সরাসরি ছাত্রী নির্মলার আগ্রহ ছিল মৃৎশিল্পে। তিনি পরবর্তী সময়ে মৃৎশিল্প নিয়ে দেশের বাইরেও গিয়েছেন। গান্ধীর সঙ্গে পরিচয় ছিল নির্মলার। গান্ধীর কাছ থেকে তিনি একটি রুমাল চেয়ে নিয়েছিলেন স্মৃতিস্মারক হিসেবে। কিন্তু পরে সেটি তিনি হারিয়ে ফেলেন। ছেলের বানানো প্রামাণ্যচিত্রে সেই স্বর্ণালি স্মৃতির ডালা মেলে ধরেন নির্মলা। ছবিতে আরও উল্লেখ করা হয় ভুলে যাওয়া পাকিস্তানি রাজনৈতিক নেতা আল্লাহ বক্সের কথা, তিনিও ভারত ভাগের বিপক্ষে ছিলেন।
ভারত ভাগের ধারণাকে পছন্দ করেননি গান্ধীও, এ কথা তিনি বলেছিলেন নেহরুকে। কিন্তু নেহরু তখন দাঙ্গার বীভৎস ছবি মেলে ধরেন গান্ধীর সামনে। গান্ধী অসহায়ের মতো নেহরুকে তখন বলেছিলেন, তুমিই তো এখন কংগ্রেস, যা ভালো মনে করো...। অথচ এই গান্ধীকে মরতে হয়েছে আরএসএসের সদস্য, হিন্দু জাতীয়তাবাদী নাথুরাম গডসের গুলিতে। গান্ধী ভারত ভাগ হোক চাননি, কিন্তু নেহরুকে বাধাও দেননি। আনন্দ পটবর্ধন আত্মস্বীকৃত গান্ধীবাদী। গান্ধীর অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। অধুনা ভারতে বিজেপি নাগরিকত্ব আইন পাসের নামে মুসলমান ও অমুসলমানের ভেতর যে মেরুকরণ করেছে, সেটারও সমালোচনা করেন আনন্দ। পরিচালক এই ছবি শেষ করেন তার মা ও বাবার মৃত্যু দিয়ে। তিনি যেন বলতে চাইছেন—এই মানুষদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গান্ধীদর্শন, রবীন্দ্রদর্শন ও সর্বোপরি অসাম্প্রদায়িক চেতনাও বিদায় নিচ্ছে। আনন্দের বাবা-মায়ের মৃত্যুতে না যতটা, তার চেয়েও বেশি আমাদের হৃদয় আর্দ্র হয় ইতিহাসের এই প্রত্যক্ষদর্শীদের প্রস্থান ঘটছে একে একে, সেটা ভেবে।
ছবির সমাপ্তিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থিরচিত্র যুক্ত করেছেন পরিচালক। কিন্তু সমাপ্তি তালিকা শুরু হতেই প্রক্ষেপণ কক্ষ থেকে আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এতে কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ করেন আনন্দ। তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের বিষয়টি ডেকে বলেন। আমি ততক্ষণে তার কাছে গিয়ে আমার ভালো লাগার কথা জানালাম। উনি যেভাবে পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে দেশ ও রাষ্ট্রের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেলেন, যেভাবে বিশ্বনেতাদের ভাবনার দ্বন্দ্বকে পারিবারিক স্মৃতিচারণার ভেতর দিয়ে দর্শকের সামনে তুলে ধরলেন, তা এককথায় অতুলনীয়।
এর মাঝেই কয়েকজন ভারতীয় সাংবাদিক আনন্দকে অনেকটা অপহরণ করে স্কশিয়াব্যাংক থিয়েটারের লাউঞ্জে নিয়ে গেলেন। আমি চলে এলাম আর্টস্কেপ স্যান্ডবক্সের প্রেস লাউঞ্জে। এই প্রেস লাউঞ্জটা নিয়ে একটু করে বলতেই হবে। কান উৎসবের চেয়েও মন খোলা এদের। ওখানে ছিল শুধু কফি। আর এখানে ফলফলাদি, মাফিন, চকোলেট বার এবং নানা ধরনের উষ্ণ ও কোমল পানীয় রাখা, দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে আসা বিনোদন সাংবাদিক, চলচ্চিত্র সমালোচক ও লেখকদের জন্য। কাজ করতে করতে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ করতে যেন দৌড়ে আবার বাইরে যেতে না হয়, সে জন্য এই ব্যবস্থা।
এরপর সোয়া তিনটায় শুরু হবে ‘শ্যাডো অব ফায়ার’, জাপানের ছবি, পরিচালক শিনাইয়া সুকামোতো। হাতে সময় আছে। এই ফাঁকে বলে নিই, এই ছবিটি আমি দেখতে যাচ্ছি সাধারণ দর্শকদের সঙ্গে, অর্থাৎ পাবলিক স্ক্রিনিং। এসব শো টিকিট কেটে দেখতে হয়। তবে মিডিয়া অ্যাক্রেডিটেশন নিয়ে আসা ডেলিগেটরা দশটি পর্যন্ত পাবলিক স্ক্রিনিংয়ে উপস্থিত থাকতে পারেন, টিকিট কাটতে হয় না। আর প্রেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি স্ক্রিনিংগুলো তো সব বিনা মূল্যেই দেখা যায়, অগ্রিম বুকিংও দিতে হয় না কান উৎসবের মতো। যাহোক, মাঝে খাওয়াদাওয়া করে আবার পাঁচ মিনিটের হাঁটা স্কশিয়াব্যাংকের দিকে। হাঁটার সময় একটু সতর্ক থাকতে হয়, কারণ এরা প্রচুর কুকুর পছন্দ করে এবং এসব কুকুর, ভয় পাবেন না, কামড়ায় না, কিন্তু রাস্তাঘাটে যত্রতত্র মল ত্যাগ করে। ফ্রান্সে দেখেছিলাম কুকুরের মালিক হাতে পলিথিন নিয়ে ঘোরে, এখানে সেটি দেখিনি। কাজেই জুতো পরিষ্কার রাখতে চাইলে পা ফেলতে হবে সাবধানে।
জাপানি ছবি ‘শ্যাডো অব ফায়ার’ দেখতে হলে ঢুকলাম। শিনাইয়া সুকামোতোর এটি যুদ্ধ-ত্রয়ীর তৃতীয় চলচ্চিত্র। ট্রিলজির প্রথম ছবি ‘ফায়ার অন দ্য প্লেইন’ টিফে দেখানো হয় ২০১৪ সালে। এরপর ২০১৮ সালে এই টরন্টো উৎসবেই দেখানো হয় দ্বিতীয় ছবি ‘কিলিং’। আর ২০২৩ সালে এসে পূরণ হলো যুদ্ধ-ত্রয়ী। তিন ছবিতেই পরিচালক জাপানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পর যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল তা তুলে ধরেছেন।

‘শ্যাডো অব ফায়ারে’ এক বাচ্চা ছেলে আশ্রয় নেয় এক নারীর বিধ্বস্ত বাড়িতে। নারীটি বেঁচে থাকার জন্য তার শেষ সম্বল দেহ বিক্রি করে। একই ঘরে এসে জোটে এক সেনা। সেই ঘরে বালকটির সাময়িক শান্তি জুটলেও, তা স্থায়ী হয় না। যুদ্ধের ভয়াবহতা তাড়া করে ফেরা, মানসিক ভারসাম্য হারানো সেনার হাতে নির্যাতিত হয় ছেলেটি, পরে নারীটি অসুস্থ হলে তাকে ছেড়ে যেতে হয় সেই বাড়ি। আরেক চালচুলোহীন লোকের সঙ্গী হয়ে তাকে দেখতে হয় প্রতিশোধের ক্রোধ এবং শেষমেশ এক নির্দয় দোকানির হাতে মার খেয়েও ছেলেটি টিকে থাকে। এ যেন গোটা বিশ্বযুদ্ধকে একটি ছোট ছেলের জীবনযুদ্ধের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া। আংশিক চেম্বার ড্রামা, কিছুটা রোড মুভির ধাঁচে বানানো ছবিতে সুকামোতো চরিত্রদের চোখে নজর ফেলতে চেয়েছেন। চরিত্রগুলোর বিশেষ করে ছোট ছেলেটি আর ওই নারীর চোখে থাকা টলমলে জল দর্শকের নজর এড়ায় না। এই চোখ দিয়ে আসলে জাপানের যুদ্ধ-পরবর্তী বিহ্বল দৃষ্টিকেই বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন পরিচালক।
জাপানি ছবি শেষ হওয়ার দশ মিনিটের মাথায় শুরু হবে চীনা ছবি ‘হান্ড্রেড ইয়ার্ডস’। জু হাওফেং ও জু জুনফেং পরিচালিত ছবিটি দেখার জন্য দ্রুত হল পরিবর্তন করলাম। ভাগ্যিস স্কশিয়াব্যাংকের ভেতর হলগুলো কাছাকাছি, একই ফ্লোরে। তো মোটামুটি আগ্রহ নিয়ে দেখতে বসেছি। ছবি শুরু হলো। দেখি, একি, চীনা মার্শাল আর্ট মারকুটে ছবি। একটি মার্শাল আর্ট একাডেমির উত্তরাধিকার কে হবে, তা নিয়ে কাহিনি। আমি খুবই পছন্দ করি মার্শাল আর্ট মুভি। কিন্তু কেন যেন টিফে এই ধারার ছবি দেখতে মন চাইল না। পনেরো মিনিট পর বেরিয়ে পড়ি হল থেকে।
তারপর হাঁটতে হাঁটতে সেই উত্তরের রেল ধরে সেন্ট এনড্রু থেকে সেন্ট জর্জ স্টেশনে, সেখান থেকে পুবের রেলে চড়ে মেইন স্ট্রিট। তারপর বাসে করে যখন ব্রেনটন স্ট্রিটে নামলাম, তখন দেখি সেই আমাদের পাড়ার মুদিদোকানি। আমাকে দেখে কুশল বিনিময় করল। প্রথমে ওকে সুদান বা এর আশপাশের লোক বলে ভেবেছিলাম। নিশ্চিত হওয়ার জন্য এবার জিজ্ঞেস করে বসলাম—দেশ কোথায়? জানাল ওরা ইথিওপিয়ার লোক। আমার আন্দাজ ভুল হয়নি তাহলে। সুদানের প্রতিবেশী দেশ ইথিওপিয়া। ওদের কথাবার্তা আর চেহারা দেখে অনুমান করেছিলাম প্রথম দিন।
যাহোক, ওদের দোকান থেকে কিছু সদাইপাতি কিনে বাসায় ফিরছি আর ভাবছি, এই যে ছিমছাম গোছানো শহরে সময় কেটে যাচ্ছে, একদিকে সময় হারাচ্ছি, কিছু অর্থ, অপর দিকে স্মৃতির ভাঁড়ারে সামান্য কিছু নুড়িপাথর জমা হচ্ছে। মনে তখন ভেসে এলো আনন্দ পটবর্ধনের প্রামাণ্যচিত্রে ব্যবহার করা রবীন্দ্রসংগীতটি: “অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়।/ কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে প্রাণ করে ‘হায় হায়’।”







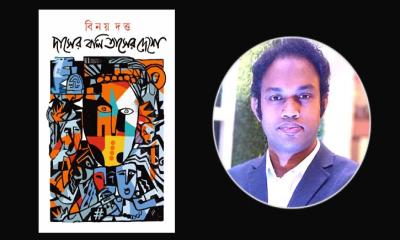






















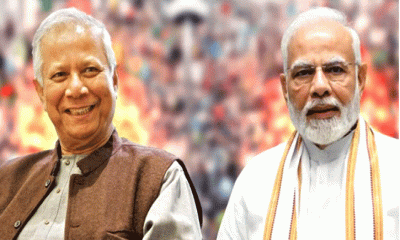







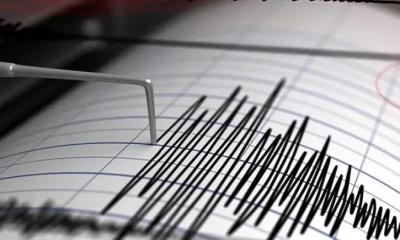










-20231109105053-20250402121817.jpg)
-20250329161133.jpeg)

