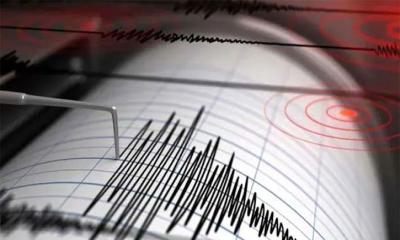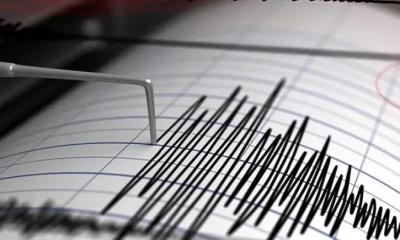ব্রিটিশদের বার্গার বা ফিশ অ্যান্ড চিপস খেয়ে যেমন পেট ভরে না, তেমনি মনও ভরে না। ভাত না হলে যে বাঙালির কী দশা হয়, তা বিদেশে কয়দিন থাকলেই টের পওয়া যায়। আমাদের ভাতবিষয়ক এই কাঙালিপনার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসের বাইরের একটি ভারতীয় ও একটি পাকিস্তানি রেস্তোরাঁ নির্ধারণ করে দেয়। সেখানেই মাছ, মাংস, সবজি ও ডালসহযোগে চলে দুপুরের ভোজন। একদিন বৃষ্টিজনিত কারণে বাইরে বের হওয়া সম্ভব না হওয়ায় লাঞ্চের ব্যবস্থা করা হয় ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে। সে মোতাবেক লাঞ্চ বিরতির সময় পেম্বারটন ভবন থেকে বেরিয়ে পড়ি খাবারের জন্য। ক্যান্টিনের অবস্থান খুব বেশি দূরে নয়। সামান্য পথ। দু-তিন মিনিটেই হেঁটে যাওয়া যায়। কিন্তু ঝামেলা বাধায় বৃষ্টি আর ঝড়-বাতাস। বিরামহীন সর্দির মতো আকাশ থেকে ঝরতে থাকা জল, যা এ দেশের এক বিরক্তিকর উপাদান। কখন যে আকাশ ভালো থাকবে, আর কখন বিগড়ে যাবে, তা আগে থেকে ঠাওর করা মুশকিল।
এমনিতে প্রবল ঠান্ডার কারণে শরীর ঢাকার জন্য ব্যাপক আয়োজন করতে হয়, তার ওপর বৃষ্টির ঝামেলা থাকলে বাড়তি প্রস্তুতিরও প্রয়োজন হয়। এই উটকো উৎপাতের হাত থেকে নাজাত পাওয়ার জন্য মামুলি ছাতাতে কোনো কাজ হয় না। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার প্রবল দাপটের কারণে ছাতা মাথায় নিয়ে চলাফেরা করাটা প্রায় অসম্ভব, এমনকি কোথাও দাঁড়িয়ে থাকাও মুশকিল। পাঁচ পাউন্ডের ছাতা ক্ষেত্রবিশেষে পাঁচ মিনিটও ব্যবহার করা যায় না। ছাতা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের ঝাপটা দৈত্যের মতো দৌড়ে এসে ছাতার হাড়হাড্ডি ভেঙে চুরমার করে দেয়। তারপরও লোকজন হয়তোবা কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক কারণে ছাতা নামের ওই অকার্যকর বৃষ্টি প্রতিরোধক ব্যবহার করে থাকে। এ ক্ষেত্রে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এক পাউন্ডের সস্তা ছাতা ব্যবহার করে এবং সাময়িক প্রয়োজন মিটিয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দেয়। যে কারণে বৃষ্টির সময় ডাস্টবিনে প্রচুর ছাতার দেখা মেলে। মাঝে মাঝে সিগারেট টানতে টানতে কৌতূহলবশত নতুন ঝকঝকে দু-একটা পরিত্যক্ত ছাতা নেড়েচেড়ে দেখি। এতে দেখা যায়, কোনো ছাতার হয়তো একটা শিক ভাঙা, কোনোটির হয়তো কাপড় ওল্টানো কিন্তু ব্যবহারযোগ্য, এত কম ক্ষতিগ্রস্ত ছাতা আমরা বাঙালিরা সাধারণত বাতিল করি না, মেরামত করে পুনর্বার ব্যবহার করি। কিন্তু এ দেশে ছাতা মেরামতের কোনো ব্যবস্থা নেই। অবশ্য যেকোনো মেরামতির কাজই এ দেশে অত্যন্ত ব্যয়বহুল।
যে কারণে ছাতা, জামা, জুতা বা প্যান্টজাতীয় ব্যবহার্য জিনিসপত্র মেরামত না করে ফেলে দেওয়াটাই আর্থিক দিক দিয়ে লাভজনক। আপাতত মেরামতির প্রসঙ্গ থাক। ছাতার প্রসঙ্গে আবার একটু আলোকপাত করি, আমাদের স্বভাবে পরোপকারের একটি প্রবৃত্তি সব সময় উঁকি দেয়, এ ক্ষেত্রে মাছের তেলে মাছ ভাজার মওকা পেলে তো কোনো কথাই নেই। সেই সুবাদেই মাঝে মাঝে পরিত্যক্ত ছাতার স্তূপ থেকে ভালো ছাতা বেছে নিয়ে তা উপহার প্রদান করতে খারাপ লাগে না, কখনো সহপাঠী আলম আরাকে, কখনো মাহবুবকে, কখনো আনোয়ারাকে বা রোকসানাকে নাই দামে কেনা ছাতা উপহার দিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলি। আজাদসহ আমরা কয়েকজন অবশ্য ছাতাটাতার ধার ধারি না, বঙ্গবাজার থেকে ক্রয়কৃত রেইনকোটে আপাদমস্তক ঢেকে চলাফেরা করি। এ ছাড়া অবশ্য গত্যন্তরও নেই। এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার যে দিকটি বেশ বিস্ময়ের সৃষ্টি করে তা হলো, একটানা বৃষ্টিতে ভিজলেও জ্বর, সর্দি কিংবা হাঁচির কোনো বালাই থাকে না। ফলে চলার পথে জলে অবগাহন করতে হলে খুব একটা দুশ্চিন্তায় পড়তে হয় না, খারাপও লাগে না। বর্ষণমুখর পরিবেশে হালকা জল-কাদা মাড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে ক্যান্টিনে এসে খাবার সংগ্রহের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকি।
এখানে বুফে সিস্টেমে খাবার পরিবেশিত হয়। নিয়ম অনুযায়ী কাউন্টারে মূল্য পরিশোধ করে নিজের খাবার নিজেকে সংগ্রহ করতে হয়। কোনো আব্দুল অথবা বয় বেয়ারার চল নেই। গাড়ির চালক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি সাহেবও একই লাইনে দাঁড়িয়ে একই তরিকায় খাদ্য সংগ্রহ করেন। এ দেশের সদাচারের এ দিকটি খুবই ভালো লাগে। কট্টর পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় বসবাস সত্ত্বেও এখানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে লোকজন সমানাধিকার ভোগ করে থাকেন। সামাজিকভাবেই বিষয়টি নিশ্চিত করা আছে। ভিআইপি, সিআইপি বা নেতাদের জন্য আলাদা খায়খাতিরের ব্যবস্থা নেই, সে ধরনের চলও নেই। আমাদের দেশের মতো পুরোনো জামানার সামন্ত ব্যবস্থা এবং ধ্যানধারণা একেবারে নেই বললেই চলে।
এখনো আমাদের সমাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভাইস চ্যান্সেলরের পাশে বসে তার গাড়িচালক ভোজন করবে, এমনটা কল্পনারও বাইরে। ওভাবে চিন্তা করাটাও মানসিক বিকৃতি হিসেবে ধিকৃত হয়ে থাকে। মনমানসিকতার দিক দিয়ে আমাদের সাবেক শাসকরা এখন সাধারণের কাতারে নেমে এসেছে, আর আমরা নিপীড়িতরা ক্ষেত্রবিশেষে নিজেরাই পদোন্নতি পেয়ে নিপীড়ক হয়ে গেছি। লাইনে দাঁড়িয়ে এসব বিষয়ে ভাবতে ভাবতে দেখি, সালোয়ার-কামিজ পরিহিতা এক ভদ্রমহিলা পেছনে এসে দাঁড়ালেন। ট্যারা চোখে একনজর দেখে তার পরিচিতি সম্পর্কে খুব একটা ঠাওর করতে পারি না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এশিয়ান বলে অনুমিত হলেও তিনি ভারতীয়, পাকিস্তানি নাকি বাংলাদেশি মেয়ে, তা নিয়েও বেশ দ্বিধায় পড়তে হয়। এ দেশে উপযাচক হয়ে কারও সঙ্গে কথা বলাটা সামাজিক সংস্কার অনুযায়ী সহি নয়, যে কারণে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও গায়ে পড়ে কিছু জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠে না। লাইন আস্তে আস্তে এগোতে থাকে।
থালাবাটির কাছাকাছি পৌঁছার পর কোনো বাক্য ব্যয় না করে ভদ্রতাবশত ভদ্রমহিলার দিকে একটি সানকি বাড়িয়ে দিলে, তিনি কৃতজ্ঞতার হাসি দিয়ে শুকরিয়া বলে ধন্যবাদ জানায়। এরপর যার যার পছন্দমতো খাবার নিয়ে এক কোনায় টেবিলে গিয়ে বসি। ভদ্রমহিলাও পেছনে পেছনে এসে আমাদের সম্মতি নিয়ে সম্মুখের আসনে বসে পড়েন। আলাপে জানা যায়, প্রাথমিক দর্শনে তিনি আমাদের পাকিস্তানি বলে ঠাহর করেছিলেন কিন্তু যখন জানালাম, আমরা পাকিস্তানি নই বাংলাদেশি, ঢাকা থেকে এসেছি। তখন তিনি বললেন, ‘ওকে, নো প্রবলেম, এ দেশে আমার অনেক বাংলাদেশি বন্ধুবান্ধব আছে, আমি কী তোমাদের সঙ্গে খেতে খেতে গল্প করতে পারি?’ মনে মনে বলি, ‘বইসাই যখন পড়ছেন, প্যাচাল পাড়তে আর অনুমতির দরকার কী’। তারপরও মাথা নেড়ে সম্মতি জানানোর পর, ভদ্রমহিলা আসন গ্রহণের কিয়ৎক্ষণবাদে কথার কিতাব খুলে ধরেন। কথাবার্তায় জানা যায়, মহিলার নাম জামিলা। পৈতৃক সূত্রে পাকিস্তানি। জন্মগ্রহণ করেছেন এ দেশে। এখন এ দেশের নাগরিক হিসেবে বসবাস করছেন। তার দাদা ১৯৫৬ সালে পাঞ্জাবের মিরপুর এলাকা থেকে অন্যান্য অভিবাসী শ্রমিকের মতো এমপ্লয়মেন্ট ভাউচারের মাধ্যমে এ দেশে এসে আখড়া বেঁধেছিলেন। এখন এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। জামিলা এ দেশেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের লেখাপড়ার পাট চুকিয়েছেন। এরপর পড়াশোনায় আর অগ্রসর হওয়ার অবসর মেলেনি। বাবার সংসারে বসবাসকাল পর্যন্ত পূর্বপুরুষের দেশের সঙ্গে সামাজিক ও পারিবারিক যোগাযোগ ছিল। এখন খুব একটা যোগাযোগ নেই। অনেক দিন যাবৎ বাপ দাদার ভিটায় যাওয়া হয়ে ওঠে না।
জামিলার মতো তৃতীয় প্রজন্মের অভিবাসীরা ব্রিটেনকেই নিজেদের মাতৃভূমি বা পিতৃভূমি হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। যে কারণে বাবা, দাদাদের মতো করে পূর্বপুরুষদের আদিভূমির সঙ্গে খুব একটা নিজেদের জড়াতে চায় না। ও নিয়ে তেমন একটা মাথাও ঘামায় না। খাবার টেবিলে জামিলা বেগম একমাত্র বক্তা। আমি, মাহবুব আর আজাদ সমঝদার শ্রোতা। বাংলায় যাকে বাচাল বলে, মেয়েটি অনেকটা তা-ই। তার পরও, একনাগাড়ে কথা বলা সত্ত্বেও তার সরলতার কারণে আমরা তাকে বাচাল হিসেবে বিবেচনা না করে একজন সহজ সরল গল্পকার হিসেবে বিবেচনা করে তার কথামালা উপভোগ করতে থাকি। গপ্পুস মহিলা সমানে বকে চলে আর আমরা তিন বাঙ্গাল অনুগত শ্রোতার মতো তার নিঃসৃত বচন হজম করতে থাকি। তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে শুনতে খাবার মুখে পুরতে থাকি। কথামালার সরল উপস্থাপনা, নিষ্পাপ অবয়ব আর অফুরন্ত উচ্ছ্বাস আমাদেরকে তার প্রতি আকৃষ্ট হতে বাধ্য করে। নির্বিকার ভঙ্গিতে অনেক দিনের পরিচিতজনের মতো সে গড়গড় করে বলে যায় তার জীবনের কথা, আমরা অবাক হয়ে শুনতে থাকি। কথা চলতে থাকে উর্দু ও ইংরেজির সংমিশ্রণে। মাহবুব ও আজাদ মাঝে মাঝে হিন্দি, উর্দু ও ইংরেজির সঙ্গে কিছুটা বাংলা মিশিয়ে, ‘তুম বহুত সুন্দরী হায়’ কিংবা ‘হাম তোমহারা বন্ধু বনেঙ্গা, চিঠিপত্র জরুর লেখেঙ্গা’ জাতীয় দু-একটা কথার ককটেল ছুড়ে আবার শ্রোতার কাতারে শামিল হয়। মেয়েটি একটানা বলতে থাকে তার জীবনের কথা, সংগ্রামের কথা, চিরায়ত সংস্কারের কথা। কথাগুলো এবার তার মুখ থেকেই শোনা যাক, ‘জন্মের পর থেকে এখানকার মুক্ত বাতাসে বেড়ে উঠতে থাকি। ছোটবেলায় আমাদের স্কুলে নানা দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়ে পড়ত। গরিব, ধনী, মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আগত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একধরনের সংহতি ছিল। আমরা একটি মুক্তমন নিয়ে উদার পরিবেশে লেখাপড়া করতাম। সহপাঠীদের অনেকে এখন অনেক বড় বড় চাকরি করে। কেউ কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য করে। মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গে দেখা হলে একটু খারাপই লাগে। একটি উন্নত দেশে জন্মগ্রহণ করে এত সুযোগ-সুবিধা পেয়েও জীবনে তেমন কিছু করতে পারিনি। চলার পথেই জীবন থমকে গেছে। পাহাড়সমান প্রতিবন্ধকতা এসে পথ করেছে অবরুদ্ধ’। এ পর্যন্ত বলার পর মহিলা একটু বিরতি দিয়ে উদাস হয়ে কী যেন ভাবতে থাকে।
দেশে ফিরে গিয়ে ভ্রমণের ওপর একটা কিছু লিখব বলে পরিকল্পনা করে রেখেছিলাম, যে কারণে মহিলাকে কাছে পেয়ে মনে হয়েছে, মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি পেয়েছি। জামিলাই আমার ভ্রমণকাহিনির একটি অনবদ্য উৎস হতে পারে ভেবে যারপরনাই উচ্ছ্বসিত হয়ে একটু নড়েচড়ে বসি এবং তার অবগতির জন্য জানাই, ‘তোমার জীবনের ঘটনাবলি শুনতে বেশ আগ্রহ বোধ করছি, কিছু মনে না করে একটু খোলাসাভাবে যদি সবকিছু বয়ান করো তাহলে আমাদের বুঝতে একটু সুবিধা হবে।’ এ কথা শুনে জামিলা নিষ্পলক দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে, হালকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার তার কথার গাড়ি ছোটাতে থাকে। এ পর্যায়ে বলে, ‘উচ্চমাধ্যমিক পাস করার পর বাবা একদিন দাদার বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুরো পরিবারসহ আমাকে নিয়ে পিআইএর হাওয়াই জাহাজে উঠে বসেন। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আমরা চাকলালা বিমানবন্দরে অবতরণ করে সড়কপথে দাদার বাড়ির পথে রওনা হই। নতুন দেশের রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, চারদিকের পরিবেশ বেশ ভালো লাগলেও, ওদের গরিবানা হালত আমাকে খুব আহত করে। গাড়ি যত এগিয়ে চলে বাবার উচ্ছ্বাস ততই যেন বাড়তে থাকে। আমার তেমন কোনো ভাবান্তর হয় না। কয়েক ঘণ্টা ভ্রমণ শেষে দাদার বাড়িতে পৌঁছে গোসল করে খাওয়াদাওয়া সেরে লম্বা এক ঘুম দিই।
সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর মন বেশ ফুরফুরে হয়ে ওঠে। নতুন পরিবেশে খুব একটা খারাপ লাগে না। অনেক ছোটবেলায় একবার ও দেশে গিয়েছিলাম, সেসবের কোনো স্মৃতি তখন আর মনে নেই। আশপাশের আত্মীয়-পরিজনরা দলে দলে এসে আমাদের দেখতে থাকেন। মা, বাবা আগেই নির্দেশনা দিয়ে রেখেছিলেন, সে মোতাবেক মাথায় ওড়না পরে সবার সামনে আমাকে হাজির হতে হয়। আত্মীয়া সম্পর্কের দু-একজন খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার উচ্চতা, গায়ের রং এবং রূপ যৌবন পরখ করতে থাকেন, ব্যাপারটা বেশ অস্বস্তিকর ঠেকলেও কিছু বলতে পারি না। বোবার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকি আর মাঝে মাঝে কোনো প্রশ্ন করলে উত্তর দিই। বোন-সম্পর্কীয়া কলেজ পড়ুয়া এক মেয়ে ব্রিটেনে আমার কোনো বয়ফ্রেন্ড আছে কি না, জানতে চাইলে বেশ অবাক হই। এ ধরনের অবান্তর প্রশ্ন কেন করা হচ্ছে তার কোনো আগামাথা খুঁজে পাই না। দেখতে দেখতে দিন কেটে যেতে থাকে। সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় এ-বাড়ি ও-বাড়ি দাওয়াত খেয়ে খেয়ে সময় বয়ে যায়।
ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও নিজের মতো করে কোথাও ঘুরতে পারি না। ওখানকার রক্ষণশীল সমাজে সাবালিকা মেয়েদের যত্রতত্র টই টই করাটা অনুমোদিত নয়। মাঝে মাঝে আত্মীয় ঘরানার দু-চারজন যুবকের সামনে পড়তে হয়, তখন খুব সন্তর্পণে পাশ কেটে যাই, ওরাও ট্যারা চোখে একটু দেখেই কেটে পড়ে। কথা বলা হয় না। ব্রাডফোর্ডে অপরিচিত কোনো যুবকের সঙ্গে কথাবার্তা বলাটা কোনো ধর্তব্যের বিষয়ই না, কিন্তু ও দেশে তা প্রায় অসম্ভব। ক্ষেত্রবিশেষে ছিনালিপনার শামিল। কত দিন এভাবে থাকতে হবে, কবে ফিরে যাব? এসবের কোনো কিছুই বাবা আমাদের জানান না, জিজ্ঞেস করলে মা-ও নিরুত্তর থাকেন। বাবা বেশ আমুদে মেজাজে সারা দিন ছোটাছুটি করেন। আমাদের সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপারে কখনো কোনো কিছু জানতে চান না। অবশ্য আমরাও তেমন করে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হইনি। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় বাবা হন্তদন্ত হয়ে বাসায় পা রেখেই মায়ের সঙ্গে কী নিয়ে যেন ফিসফাস করে আবার বেরিয়ে পড়েন। এরপর মা আমার পাশে বসে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ঘোষণা করেন, আজ রাতে আমার শাদির এন্তেজাম করা হয়েছে। অচমকা শাদির কথা শুনে আমি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। মুখ্যত আমার মধ্যে তখনো এ-সম্পর্কিত কোনো চেতনার উদয় হয়নি। যদিও শারীরিকভাবে আমি বালেগ ছিলাম কিন্তু মানসিকভাবে একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। তা ছাড়া কেবল কৈশোর পেরিয়েছি, বয়সও এমন কিছু হয়নি যে বিয়ের পিঁড়িতে বসতেই হবে। ইচ্ছে ছিল আরও লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের পছন্দের কোনো জওয়ানকে নিয়ে ঘর বাঁধব। যে কারণে আচমকা বিয়ের কথা শুনে প্রথমটা বেশ ভড়কে যাই, মৃদু প্রতিবাদ করতে গিয়ে বুঝতে পারি পারিবারিক সমর্থন পুরোটাই বাবার দিকে। মা এ ব্যাপারে নিরুপায়, বিধায় নির্বিকার। একটি উদার সামাজিক পরিবেশে জন্ম নিয়েও আমাকে বসবাস করতে হয়েছে অত্যন্ত রক্ষণশীল পারিবারিক পরিমণ্ডলে। যে কারণে সেদিন বিয়েতে সম্মত না থেকেও বিয়ে নামের লাড্ডু হজম করতে হয়েছে।
যে ছেলেটির সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়, সে ছেলেটিকে আগে কখনো দেখিনি। ওর সঙ্গে কোনো কথাবার্তাও হয়নি। বিয়ের দিনেই প্রথম দর্শন। প্রথম দেখাতে ও আমাকে খুব একটা মোহিত করতে পারেনি। প্রাথমিক পরিচয় পর্বের সময়ও তার আচার আচরণ খুব ভালো ঠেকেনি। কথাবার্তায় সব সময় একধরনের আদেশের আমেজ অনুভূত হয়েছে। বিনয়ের ‘ব’ও জানে বলে মনে হয়নি। আমার কাছে মনে হয়েছিল আমি যেন প্রথম বিশ্ব থেকে তৃতীয় বিশ্বে ছিটকে পড়েছি। আমাদের পারিবারিক সংস্কার, ধর্মীয় অনুভূতি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থানের কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওই চিড়িয়ার সঙ্গে বাসর রাত কাটাতে হয়েছে, ভালোবাসা প্রদান করতে হয়েছে। এখানে অবশ্য ঠিক ভালোবাসা বলাটা ঠিক হবে না। কারণ, বিষয়টি ছিল একতরফা। যে ধরনের ভালোবাসা প্রত্যাশা করেছিলাম, সে ধরনের কোনো কিছু তার ভাণ্ডারে আদৌ মজুত ছিল কি না, সন্দেহ। প্রথম রাতেই বিড়াল হত্যার নামে সে আমার সঙ্গে যা করেছে, সেটাকে ধর্ষণ বললেও ধর্ষণের অপব্যাখ্যা করা হবে। বন্য হস্তীরা যেমন সদ্য গজিয়ে ওঠা ধানের শিষ পদতলে নিষ্পেষিত করে, আমার অবস্থাও হয়েছিল অনেকটা সে রকম। সে বিগড়ে যাওয়া কুকুরের মতো শরীরের স্পর্শকাতর উপত্যকাগুলোতে দাঁতের দাগ বসিয়েছিল, দাগগুলো শুকাতে প্রায় এক মাস সময় লেগে যায়।
পরবর্তী দিনগুলোতে পেয়ার মহব্বতের নামে ও যা করেছে, তা স্রেফ আগ্রাসন বৈ অন্য কিছু নয়। আজন্ম লালিত সংস্কার আমাকে বিদ্রোহী হতে বাধা দেয়, শৃঙ্খলে কুঠারাঘাত করার আগেই হাত থেকে কুঠার পড়ে যায়। যে কারণে আমি বিদ্রোহী হতে ব্যর্থ হই। নিয়তিকে মেনে নিয়ে বেহায়ার মতো নিজেকে মেলে ধরি তার সমীপে। হায় বদনসিব! বলে নিজেকেই নিজে তিরস্কার করি। বিয়ের পনেনো দিন পরে আমরা ফিরে আসি ব্রাডফোর্ডে। সে থেকে যায় ওদের দেশে। সলিসিটারের মাধ্যমে বিভিন্ন কাগজপত্র ঠিকঠাক করে বাবা তার পেয়ারের দামানকে ছয় মাসের মধ্যে এ দেশে নিয়ে আসে। এখানে আসার পর তার প্রভুত্বসুলভ আচরণের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। আমি হয়ে পড়ি তার নাচের পুতুল। তার কথায়, শারীরিক ভাষায় বোঝা যায়, সে ভালোবাসবার জন্য বিয়ে করেনি, সংসার করার জন্যও নয়। এ দেশে ইমিগ্র্যান্ট হবার লোভেই সে বিয়ে করেছে। গ্রামের এক সাদামাটা দেহাতি ব্রিটেনে পদার্পণের পর থেকেই শরীরে পাখনা লাগিয়ে উড়তে থাকে। নতুন সমাজ, নতুন দেশে এসে সে নতুন জীবনের দিকে পা বাড়ায়। আমি কিসমতকে মেনে নিয়ে ওপরঅলার কৃপায় ভর করে তার সঙ্গে একটি সুখের সংসার গড়তে চেয়েছিলাম। দুজন মিলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর জগৎ রচনা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দিনে দিনে প্রতি পদে পদে আমার স্বপ্নের ডানা থেকে পালক খসে পড়তে থাকে। স্বপ্নগুলো কর্পূরের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে থাকে।
ও এখানে আসার কিছুদিন পর থেকে আমরা আলাদা বাসা নিয়ে বসবাস করতে থাকি। বাবা ওকে একটি ভালো কাজও জুটিয়ে দিয়েছিল, ও ইচ্ছে করলে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারত। আমাদের যৌথ শ্রমে আমরা আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ হতে পারতাম। কিন্তু ওর মধ্যে বাস করত একটি লোভার্ত মন। ওপরে ওঠার, বিশেষ করে বিপুল ধনসম্পদ অর্জনের অদম্য স্পৃহা ছিল ওর মনে। কিছুদিন এখানে বসবাসের পর, এখানকার রাস্তাঘাট চেনার পর, আয়-রোজগারের অলিগলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের পর, তার ভেতরের লোভাতুর মন আরও চাঙা হয়ে ওঠে। আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থিত হয় শারীরিক সম্পর্কের চৌহদ্দীতে। আগেই বলেছি, রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন ওই পুরুষটির ভেতরে প্রেম-ভালোবাসার লেশমাত্র ছিল না। মুক্ত সমাজের মুক্ত পরিবেশ পেয়ে দিনে দিনে ও হয়ে ওঠে বেপরোয়া। এখানকার সমাজের নেতিবাচক সংস্কৃতিতে সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। বউকে বোরকা পরতে বলে নিজে সমানে মেয়েদের সঙ্গে ডেটিং করতে থাকে। শরাব খাওয়া তার কাছে ফ্যাশনে পরিণত হয়। আকণ্ঠ মদ গিলে মাতালি করতে করতে স্ত্রীর গায়ে হাত তোলাতেও সে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। অনেক চেষ্টা করেও তাকে সংসার, সন্তান কিংবা আমার প্রতি মনোযোগী করতে পারিনি। কখনো কখনো মনের অজান্তে চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ত এক নদী বেদনার জল।’
মাঝে মাঝে খাওয়া স্থগিত রেখে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকি এই দুখিনি কন্যা জামিলার দিকে। কিছু বলবার বা সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পাই না। তারপরও জিজ্ঞেস করি, ‘তোমরা কি কোনো সন্তান নিয়েছিলে?’ মুখে খাবার পুরে হালকা করে চিবাতে চিবাতে আবার সে বলে চলে, ‘বিয়ের রাতে যেদিন বাসর শয্যা হয়, সেদিন থেকে তালাকের আগপর্যন্ত কোনো দিন সে আমাকে আদর-ভালোবাসার রসায়নে কোনো কথা বলেনি। বাসর রাত থেকে শুরু করে সর্বশেষ দিন পর্যন্ত সে শারীরিক ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করেছে আদিম আদলে। বর্বরতার একটা নিকৃষ্ট মডেল ছিল আমার সোয়ামির। তার কাছে বলাৎকারই প্রেম-ভালোবাসার সার্থক সিম্বল। পার্টনারের সম্মতির কোনো তোয়াক্কা সে কোনোকালে করেনি। তার অন্যায্য আগ্রাসনের ফলে একে একে জন্ম দিতে হয় তিনটি সন্তান। ভেবেছিলাম বাচ্চারা বড় হলে অবস্থানের উন্নতি হবে, কিন্তু বাস্তবে হয়েছে উল্টো।’ এ পর্যন্ত শুনে তাকে বলেছিলাম, ‘তুমি তোমার বাবা-মাকে এ বিষয়ে কিছু বলোনি বা এর একটা বিহিত করোনি কেন?’ প্রশ্ন শুনে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে আবার বলতে থাকে, ‘বাবা, মা, ভাই, বোন এবং আত্মীয়স্বজনরা পুরো ঘটনা সম্পর্কে সব সময় অবহিত ছিলেন, কিন্তু এত সব দেখে শুনেও ওনারা বরাবরই বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। তারা বাস করেন ইউরোপের উদার পরিবেশে কিন্তু ভেতরে লালন করেন মধ্যযুগের অন্ধকার। পুরুষশাসিত সমাজের মূল্যবোধ, ধ্যান-ধারণার পুরোটাই এখনো তাদের মধ্যে রয়ে গেছে। মা, বোন, স্ত্রী, মেয়ে, সম্পর্ক যা-ই থাক না কেন, তাদের কাছে এখনো আওরাত মানে আওরাত। যাদের কোনো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থাকতে নেই। নিজস্ব চিন্তাচেতনা থাকতে নেই। প্রেম, ভালোবাসা, ভালো লাগা থাকতে নেই।
দুঃসহ যাতনাযুক্ত প্রেমহীন, ভালোবাসাহীন এই অসার সংসার ভেঙে ফেলার জন্য অনেক চেষ্টা করেও বারবার পিছিয়ে আসতে হয়েছে। প্রাচ্যের হাজার বছরের লালিত সংস্কৃতির প্রভাবে এবং সন্তানদের পিতৃহীন না করার তাগিদে বারবার গর্জে উঠতে গিয়েও ফুটা বেলুনের মতো চুপসে গিয়েছি, কী এক অদৃশ্য শক্তি যেন আমাকে পেছন থেকে টেনে ধরে থামিয়ে দিয়েছে। বলেছে, রুখ যা জামিলা, তু তো আওরাত হ্যায়। পরিশেষে সে যখন গায়ে হাত তোলা শুরু করে, তখন থেকে ধীরে ধীরে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে থাকি। ওরা যেহেতু দেশের বাড়িতে খুব প্রভাবশালী পরিবারের লোক ছিল, সেহেতু আমাদের পরিবারের মানসম্মান আর নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে ওর বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে নালিশ করিনি। আইনগত কোনো ব্যবস্থাও গ্রহণ করিনি। কিন্তু সবকিছুরই একটা শেষ আছে, যে কারণে শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে আমার আর থাকা হয়নি। একসময় পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেলে, ঘুরে দাঁড়াতে হয়। প্রাচ্যের মূল্যবোধ ঝেড়ে ফেলে আমাকে হতে হয় ইউরোপের স্বাধীন আওরাত। ভেঙে ফেলতে হয় কুসংস্কারের অচলায়তন। এরপর দ্বিধাহীন চিত্তে তাকে তালাক দিয়ে দিই।’ এতক্ষণ পরে গল্পের একটা পরিণতি পেয়ে যেন কিছুটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। তারপর সন্তানদের ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে গিয়ে জানতে পেলাম, তালাকের পর তিন সন্তান নিয়ে শুরু হয় তার পথচলা, যে হেতু এখানকার বাড়িটা তার নামে বরাদ্দ ছিল, সেহেতু সে বাড়িতে থেকে ওকে চলে যেতে বাধ্য করে। এরপর সমাজসেবা বিভাগের ভাতা আর কঠোর পরিশ্রমের আয়-রোজগারে চলতে থাকে তার সংসারের চাকা। এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া চালিয়ে নিতে থাকে। তার ত্যাগ-তিতিক্ষা আখেরে তার সঙ্গে প্রতারণা করেনি। বড় ছেলে এখন অক্সফোর্ডে মেডিকেল সায়েন্সে পড়ছে, ফাইনাল ইয়ারে। মেয়ে দুটোর একজন কলেজে এবং একজন মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়ছে।
এত কিছু শোনার পর শ্রোতাদের অবাক হওয়ার পালা শুরু হয়, একজন আরেকজনের দিকে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে থাকি। আমরা মেয়েটিকে মনে করেছিলাম অনূর্ধ্ব ত্রিশ কিন্তু তার বড় ছেলে মেডিকেলে পড়ে জানতে পেরে একটু খটকা লাগে। আমাদের কৌতূহল মেটাতে জামিলাই সমস্যার সুরাহা করে দেয়। সে আবার বলে, ‘মাত্র ১৫ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল বলে জীবনকে জানার আগেই জীবন আমার কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, এখন ছেলেটির একটি গতি করে, মেয়েদের লেখাপড়ার লাইনে দাঁড় করিয়ে নিজেও একটু নড়ে চড়ে উঠতে চাই। বয়স মাত্র ৩৪ হয়েছে, আহামরি এমন কিছু নয়। তাই আবার নতুন করে সবকিছু শুরু করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। মন প্রাণ সঁপে লেখাপড়া করছি আর সেই সঙ্গে একটি ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও খুলেছি। টুকটাক যা আয় হয়, তা দিয়ে মোটামুটি ভালোভাবে দিনকাল চলে যাচ্ছে’। জামিলার জীবনসংগ্রামের কথাগুলো বেশ ভালো লাগে। ঔৎসুক্য দমাতে না পেরে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করি, ‘আবারও কি ঘরসংসার করবে, নাকি এভাবেই জীবন কাটিয়ে দেবে।’
এ কথা শোনার পর, জামিলা অনেকটা কুমারী কন্যার মতো লাজে নেতিয়ে পড়ে, পরমুহূর্তেই উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে থাকে, ‘তোমাদের বলতে দ্বিধা নেই, আবার নতুন করে সবকিছু শুরু করব মানে প্রকৃত অর্থেই সবকিছু শুরু করব। জানো, আমার জীবনে এই প্রথম একজন পুরুষ এসেছে যে আমাকে প্রকৃত অর্থে ভালোবাসে, সব সময় আমাকে ফিল করে, আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে, একেবারে জানপ্রাণ উজাড় করে আমাকে অনুভব করে।’ কথাবার্তা শুনে মনে মনে ভাবি পাগলি বলে কী? এই তিন বাচ্চার মাকে আবার কোন পাগলে জান দিয়ে ভালোবাসতে গেল? এরপর সে আমাদের মতামতের তোয়াক্কা না করে তার ব্যাগ থেকে একগাদা ছবি বের করে তার মনের মানুষকে দেখাতে থাকে। এক একটা ছবি বের করে আমাদের সামনে মেলে ধরে আর ছোটবেলায় দেখা বায়োস্কোপের কথকের মতো একেক ধরনের বিশেষণে হবু বরকে সম্বোধন করতে থাকে। ছবি দেখিয়েই সে ক্ষান্ত হয় না। ক্ষণিক বাদে মোবাইলে ধারণকৃত ছবির সিরিজ দেখাতে থাকে। মোবাইলে দেখলাম, অনূর্ধ্ব ত্রিশ বছর বয়সের এক খুবসুরত তাগড়া যুবকের বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে তোলা ছবি। চেহারা সুরত দেখে বোঝা যায়, ছেলেটি কোনো এক সামন্ত ঘরের অভিজাত সন্তান এবং মেয়েটির তুলনায় বয়সে অনেক ছোট। ‘এ ছেলের সন্ধান কীভাবে পেলে, কেমন করে এর সঙ্গে সম্পর্কে জড়ালে?’ এ ধরনের প্রশ্নের জবাবে জামিলা গড়গড় করে বলে, ‘লন্ডনে ওর সঙ্গে আমার এক কনসার্টে দেখা হয়েছিল। ও খুব ভালো গান করে, চমৎকার কণ্ঠ। ওর গান শুনে ওকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে একপলকেই উভয়ে উভয়কে পছন্দ করি। তা ছাড়া ওর লেখাপড়া শেষ। ম্যানেজমেন্টে মাস্টার্স সম্পন্ন করেছে। এখন ভিসার মেয়াদও প্রায় শেষ।
আইনগতভাবে কদিন বাদে সে আর এ দেশে অবস্থান করতে পারবে না। যেহেতু আমি এখানকার সিটিজেন সেহেতু আমাকে বিয়ে করলে ওর একটা হিল্লে হয়ে যাবে, এ দেশে অবস্থান করতে পারবে, এখন আমার ওপরই নির্ভর করছে ওর ভবিষ্যৎ’। এত সহজ-সরলভাবে একজন নিষ্পাপ প্রেমিকা তার প্রেমিকের প্রতি আস্থা রেখে যে বয়ান পেশ করে তাতে করে কিঞ্চিৎ শঙ্কা বোধ করি। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করি, ‘তুমি যে তিন বাচ্চার মা, তা কি তোমার প্রেমিক ইমতিয়াজ এবং তার বাবা-মা জানেন’? জামিলা প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে, ‘হ্যাঁ, ইমতিয়াজ ওর বাবা মাকে আমার বিষয়ে সবকিছু বিস্তারিতভাবে জানিয়েছে, মুরব্বিদের তরফ থেকে কোনো আপত্তি নেই, তা ছাড়া ছেলে তো আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, আমার সঙ্গে রাতে কথা না বলে সে তো ঘুমাতেও পারে না, মজনুর মতো সে আমার দেওয়ানা। আমার অনুভূতি তাকে প্রতিনিয়ত মোহগ্রস্ত করে রাখে। আমি কখনো কোনো পুরুষের কাছে এভাবে প্রেম পাইনি। আগের স্বামীর আচার ব্যবহারের কারণে একপর্যায়ে পুরো পুরুষ জাতির ওপর আমি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলাম, এখন ইমতিয়াজ আমার হারানো আস্থা ফিরিয়ে দিয়েছে। আমার এ শূন্য জীবনে পূর্ণতা এনে দিয়েছে। ওর নিশ্বাসে, বিশ্বাসে এখন শুধু আমার প্রেমই প্রতিধ্বনিত হয়।’
লাঞ্চ শেষ হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। জামিলার কথা শোনার জন্য এতক্ষণ বসেছিলাম। ক্লাস শুরু হয়ে যাবে, যে কারণে একসময় তাকে রেখে উঠতে হয়। বিদায়কালে চপলমতি জামিলা বারবার করে তার ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আমাদের দোয়া করতে বলে। আমরা খাস দিলে ওর জন্য স্রষ্টার দরবারে দোয়া করবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বিদায় নিয়ে ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে আসি। সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে ভাবতে থাকি, ইমতিয়াজ কি সত্যি সত্যি জামিলাকে ভালোবাসে, নাকি নাগরিকত্ব হাসিলের জন্য প্রেম-ভালোবাসার নাটক করছে? ছেলের বাবা-মা কি আদৌ তিন বাচ্চার মাকে নিজেদের ডেগা পোলার বউ হিসেবে বরণ করে নেবেন, ওই দেশের পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ কি এখনো অতটা উদার হতে পেরেছে? এত সব নেতিবাচক ভাবনার মাঝেও আমাদের প্রিয় জামিলার জন্য একটি সুন্দর জীবন প্রত্যাশা করে ঝড়ো-হাওয়াসহ শূলের মতো নিঃসৃত বৃষ্টি উপেক্ষা করে ক্লাসরুমের দিকে হাঁটতে থাকি। পেছনে পড়ে থাকে এক প্রেমিকার মায়াভরা ছায়া।
দেশে ফেরার পর জামিলাকে আর সেভাবে কখনো স্মরণ করিনি। তিন বছর পর পুরোনো কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করার সময় হঠাৎ তার একটি ভিজিটিং কার্ড নজরে পড়ে। ওতে ওর মেইল অ্যাড্রেস দেওয়া ছিল। অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও নয়া প্রেমিক নিয়ে কেমন আছে, তা জানতে চেয়ে একটি মেইল করি। সাত দিন পর তার জবাব আসে। অনেক কথার পর সে লিখেছিল, ম্যায়নে এক বদনসিব আওরাত হুঁ।


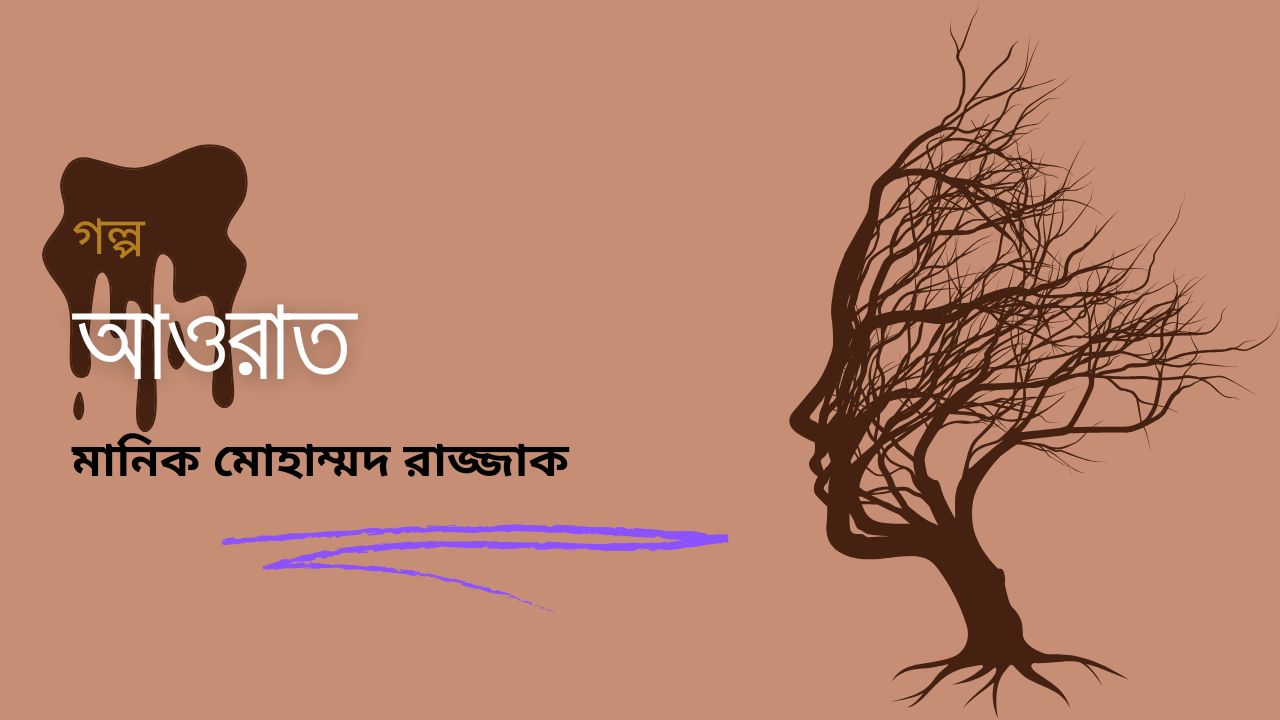
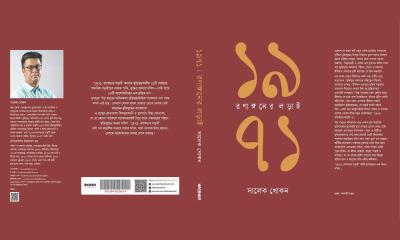


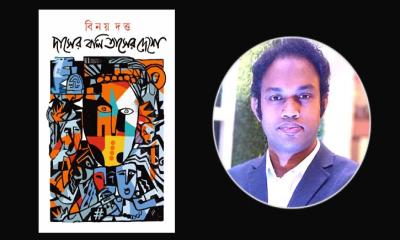





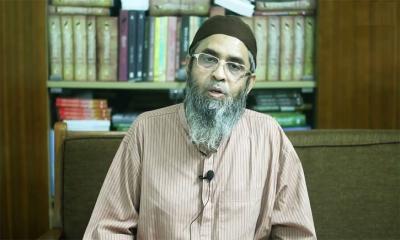







-20250330102725.jpeg)




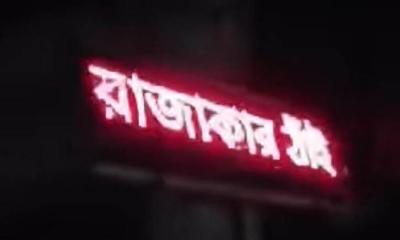



-20250330080132.jpeg)