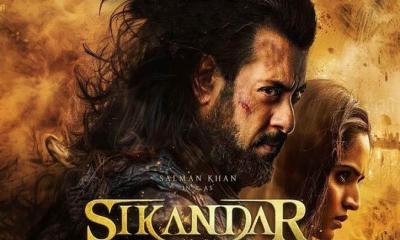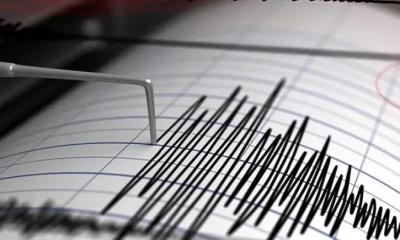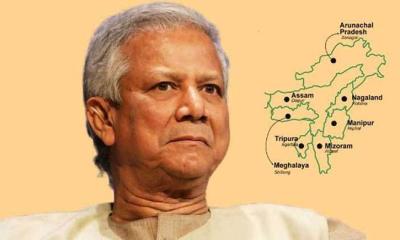জার্মান মার্ক্সবাদী বিপ্লবী ও রাজনীতিবিদ রোজা লুক্সেমবার্গ এক চিঠিতে লিখেছিলেন, “মোটাদাগে বার্লিনকে আমার ভালো লাগে না: শীতল, বিস্বাদ, নিথর… বার্লিনকে আমি অপছন্দ করি এবং জার্মানদের এতোটাই অপছন্দ করি যে ওদের দেখলে খুন করতে ইচ্ছে করে।” আসলে রোজা লুক্সেমবার্গের জার্মানি আর নেই, বার্লিনও বদলেছে অনেকটা। বার্লিন এখন হয়েছে নানা জাতি ও বর্ণ মিলিয়ে এক বিচিত্র শহর। এখানে ঠাণ্ডা আছে ঠিক, তবে স্বাদহীন আর নেই, পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে লোকজন এসে বার্লিনকে উপহার দিয়েছে নানা স্বাদের খাবার। নিশ্চল তো বলাই যাবে না বার্লিনকে। সারারাতই মানুষের চলাচল থাকে এখানে। জেগে থাকে নাইটক্লাবগুলো।
অল্প করে খাবারদাবারের কথা বলেই আমরা সিনেমার আলাপে চলে যাব। এখানে বেকারি আইটেম খুব পাওয়া যায়। অন্য দেশের ক্যুইজিনও অহরহ দেখা যায় বিভিন্ন ফুডকোর্টে। বিশেষ করে পাতালস্টেশনের একেকটা জায়গা তো খাবারের দোকান দিয়ে ভর্তি। কোথাও ইন্ডিয়ান ফুড, তো কোথাও তুর্কি খাবার, কোথাও ইতালিয়ান খাবার, কোথাও বা চীনা খাবার। তবে এদের পেস্ট্রিশপ, ক্যাফে ও মুদি দোকানে একটা খাবার থাকেই, সেটি হলো ব্রেজেল বা প্রেৎজেল। শাহী জিলাপির মতো দেখতে অনেকটা, কিন্তু ভেতরে ক্রিম দিয়ে ওভেনে বানানো হয় এটি। গায়ের উপর নানা জিনিস যুক্ত করায় ব্রেজেল হয়ে ওঠে ভিন্নভিন্ন স্বাদের। জার্মানরা দেখলাম সকাল ও বিকেলের নাস্তায় খুব পছন্দ করে এই ব্রেজেল খেতে। আমিও খেয়ে দেখেছি। পছন্দ হয়েছে খাবারটি। কফি বা সোডা জাতীয় পানীয়র সাথে দিব্বি মানিয়ে যায় এই ব্রেজেল।
কদিন ধরে মেট্রোস্টেশনের ফুডকোর্টের খাবার পরখ করে দেখছি। সকালে ভেন্যুতে যাওয়ার পথে স্টেশনে নেমেই কিনে নিচ্ছি ডিম ওমলেট ও বেকন দিয়ে বানানো স্যান্ডুইচ অথবা মিষ্টি দেওয়া খোয়াজো। এগুলো তিন থেকে ছয় ইউরোর মধ্যেই পাওয়া যায়। এছাড়া ডোনাট, চিজকেক, মিষ্টি বনরুটি ইত্যাদি সব দোকানেই শোভা পায়। এগুলোর ভেতরেই নানা উপাদান এদিক-সেদিক করে স্বাদের ভিন্নতা আনা হয়। দুদিন হলো আবিষ্কার করেছি এক আফগান খাবারের দোকান। আলেক্সান্দার প্লাৎজের পাতাল স্টেশনে ইউ-টু লাইনের ট্রেন ধরতে যাওয়ার সময় পড়ে দোকানটি। কিউবিক্সের পাশ দিয়ে নিচে নেমে সোজা গেলেই হাতের বায়ে। সেখান থেকে একদিন খাওয়া হলো ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের সাথে সসেজ ভাজা। এটার নাম ‘কারিভুর্স্ট উইদ পোমস’। আফগান দোকান থেকে খেলেও, এটা কিন্তু খাঁটি জার্মান খাবার। একই দোকান থেকে সপ্তম দিনে রাতে বাসায় ফেরার পথে খেয়েছি ‘কাবেলি পালাউ’ মানে কাবুলি পোলাও মাংস। এটা একেবারে আফগান খাবার। ছোট থালার দাম সাত ইউরো, আর বড়টা বারো। ছোট থালাটাই আমি পুরো শেষ করতে পারিনি। মুরগির হলুদ কারির সাথে সালাদ দিয়ে আফগানি ঢংয়ে রান্না করা পোলাও খেতে ভালোই লেগেছে।
তো উৎসবের এই সাত নম্বর দিনটাতে ভেন্যুর স্টেশনে নেমেছি ঠিকই, কিন্তু মূল ভেন্যুতে না গিয়ে আমাকে ধরতে হয়েছে আরেকটি ট্রেন। কারণ আজ সব স্ক্রিনিংই আলেক্সান্দার প্লাৎজের কিউবিক্সে। জুলিয়াস-লেবার-ব্রুক থেকে প্রথমে ওরানিয়ানবুর্গগামী এস-ওয়ান ট্রেনে চেপে পটসডেমার প্লাৎজ, এরপর সেই স্টেশন থেকে বেরিয়ে অদূরের ইউ স্টেশনে গিয়ে পানকোগামী ইউ-টু ট্রেনে চড়তে হয়। সেই ট্রেন ছয়টি স্টেশন পেরিয়ে এগারো মিনিটের মধ্যে সপ্তম স্টেশন আলেক্সান্দার প্লাৎজে পৌঁছে যায়। আমি ওখানেই নেমে যাই। ঠিক এই ট্রেনগুলো ধরেই ফিরতে হয়। শুধু ফেরার সময় খেয়াল রাখতে হয় ইউ-টু ট্রেনটি হবে রুলেবেনগামী আর এস-ওয়ান হবে ভানজিগামী। ব্যাস, ব্যাপারটা সোজাই।
আলেক্সান্দার প্লাৎজে নেমে আজ একটি স্যান্ডুইচ কেনার সাথে সাথে দোকানি ছেলেটা বলল, গরম করে দিই? বললাম, দাও। গরম স্যান্ডুইচ খেতে খেতে যখন পাতাল থেকে উপরে উঠে এলাম, অন্তত দুজন ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইল। একজন নারী, একজন পুরুষ। এবং এদের কেউই জার্মান নয়। একজন এশীয় লোককে দেখলাম কি যেন ফেরি করছে, ভারতীয় বা বাংলাদেশী হবে। আরেকজন অজার্মান নারীকে দেখলাম বিশেষ পোশাক পরে, ব্যানার নিয়ে ‘হপ-অন হপ-অফ’ বাসের টিকিট বিক্রি করছে, নারীটি আরব হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কত বিচিত্র কাজই না করতে হয় এই বিশাল শহরে টিকে থাকার জন্য। আমি খাওয়া শেষ করে কিউবিক্সে প্রবেশ করলাম। প্রথম ছবিটি আমার পার্সপেক্টিভস বিভাগের ছবি নয়, ফোরাম সেকশনের ছবি।
তাইওয়ানের ছবিটির নাম ‘দ্য ট্রায়ো হল’ (২০২৫), পরিচালকের নাম সু হুই-ইয়ু। ব্যাঙ্গধর্মী ছবিটিতে বর্তমান বিশ্বের যে অস্থিরতা সেটিকে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা হয়েছে শীতল যুদ্ধের আমলের সাথে। মানে পঞ্চাশ থেকে আশির দশক পর্যন্ত যে কোল্ড ওয়ারের জ্বরে পুরো পৃথিবী বিভক্ত ছিল সেই বিষয়টি এসেছে কৌতুকের আকারে। যেমন বিকিনি পরে সুন্দরী প্রতিযোগিতায় দেখা যায় কোনো তরুণীর নাম স্ট্যালিন, কারো নাম চার্চিল, কেউ আবার হিটলার, আরেকজনের নাম মাও জেদং ইত্যাদি। তারা নাকি হেগেলিয়ান ডায়ালেক্টিকাল ডান্সে অবতীর্ণ হয়েছেন। সত্যি বলতে এত ফালতু ভাঁড়ামো মার্কা ছবি আমি আশা করিনি বার্লিনালের ফোরামে দেখতে পাবো। পলিটিকাল স্যাটায়ার করার জন্য ন্যূনতম যে জ্ঞান দরকার সেটি পরিচালকের নেই।
ছবি শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে যখন মঞ্চে এসে পরিচালক দাঁড়ালেন, তখনই বোঝা গেছে তার লেখাপড়ার দৌঁড়। উনি বলছেন, আমরা দুনিয়ার সবকিছু নিয়ে জোকস করতে চাই। আমরা কাউকে ভয় পেতে চাই না। ইত্যাদি ইত্যাদি। নিজের ছবিটার মতোই তিনি বুঝিয়ে দিলেন তিনি মূঢ় বটেন। বিশ্বনেতাদের নিয়ে সমালোচনা হতে পারে, ব্যাঙ্গ হতে পারে, কেরিকেচার হতে পারে। কিন্তু এই লোক ফিজিকাল কমেডি দিয়ে যা করার চেষ্টা করল, সেটা শেষ পর্যন্ত কোনো কিছুতেই গিয়ে দাঁড়াল না, বরং ব্যর্থ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে। আমরা পলিটিকাল স্যাটায়ারের কথা যদি বলি তাহলে দুনিয়ায় তো চার্লস চ্যাপলিন, স্ট্যানলি কুব্রিক, টেরি গিলিয়াম, রুবেন উস্টলান্ড প্রমুখরা ছিলেন। তাদের কাজ দেখেও তো শেখা যেত! আমি পাশে বসে থাকা দর্শককে জিজ্ঞেস করলাম, তিনিও কাঁধ ঝাকিয়ে বললেন, সবকিছু একজায়গায় আনতে গিয়ে কিছুই ফুটিয়ে তুলতে পারেনি ছবিটি। ওর পাশে বসে থাকা মেয়েটি বলল, বেটার লাক নেক্সট ফিল্ম!
অচেনা মেয়েটির শুভকামনা কাজে লেগেছে। পরবর্তী দুটি ছবিই পার্সপেক্টিভস সেকশনের এবং দুটোই যথেষ্ট ভালো মানের ছবি। একই ভবনের নয় নম্বর থিয়েটারে বিকাল চারটায় শুরু হলো পর্তুগালের ছবি ‘টু টাইমস জোয়াও লিবেরাদা’ (২০২৫), পাওলা থমাস মার্কুজের প্রথম ছবি। এমনিতে কুয়ের (Queer) ফিল্ম খুব একটা দেখা হয় না, কিন্তু এই ছবিটা দেখে ভালো লেগেছে। ছবিটিকে ফিল্ম উইদিন ফিল্মও বলা যায়। ছবির ভেতর ছবি বানানোর গল্প। কিন্তু তারই উছিলায় দেখানো হয় সমাজে বিদ্যমান বাইনারি লিঙ্গ ভাবনার বিপরীতে তৃতীয়লিঙ্গের শক্ত অবস্থান জানানোর প্রচেষ্টা। জোয়াও, লিসবন ভিত্তিক তৃতীয়লিঙ্গের অভিনেত্রী, সে অভিনয় করছে অষ্টাদশ শতকের একটি কাহিনভিত্তিক চলচ্চিত্রে। যে কাহিনিটি লিবেরাদা নামের একজন তৃতীয়লিঙ্গের ধর্মযাজিকার জীবনের উপর লিখিত। সেসময় পর্তুগিজ চার্চ ওই ধর্মযাজিকাকে বিচারের মুখোমুখি করেছিল। ওই মুহুর্তে মানুষটির যন্ত্রণা ও পরিত্রাণের বিষয়টি যেভাবে উঠে আসার কথা চলচ্চিত্রে, দেখা যায় জোয়াও’র পরিচালক তা তুলে আনতে পারছে না। ভাগ্যচক্রে পরবর্তীকালে পরিচালক ছবিটি শুট করতে অপরাগ হয়ে পড়লে, জোয়াও নিজে পরিচালনার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয় এবং অষ্টাদশ শতকের লিবেরাদাকে সে যেভাবে নিজের চিন্তা ও মননে ধারণ করেছে, সেভাবে প্রস্ফূটিত করার চেষ্টা করে। এটাই এই ছবির কাহিনি।
আমার আরো ভালো লেগেছে, ছবিটি শুরুর আগে ঢোকার মুখে সকলকে একটি ছোট পোস্টকার্ডের মতো কার্ড দেয়া হয়। তার এক পিঠে উডকাট প্রিন্টে লিবেরাদার ছবি, অন্যপিঠে গানের কথা। এই গানটিই ছবির শেষে বেজে ওঠে। উপমহাদেশে ষাটের দশকে এই চলটা ছিল, গানের কথা ছাপানো হতো এবং দর্শকরা সেটা সংগ্রহ করতেন। এসব ইতিহাসের বইতে পড়েছি। কিন্তু বার্লিনে এসে সেই চর্চাটি দেখলাম। যাক আগের দেখা পঁচা ছবি দেখার বেদনা কিছুটা ঘুচিয়ে দিল এই ছবিটি। পরেরটি দেখে তো আমি সত্যি ভীষণ আপ্লুত হয়েছি।
পরবর্তী ছবি শুরু হতে বাকি এক ঘন্টা। আমি বাইরে বেরিয়ে এসে ক্যাফেতে বসে বই পড়ছি। দেখি দূর থেকে আমার দিকে ছুটে আসছে এক ভদ্রমহিলা। আরে এ দেখি ডিয়ানা। আর্মেনিয়ার ফিল্ম ক্রিটিক। ও এসে বলল, ও জানে আমি এসেছি বার্লিনে, কিন্তু সে নিজে যে আসবে সেটা আমাকে জানাতে পারেনি। আমি বললাম, যাক দেখা হলো, তোমার দেশের ছবি আছে কি এবার? হ্যাঁ আছে বলেই সে বার্লিনে এসেছে। শুধু তাই নয়, দু-তিনটা পত্রিকায় লেখা দেয়ার পরিবর্তে পয়সা পাবে এই প্রতিশ্রুতি পেয়েই সে বার্লিনে এসেছে। মনে মনে ভাবলাম বাংলাদেশের কথা। একটি প্রবন্ধ লিখে যে পয়সা পাওয়া যায় বাংলাদেশে, তা দিয়ে টেনেটুনে হয় তো একটা প্রপার লাঞ্চ করা যাবে বার্লিনে। আর পুরো ট্যুর স্পন্সর তো স্বপ্নেও ভাবা যায় না। অনেক পত্রিকা তো লেখা নিয়ে আর যোগাযোগই করে না। পয়সাকড়ি তো দূর কি বাত!
ডিয়ানা দ্রুত বিদায় নিয়ে চলে গেল। আমিও আরো কিছুক্ষণ বই পড়ে হাঁটা দিলাম কিউবিক্সের আট নম্বর থিয়েটারে। এখানে দেখানো হবে জোয়েল আলফনসো ভারগাস পরিচালিত মার্কিন ছবি ‘ম্যাড বিলস টু পে (অর ডেস্টিনি, দিলে ক্যু নো সোই মালো)’ (২০২৫)। শেষের স্প্যানিশ কথাটার অর্থ হলো, ডেস্টিনি, বলে দাও সবাইকে আমি অতোটা খারাপ নই। এই বক্তব্যটা আসলে রিকার্ডো বলে কুড়ি বছর বয়সী একটি ছেলের। ডোমিনিকান-আমেরিকান কমিউনিটির রিকো ককটেল ড্রিংক্স বিক্রি করে সমুদ্র সৈকতে। নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারে রয়েছে মা আর কিশোরী বোন। তাদের টানাপোড়েনের সংসারে হঠাৎ জানা যায় রিকো বাবা হতে চলেছে, মেয়েটি বয়সে বোনের সমান, নাম ডেস্টিনি। ছবিটি মোড় নেয় নতুন দিকে। মেয়েটি বাসায় ঝগড়া করে বেরিয়ে আশ্রয় নেয় রিকোর বাসাতে। চারজনের সংসারে নতুন মাত্রা যোগ করে মাতৃগর্ভে থাকা শিশুটি। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা আর রিকোর পরিকল্পনাহীন জীবন বাকি তিনজনকে চিন্তিত করে তোলে।
এই ছবিটি আমার ভালো লেগেছে একটি কারণে, তা হলো, যে কোনো ভালো ছবি দেখবেন কোনো চেষ্টা ছাড়াই আপনাকে একটা গল্প বলবে এবং বলতে বলতে চলচ্চিত্রের এমন ভাষা ব্যবহার করবে, যার চোখ আছে সে দেখবে, আর যে দেখবে না, তাতে তার ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। এই ছবিতে একটি দীর্ঘ আলাপের দৃশ্য আছে। রিকোর সাথে রাগ করে ডেস্টিনি যখন নিজের বাবা-মায়ের বাড়িতে চলে আসে। গর্ভে সন্তান। রিকো চুলটুল কাটিয়ে, মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়ে আসে ডেস্টিনির কাছে। বলে, তার জীবন ডেস্টিনি আর আগত সন্তানকে ছাড়া চলবে না। ক্ষমা করে ফিরে আসতে বলে ডেস্টিনিকে। একদিন তাদেরও আলাদা বাড়ি, গাড়ি ইত্যাদি হবে। সেই দৃশ্যে একপাশে ডেস্টিনিদের বাসার দরজা। অন্যদিকে তারা সিঁড়িতে বসে কথা বলছে। ফ্রেম পুরোপুরি দুই ভাগে বিভক্ত। যেন পরিচালক বুঝিয়ে দিতে চাইছেন এখনো সিঁড়ি ভাঙা বাকি। রিকো যে কথাগুলো বলছে, জীবনের নিশ্চয়তার কথা, সেটি আসতে কষ্ট করতে হবে। এরই ফাঁকে কোলে ছোট বাচ্চা নিয়ে এক দম্পতি টুকটুক করে উপরে উঠে গেল। দারুণ রূপক। পুরো ছবিটার ভেতর থেকে এই দৃশ্যের কথা আমার মনে থাকবে।
এটিই ছিল পার্সপেক্টিভস সেকশন থেকে দেখা আমার শেষ ছবি। মানে এই বিভাগের চৌদ্দটি ছবি দেখা শেষ। এর বাইরে যেসব ছবি দেখব, বা দেখেছি, সব বোনাস। তো মেট্রো চেপে ফেরার পথে আঁচ করতে পারলাম ঘন্টা কয়েক পরই ধর্মঘট শুরু হতে যাচ্ছে। কারণ এক লাইনের ট্রেন আরেক লাইন দিয়ে আসছে। তারপরও একটা বিষয় কিন্তু চোখে পড়ার মতো, মানুষের ভোগান্তি হচ্ছে না। কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে বটে, কিন্তু সেটা ভোগান্তি পর্যন্ত গড়াচ্ছে না। বার্লিনে আসার এক সপ্তাহ আগেই ঢাকায় দন্তচিকিৎসকের কাছে যেতে পারিনি, আমাদের মাঝরাস্তা থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল। কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় বানাতে হবে এই দাবিতে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ তরুণরা মহাখালির মতো রাস্তা আটকে বসেছিল পাঁচ ঘন্টা। পুলিশ অসহায়ের মতো বলেছিল, কিছু করার নাই ভাই। যদি পারেন হেঁটে চলে যান। সেদিন হেঁটে আর যেতে পারিনি। দুনিয়ার অন্যসব দেশ যেখানে পায়ে হাঁটা বাদ দিয়ে সুপারসনিক ট্রেনে চড়ছে। সেখানে আমরা পায়ে হাঁটা ধরেছি। দুদিন পর গড়াগড়ি খাবো। তিনদিন পর যেখানে আছি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে জগদ্দল পাথরে পরিণত হবো।





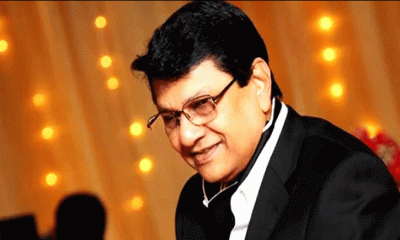

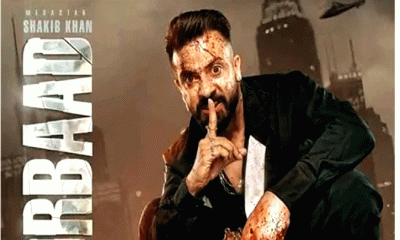


-20231109105053-20250402121817.jpg)